
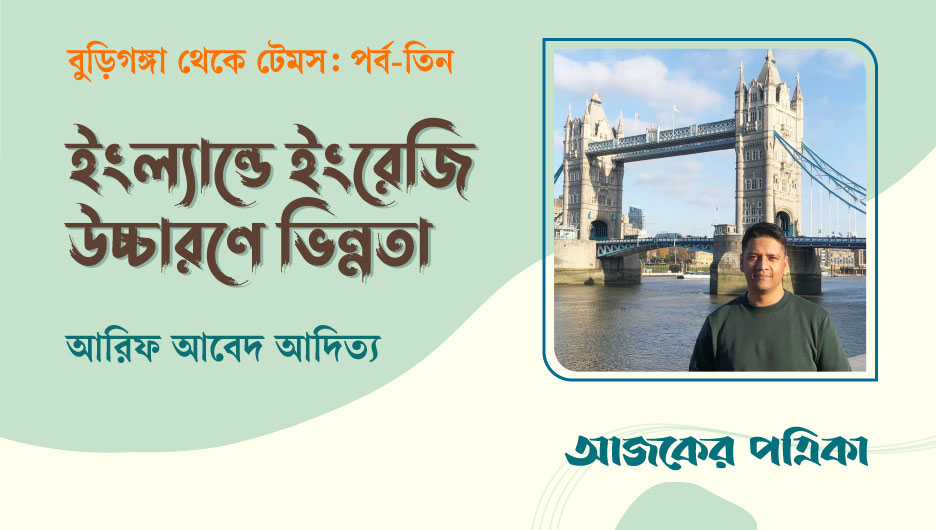
নন-ইংলিশ স্পিকিং দেশের কান যেভাবে ইংরেজি শুনে অভ্যস্ত, তা প্রথম ধাক্কাতেই ভিরমি খাবে বিলাতে এসে। আমারও তেমনটি হয়েছে। ব্রিটিশদের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে বারবার শুধু মনে হচ্ছিল স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে কী ইংরেজি ভাষা শিখলাম! কীসের আইইএলটিএস দিলাম! সবকিছু অনর্থ মনে হচ্ছিল, যখন নেটিভ ইংলিশরা আমার সঠিক ব্যাকরণে বলা কথা বুঝতে না পেরে বারবার বলছিল—পারডন! মাফ করবে—কী বললে? এরা কথায় কথায় পারডন, অ্যাপোলজি ইত্যাদি শব্দ বলবেই। আর আলাপের মাঝখানে পারডন, অ্যাপোলজি ইত্যাদি বললে কার আর বেশি কথা বলার খেই থাকে। ফলে, মুখ এমনিতেই বন্ধ হয়ে যায়—নিজেকে তখন বোবা বোবা লাগে। প্রথম কয়েক সপ্তাহ তাই ‘ইয়েস’ ‘নো’ ‘ভেরি গুড’ দিয়েই চালিয়ে নিতে হয়।

ইংল্যান্ডে ইংরেজি ভাষার উচ্চারণ বৈচিত্র্যের কারণে নিজেকে প্রথম দিকে মনে হয়েছে ভিনগ্রহের কোনো আগন্তুক। মাঝে মাঝে মনে হতো, এই জীবনে আমি কোনো দিন ইংরেজি ভাষা শুনিনি, শেখা তো দূরের কথা। প্রথম কয়েক দিন নেটিভ ব্রিটিশদের অর্ধ-উচ্চারিত শব্দ ও বাক্য শুনে প্রায় বোবা হয়ে যেতাম। এদিকে আমি যতই গ্র্যামার-অ্যাকসেন্ট ঠিক করে কথা বলি, এরা এমন ভান করত, আমি যেন কোনো অজানা ভাষায় কমিউনিকেট করছি। অথচ ক্লাস-লেকচারে প্রফেসরদের কথা ঠিকই বুঝতাম, নোট নিতাম। যাহোক, ধীরে ধীরে আয়ত্তে আসতে থাকে।

প্রথমে আমেরিকান বলল, জানো, আমেরিকা কত বড়? তুমি গাড়িতে চার দিন ধরে একই দিকে যাবে—চার দিন পরও তুমি একই প্রদেশে থাকবে।
তা শোনে অস্ট্রেলিয়ান বলল, আরে, এ আর তেমন কী? অস্ট্রেলিয়া কেমন জানো? চার ঘণ্টা ধরে প্লেনে যাবে; তারপরও দেখবে তুমি একই প্রদেশে আছ।
তখন ব্রিটিশ অট্টহাসি দিতে দিতে বলে, তোমাদের কথা শুনে হাসি থামাতেই পারছি না। শোনো, ইংল্যান্ডে তুমি মাত্র দুই ঘণ্টা হাঁটলে ইংরেজি ভাষার দশ রকমের উচ্চারণ পাবে।
উপভাষা বুঝো হে? উপভাষার ভূগোল জেনে গপ্পো দাও প্লিজ!
ইংল্যান্ডের নেটিভ স্পিকারদের ভাষার ক্ষেত্রে মিডল-নর্দার্ন-সাউথ-ইস্ট-ওয়েস্ট অঞ্চলের যেমন আলাদা উচ্চারণ আছে, তেমনি ব্ল্যাক কান্ট্রি, বার্মিংহাম, নটিংহ্যাম, স্কটিশ, আইরিশ ইত্যাদি আরও নানা উপভাষা আছে। এখানে ইংরেজি উচ্চারণ শুনেই ধরে নেওয়া যায়, ব্যক্তিটি কোন অঞ্চলের বাসিন্দা। আফ্রিকান-আরব-ইন্ডিয়ান-চাইনিজদের ইংরেজি উচ্চারণের কথা বলাই বাহুল্য—নিজেদের দেশের বাক্ভঙ্গি এরা ব্যবহার করে। ফলে খুব সহজেই বলে দেওয়া যায় কে কোন বংশোদ্ভূত জাতি। আবার ইউরোপের বাসিন্দা যেমন, রোমানিয়া, পোলিশ, ফরাসি এদের ইংরেজি উচ্চারণও আলাদা।
টেমসের উত্তর পাড়ের সাধারণ মানুষেরা আনুমানিক ১১৫০ থেকে ১৫০০ সাল পর্যন্ত তাদের দৈনন্দিন জীবনে, চলাফেরায়, হাটবাজারে পরস্পরের সঙ্গে ভাব বিনিময়ের জন্য এই ভাষা ব্যবহার করত। চসারের সময়ে রোমান সাম্রাজ্যের পতন ঘটে গেলেও ক্যাথলিক চার্চের প্রভাব থাকায় ইস্ট-মিডল্যান্ড এলাকার মানুষকেও আনুষ্ঠানিকতা বা ভ্রমণ, সবই করতে হয়েছে লাতিন ভাষায় (কারণ, ধর্মীয় শাস্ত্র ছিল লাতিন ভাষায়)। যদিও শাসক নরমানদের ফরমান করা বিভিন্ন সরকারি দপ্তরের ভাষা ফরাসিতে।
বাংলা ভাষা বা সর্বসাধারণের ‘বুলি’ মধ্যযুগে ঠিক এমন পরিস্থিতির শিকার হয়েছিল। মোগল শাসকদের দাপ্তরিক ভাষা ছিল ফারসি এবং বেদ-গীতা-উপনিষদ ছিল সংস্কৃত ভাষায়। ফলে, সাহিত্যের ভাষা সংগত কারণেই ফারসি-সংস্কৃত মিশ্রিত হয়েছে। অন্যদিকে, ব্রিটিশ আমলে ফারসির পরিবর্তে নতুন শাসকের ভাষা সরকারি দপ্তরে স্থান করে নেয়। ফারসি-সংস্কৃতের মধ্যে তখন ইংরেজির প্রবেশ ঘটে (ইউরোপীয় অন্যান্য দেশের শব্দও যুক্ত হয়)। কলোনিয়াল যুগে বাঙালি মুসলমান সমাজ সাহিত্যচর্চায় এগিয়ে এলে বাংলা ভাষায় যোগ হয় আরবি শব্দের।
ঔপনিবেশিক ফরাসি ও লাতিন ছুড়ে ফেলে দিয়ে চসার টেমসের উত্তর পাড়ের এলাকার মানুষের মুখের ভাষায় সাহিত্য রচনার মাধ্যমে কেবল তৎকালীন রোমান ও নরমান-ফরাসিদের উপনিবেশবাদের অবদমনের বিরুদ্ধে অবস্থান নেননি; মূলত তাঁর প্রচেষ্টা আধুনিক ইংরেজি ভাষার গোড়াপত্তনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। যার কারণে পরে আমরা পৃথিবী বিখ্যাত সব ইংরেজ কবি-সাহিত্যিক পেয়েছি। অপরদিকে, মধ্যযুগে বাংলা ভাষাকে প্রতিষ্ঠার জন্য কবি আব্দুল হাকিমকে লড়াই করতে হয়েছে। আধুনিক যুগে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এই বাংলাকে বিশ্বের দরবারে পৌঁছে দিয়েছেন। বাংলা কথ্যরীতি বা ‘বুলি’ অন্য ভাষাকে ‘অপর’ না করে আপন করে নিয়ে নিজের মতো করে একটা ছাঁচ দিয়েছে। বাংলা ভাষা নানান যুগ ও শাসনামলে আগত/প্রযুক্ত বিদেশি ভাষাকে আত্মসাৎ করেছে, বাংলা ভাষার এমন বিদেশি ভাষাকে নিপুণভাবে হজম করার অপূর্ব ক্ষমতায় মুগ্ধ না হয়ে পারা যায় না।
আরও পড়ুন: