প্রবোধচন্দ্র বাগচী ছিলেন বিংশ শতাব্দীর ভারতীয় উপমহাদেশের অন্যতম পণ্ডিত, সাহিত্যের গবেষক ও শিক্ষাবিদ; বিশেষ করে চীন বিষয়ে গবেষণার জন্য তিনি বিশেষজ্ঞ ব্যক্তি ছিলেন। ১৯২০ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রাচীন ভারতের ইতিহাস ও সংস্কৃতিতে এমএ ডিগ্রি লাভ করার পর তিনি একই বিভাগে প্রভাষক পদে নিযুক্ত হন। ১৯২১ সালে প্রথিতযশা ফরাসি পণ্ডিত সিলভেইঁ লেভির অধীনে বৌদ্ধধর্ম ও চৈনিক ভাষা সম্পর্কে গবেষণার জন্য তাঁকে নব-প্রতিষ্ঠিত বিশ্বভারতীতে পাঠানো হয়। এখানে গবেষণা করার সময় তিনি বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের তৃতীয় উপাচার্য হিসেবে দায়িত্ব পান।
পাশ্চাত্য গবেষণাপদ্ধতির সঙ্গে নিবিড় পরিচয় থাকার ফলে প্রত্নতাত্ত্বিক তথ্য-উপাত্তের সঙ্গে কীভাবে সাহিত্যিক উপাত্তকে সমন্বিত করতে হয়, তা তাঁর জানা ছিল। তিনি চীন গবেষণার ক্ষেত্রে নিচের গবেষণার কাজগুলো করেছিলেন। যেমন—ক. প্রাচীন চৈনিক বৌদ্ধ গ্রন্থাবলি উদ্ধার ও প্রকাশ করা, সেগুলো সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত বিবরণ তৈরি করা এবং সংগৃহীত বিভিন্ন পাণ্ডুলিপির অনুবাদ করা; খ. বৌদ্ধ সাহিত্য ও দর্শন থেকে ভারতীয় সাংস্কৃতিক বিনিময়ের অন্য বহু দিক সম্পর্কে বিস্তৃত বিষয়াবলি নিয়ে গবেষণা করার জন্য প্রত্নসামগ্রী যথা—মুদ্রা, লিপি ও অন্যান্য ধ্বংসাবশেষ সম্পর্কে গভীরভাবে জেনে, তা তাঁর গবেষণায় ব্যবহার করেছিলেন। এ ক্ষেত্রে তিনি চৈনিক গ্রন্থগুলো সম্পর্কে গবেষণায় উদ্ভাবনকুশলতা ও দূরদৃষ্টির নতুন পদ্ধতি প্রয়োগ করেছিলেন।
সহস্র বছরের অধিককাল আগেই বৌদ্ধধর্ম সম্পর্কে সংস্কৃত ভাষায় লেখা বহু গ্রন্থ হারিয়ে গিয়েছিল। বিভিন্ন সময়ে সেগুলো চীনা ভাষায় অনূদিত হয়েছিল। তিনি সেগুলোর কিছু কিছু ইংরেজি অনুবাদ করেছিলেন।
তিনি জীবনের অধিকাংশ সময় চীন ও ভারতের হারিয়ে যাওয়া গ্রন্থ উদ্ধার এবং অনুবাদে ব্যয় করেছেন। তাঁর কাজ ভারতীয় পণ্ডিতদের মধ্যে চীন এবং ভারত-বিদ্যার মধ্যে একধরনের সেতুবন্ধ সৃষ্টি করেছিল। এ জন্য তাঁকে একজন ‘চীন-ভারতবিদ্যা বিশারদ’ পণ্ডিত বলা হয়।
এই পণ্ডিত ব্যক্তিটি ১৮৯৮ সালের ১৮ নভেম্বর যশোর জেলায় জন্মগ্রহণ করেন।

২১ ফেব্রুয়ারির আগে-পরের বছরগুলোজুড়ে নানা কিছু ঘটছিল। এখন এসে দিনগুলোতে ফিরে গেলে শিহরণ বোধ করি, বাংলা ভাষা নিয়ে এখন কিছু হতে দেখলে সেসব দিনে ফিরে যাই। তেমনই একটা হলো ১৯৪৮ সালের ২৪ মার্চ সমাবর্তন সভা। পাকিস্তানের গভর্নর জেনারেল জিন্নাহ ঘোষণা দিলেন—ঢাকাতেই, উর্দু পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা।
৫ ঘণ্টা আগে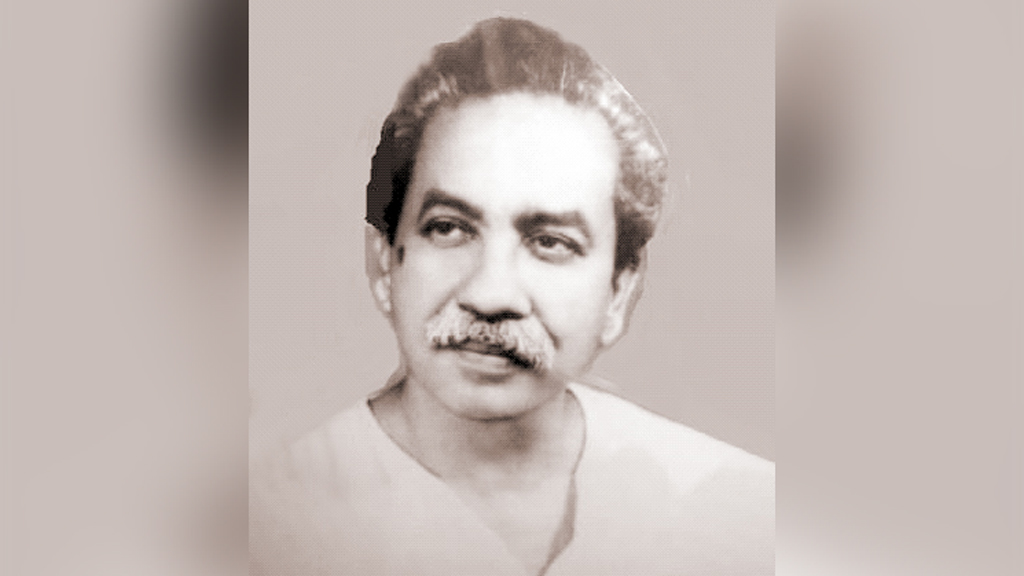
২১ ফেব্রুয়ারি আমতলার সভায় সভাপতির দায়িত্ব পালন করেছিলেন গাজীউল হক। ভাষা আন্দোলন বিষয়ে তিনি লিখেছেন, ‘ভাষা আন্দোলন কোনো বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। এ আন্দোলন ধীরে ধীরে গড়ে উঠেছে। ১৯৪৭ সালে এ আন্দোলনের বুনিয়াদ রচনা হয়। ১৯৪৮-এ আন্দোলনের অঙ্কুরোদ্গম হয়। ১৯৫২ সালে এ আন্দোলন এক বিরাট মহীরূহে পরিণত হয়।
১ দিন আগে
বাংলা ভাষার প্রতি ভালোবাসার প্রকাশ দেখা যায় কবি ফররুখ আহমদের মধ্যে। ১৯৪৭ সালের সেপ্টেম্বর-অক্টোবরের সওগাতে তিনি ‘পাকিস্তান: রাষ্ট্রভাষা ও সাহিত্য’ নামে প্রবন্ধে লিখেছিলেন, ‘পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা কী হবে, এ নিয়ে যথেষ্ট বাদানুবাদ চলছে আর সবচাইতে আশার কথা এই যে, আলোচনা হয়েছে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে...
৬ দিন আগে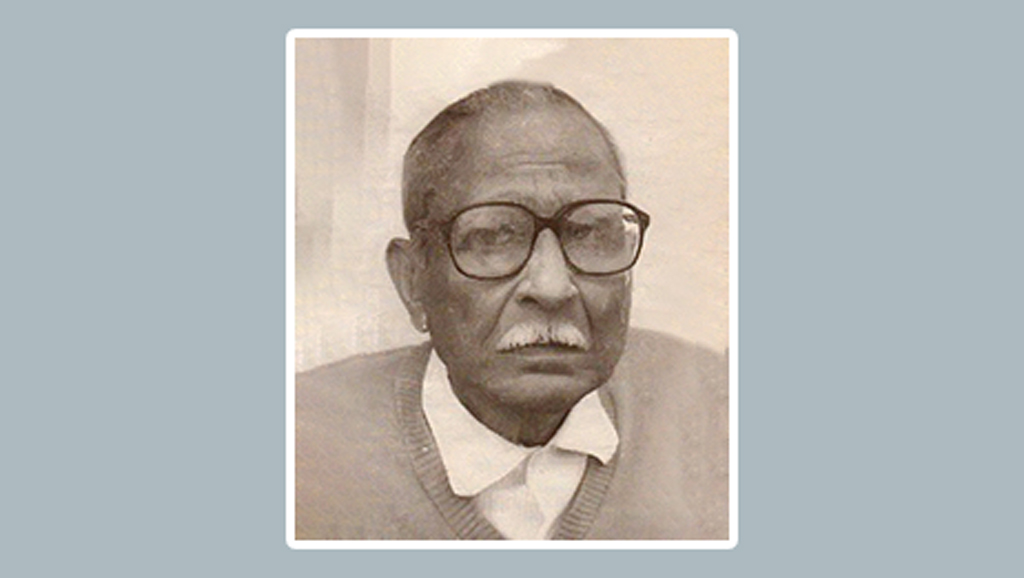
১৯৪৭ সালের ৩০ জুন দৈনিক আজাদে ছাপা হওয়া ‘পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা’ শিরোনামে প্রকাশিত প্রবন্ধে আবদুল হক লিখেছিলেন, ‘পাকিস্তানের সবচেয়ে প্রচলিত ভাষা পাঁচটি। বেলুচি, পশতু, সিন্ধি, পাঞ্জাবি ও বাংলা। পশ্চিম পাকিস্তানে উর্দু ভাষা নেই, তা নয়, বাংলাও আছে। কিন্তু পূর্ব পাকিস্তানের তো নয়ই, পশ্চিম...
১৫ দিন আগে