সুরেশচন্দ্র মজুমদারকে অনেকেই চেনেন। জাতীয়তাবাদী পত্রিকা প্রকাশের উদ্দেশ্যে আবাল্য বন্ধু প্রফুল্লকুমার সরকারের সাহায্য ও সম্পাদনায় ১৯২২ সালের ১৩ মার্চ তিনি আনন্দবাজার পত্রিকা প্রকাশ করেন। তাঁরই উদ্যোগে দেশ এবং দ্য স্টেটসম্যানের প্রতিপক্ষ হিসেবে হিন্দুস্তান স্ট্যান্ডার্ড প্রকাশিত হয়।
১৯৪৪ সালে সৈয়দ মুজতবা আলী ‘সত্যপীর’ নাম নিয়ে আনন্দবাজার পত্রিকায় সম্পাদকীয়-পরবর্তী স্তম্ভে প্রবন্ধ লিখতে শুরু করেন। দুটো লেখা প্রকাশিত হওয়ার পর তিনি বুঝতে পারেন যে লেখাগুলো পছন্দ করছেন প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তারা।
সুরেশচন্দ্র মজুমদারের সঙ্গে বন্ধুবান্ধবদের মাধ্যমে সৈয়দ মুজতবা আলীর পরিচয় হয়। সুরেশচন্দ্র মজুমদার লেখা চেনার ব্যাপারে ছিলেন একেবারে জহুরি। খুব ভালোভাবে লেখা বুঝতে পারতেন তিনি। কড়া সমালোচনা যেমন করতে পারতেন, তেমনি তিনি ছিলেন সহৃদয় ব্যক্তি। এই দুইয়ের দ্বন্দ্বে কখনো কখনো খারাপেরাও তাঁর প্রশ্রয় পেত।
সৈয়দ মুজতবা আলী সুরেশচন্দ্র মজুমদারকে বাঘের মতো ভয় পেতেন, যদিও জানতেন তাঁকে ভয় পাওয়ার কিছু নেই। মজার ব্যাপার, তখন পর্যন্ত একদিনও সুরেশচন্দ্র মজুমদার সৈয়দ মুজতবা আলীর কোনো লেখার কোনো সমালোচনা করেননি, কোনো কিছু নতুন করে লিখতে বলেননি বা কোনো ধরনের উপদেশও দেননি।
১৯৪৪-৪৫ সালের দিকে কলকাতায় একটা অশান্তির সৃষ্টি হলে সৈয়দ মুজতবা আলী তাঁর জন্য নির্দিষ্ট লেখা না লিখে লিখে ফেললেন একটি কবিতা। এখন কী করবেন! কবিতা কি এখানে ছাপা যেতে পারে! সে বিষয়ে কোনো দিকনির্দেশনা ছিল না। অগত্যা তিনি সেই লেখা নিয়ে গেলেন সুরেশবাবুর কাছে। দুটো ছত্র পড়েই সুরেশবাবু লেখাটা পাঠিয়ে দিলেন প্রেসে।
এবং বললেন, ‘ওরে...একে চা দে আর কী দিবি দে...আর...’, কথা অসমাপ্ত রেখেই তিনি ফের কাজে মন দিলেন।
আজ সৈয়দ মুজতবা আলীর জন্মদিনে দেশ পত্রিকায় আফটার এডিট না লিখে কবিতা লেখার গল্পটি বলা হলো।
সূত্র: সৈয়দ মুজতবা আলী রচনাবলী, চতুর্থ খণ্ড, পৃষ্ঠা ৩৮-৩৯

২১ ফেব্রুয়ারির আগে-পরের বছরগুলোজুড়ে নানা কিছু ঘটছিল। এখন এসে দিনগুলোতে ফিরে গেলে শিহরণ বোধ করি, বাংলা ভাষা নিয়ে এখন কিছু হতে দেখলে সেসব দিনে ফিরে যাই। তেমনই একটা হলো ১৯৪৮ সালের ২৪ মার্চ সমাবর্তন সভা। পাকিস্তানের গভর্নর জেনারেল জিন্নাহ ঘোষণা দিলেন—ঢাকাতেই, উর্দু পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা।
৩ ঘণ্টা আগে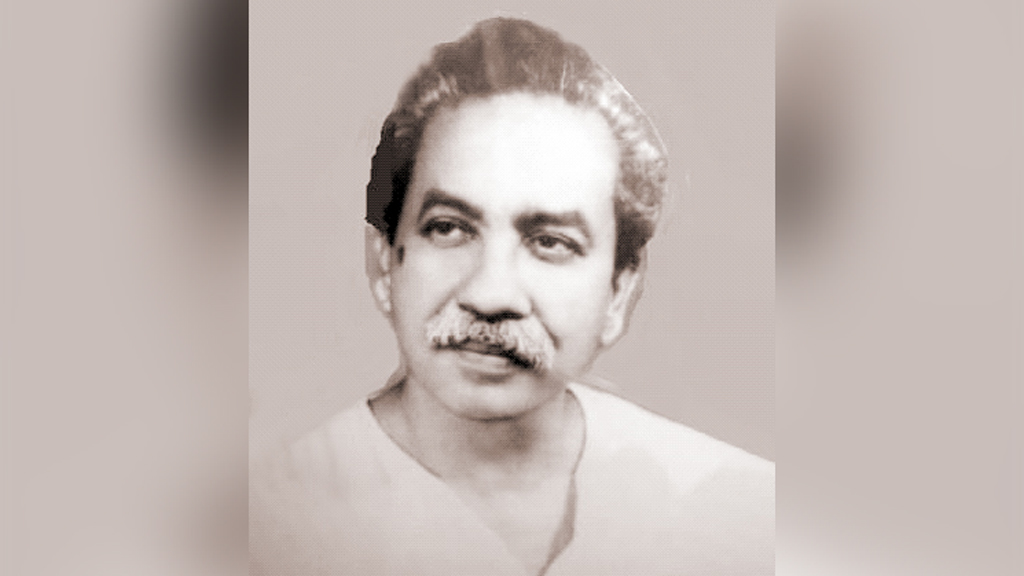
২১ ফেব্রুয়ারি আমতলার সভায় সভাপতির দায়িত্ব পালন করেছিলেন গাজীউল হক। ভাষা আন্দোলন বিষয়ে তিনি লিখেছেন, ‘ভাষা আন্দোলন কোনো বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। এ আন্দোলন ধীরে ধীরে গড়ে উঠেছে। ১৯৪৭ সালে এ আন্দোলনের বুনিয়াদ রচনা হয়। ১৯৪৮-এ আন্দোলনের অঙ্কুরোদ্গম হয়। ১৯৫২ সালে এ আন্দোলন এক বিরাট মহীরূহে পরিণত হয়।
১ দিন আগে
বাংলা ভাষার প্রতি ভালোবাসার প্রকাশ দেখা যায় কবি ফররুখ আহমদের মধ্যে। ১৯৪৭ সালের সেপ্টেম্বর-অক্টোবরের সওগাতে তিনি ‘পাকিস্তান: রাষ্ট্রভাষা ও সাহিত্য’ নামে প্রবন্ধে লিখেছিলেন, ‘পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা কী হবে, এ নিয়ে যথেষ্ট বাদানুবাদ চলছে আর সবচাইতে আশার কথা এই যে, আলোচনা হয়েছে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে...
৬ দিন আগে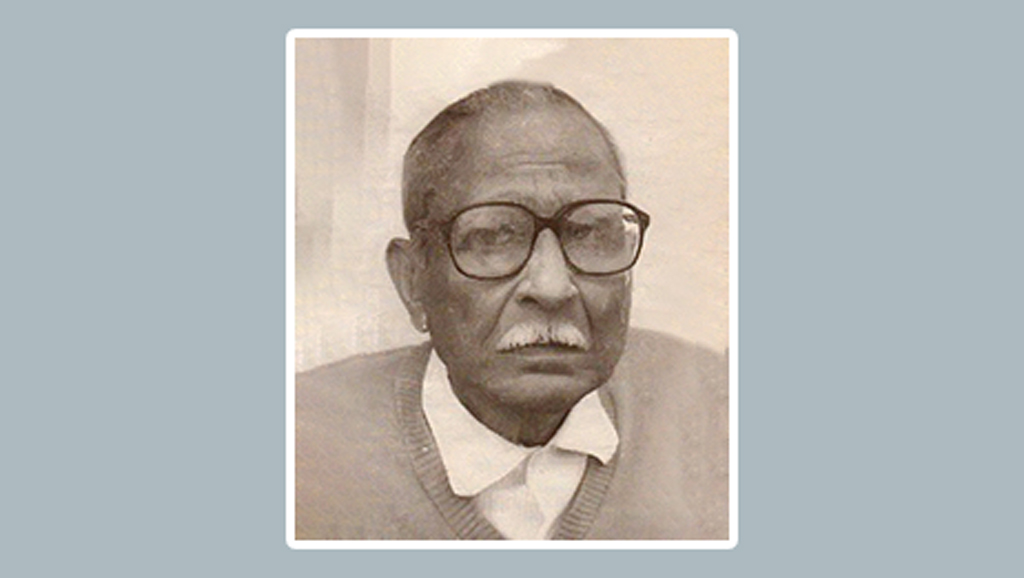
১৯৪৭ সালের ৩০ জুন দৈনিক আজাদে ছাপা হওয়া ‘পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা’ শিরোনামে প্রকাশিত প্রবন্ধে আবদুল হক লিখেছিলেন, ‘পাকিস্তানের সবচেয়ে প্রচলিত ভাষা পাঁচটি। বেলুচি, পশতু, সিন্ধি, পাঞ্জাবি ও বাংলা। পশ্চিম পাকিস্তানে উর্দু ভাষা নেই, তা নয়, বাংলাও আছে। কিন্তু পূর্ব পাকিস্তানের তো নয়ই, পশ্চিম...
১৫ দিন আগে