আরিফ আবেদ আদিত্য

বুড়িগঙ্গার পাড় থেকে টেমসের তীরে আসার প্রায় এক বছর হয়ে এল। গত বছর অক্টোবরে সূর্যালোক উদ্ভাসিত প্রাণচাঞ্চল্যে ভরপুর এক দেশ ছেড়ে সাত সমুদ্র তেরো নদীর পাড়ে হাড়কাঁপানো ধূসর ভূমিতে পদার্পণ করি। আমার আগমনের সময়টায় বিলাতে শীত আসি-আসি করছে—জাঁকিয়ে বসেনি। অভিজ্ঞ ব্যক্তিরা আগেই বলেছিলেন, ইউরোপের শীত কোনো ছেলেখেলা নয়। গরমের দেশ থেকে গিয়ে শীত নিয়ে সামান্য হেলাফেলা করলেই সর্দি-কাশি আর জ্বরে জীবন জেরবার করে দেবে। কনকনে মাঘের ঠান্ডার চেয়েও অধিক হাড়কাঁপানো শুধু নয়, হাড় ফুটা করা শীত এখানে বিরাজ করে। কয়েক পরতের গরম কাপড়েও এই কনকনে ঠান্ডা নিবারণ সম্ভব হয় না। লন্ডনে যেদিন আসি, এয়ারপোর্ট থেকে বের হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ঠান্ডা একটা হালকা ঝাপটা এসে লাগে নাকে-মুখে। আগেভাগে প্রস্তুতির কয়েক প্রস্থ কাপড়ে অবগুণ্ঠিত শরীর টের না পেলেও ঠান্ডার দাপটের ঈষৎ বিজ্ঞাপন নাকের ডগা ছুঁয়ে ঝাঁজের আঁচ দিয়েছিল বৈকি!
আমার ইংল্যান্ডে আসার কারণ, দ্বিতীয় মাস্টার্স করা—একটা ডিগ্রি অর্জনের চেয়ে ইংরেজি শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতিকে কিছুটা ঘনিষ্ঠভাবে অবলোকন-পর্যবেক্ষণ করা। সাহিত্যের ছাত্র হিসেবে—প্রায় দুই শ বছর যারা শাসন করল, যাদের সাংস্কৃতিক প্রভাববলয় কলোনিয়াল দেশগুলোতে এখনো বিরাজমান, তাদের যাপিত জীবনপদ্ধতি ও সমাজকে কাছ থেকে দেখার আগ্রহই আমাকে এখানে নিয়ে আসে।
বাংলাদেশ বিমানের ফ্লাইটে লন্ডনের হিথরো এয়ারপোর্টে নামি রাত ১০টার দিকে। ইমিগ্রেশন, লাগেজ বেল্ট থেকে ব্যাগপত্র নিয়ে বের হতে হতে সাড়ে ১১টা। বাইরে আমার জন্য অপেক্ষা করছিল বন্ধু ও সহকর্মী কিংস কলেজে পিএইচডি ফেলো জগদীশ। হিথরো ইমিগ্রেশনে লম্বা লাইন, ফ্লাইট সরাসরি বিমান বাংলাদেশের হওয়ায় লাইনে সবাই বাংলাদেশি নাগরিকই ছিলেন। নানা পেশার বিভিন্ন বয়সী নারী-পুরুষ লম্বা লাইন দাঁড়িয়ে। ইমিগ্রেশনের কাউন্টার অনেক; মাথার ওপরে বড় করে সাইনবোর্ডে স্থানে স্থানে লেখা ‘ইউকে বর্ডার’। লাইনে দাঁড়িয়ে লেখাটায় চোখ পড়তেই মনে হলো নতুন কোনো দেশে প্রবেশ করতে যাচ্ছি। বাংলাদেশ থেকে উড়াল দেওয়ার আগ পর্যন্ত এমন মনে হয়নি।
লন্ডনে ইমিগ্রেশন অফিসাররা ভিসা-পাসপোর্ট চেক করার সময় যাত্রীদের অনেক ধরনের প্রশ্ন জিজ্ঞেস করেন। এতে এয়ারপোর্ট থেকে বের হতে বেশ সময় লেগে যায়। ইমিগ্রেশনের জেরায় আমার মতো পড়তে আসা শিক্ষার্থী ছাড়াও প্রথমবার যারা ব্রিটেনে এসেছে, সবাইকেই দেখলাম কমবেশি উদ্বিগ্ন হতে। এর পেছনে কারণও আছে বৈকি! কারও প্রশ্নের উত্তর মনঃপূত না হলে তাকে আলাদা করে অন্য একটি রুমে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। কালো উর্দির ওপর পুলিশ লেখা ব্যক্তিরা যখন কাউকে আলাদা করে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য নিয়ে যায়, তখন পেছনে লাইনে দাঁড়ানো যাত্রীদের মানসিক অবস্থা কেমন হয়, তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। ইউএসএ, ইউকের ইমিগ্রেশনের কড়াকড়ি নিয়ে নতুন কিছু বলার নেই আসলে। তবে আমার কাছে যত দূর মনে হয়েছে, ভাষা সমস্যাই ইমিগ্রেশনে ভোগান্তির অন্যতম কারণ। অনেককে দেখলাম দোভাষীর আশ্রয় নিতে। লাইনে দাঁড়ানো ব্যক্তিদের মধ্য থেকেই কেউ দোভাষী হিসেবে সাহায্য করবে কি না, জিজ্ঞেস করা হয়। ইমিগ্রেশন অফিসারদের নিজস্ব ব্রিটিশ উচ্চারণে বলা প্রশ্ন অনেকের পক্ষেই বোঝা কষ্টসাধ্য ব্যাপার। বুঝে বা না বুঝে ‘ইয়েস’, ‘নো’-এর মতো উত্তর দিয়ে কোনোমতে ইমিগ্রেশন পার হওয়ার চিন্তা করতে গিয়েই অনেকে ঝামেলা বাড়ায়। এরা সঠিক উত্তর না পাওয়া পর্যন্ত পাসপোর্টে ছাড়পত্রের সিল দেবেই না। আমার সামনে তখন ৮-১০ জন। এমন সময় জিজ্ঞেস করা হয়, কেউ দোভাষী হবে কি না। দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে পা ব্যথা হওয়ার জোগাড়। যারা দোভাষী হিসেবে সাহায্য করেছে, দেখলাম, তারা তাড়াতাড়ি বের হয়ে গেছে। তাই আমিও এবার সুযোগটা নিই। একজনকে সাহায্য করলাম। তাকে ইউকেতে কে থাকে, কোথায় থাকবে, কী জন্য এসেছে ইত্যাদি কয়েকটা প্রশ্ন করেই ছেড়ে দেয়। এবার আমার পালা। ব্রিটিশদের একটা খুব ভালো দিক আছে। কাউকে সামান্য সাহায্য করলে, ফুটপাতে হাঁটার সময় একটু রাস্তা ছেড়ে দিলে, কোনো লাইনে আগে যেতে দিলে ধন্যবাদ দিতে দিতে মুখে ফেনা তুলে ফেলে। আগের যাত্রীকে সাহায্য করেছি—এ জন্যই হয়তো ইমিগ্রেশন কাউন্টারে বসা প্রায় পঞ্চাশোর্ধ্ব স্থূলকায় শ্বেতাঙ্গ অফিসার আমার পাসপোর্ট হাতে নিয়ে কেবল একটা প্রশ্নই করেন, ‘কোন বিষয়ে পড়তে এসেছ?’ উত্তর দেওয়ার আগেই সিল মেরে পাসপোর্ট ফেরত দিতে দিতে হাস্যোজ্জ্বল ভঙ্গিতে তিনি বলেন, ‘ওয়েলকাম টু ইউনাইটেড কিংডম মাই বয়।’ অপ্রত্যাশিত এমন উষ্ণ অভ্যর্থনায় দীর্ঘ ভ্রমণক্লান্তি নিমেষে উবে গেল।
 ইমিগ্রেশন শেষ করে লাগেজসহ গেট পেরোতেই বন্ধু জগদীশের দেখা পাই। বেচারা তিন-চার ঘণ্টা ধরে অপেক্ষায় আছে। লন্ডনের বিখ্যাত টিউবে চড়ার অভিজ্ঞতা এই প্রথম। টিউব অনেকটা মেট্রোরেলের মতো—পার্থক্য হলো টিউব মাটির নিচ দিয়ে চলে। হিথরো থেকে বন্ধুর বাসা পূর্ব লন্ডনের ফরেস্ট গেটে আসতে আসতে রাত ১২টা পার হয়ে যায়। মজার ব্যাপার হলো, টিউবে সেই মধ্যরাতেও দেখলাম মেয়েরা নির্বিঘ্নে চলাফেরা করছে। কোথাও কোনো ভয়-শঙ্কার লেশমাত্র নেই। এ ছাড়া লন্ডনে নেমেই একবারের দর্শনে যে বিষয়টা দৃষ্টিগ্রাহ্য হয়, তা হলো টিউবের কামরায় দেখা জাতিগত বৈচিত্র্যের সমাহার। ধরা যাক, একেকটা কামরায় ১০ জন যাত্রী—তাদের আটজনই দেখা যাবে ভিন্ন ভিন্ন জাতির প্রতিনিধিত্ব করছে। কী চুলের বাহার, কী বেশভূষা, গাত্রবর্ণ বা ভাষা ইত্যাদি সব মিলিয়ে মনে হবে একটি আন্তর্জাতিক কামরায় বসে আছি। লন্ডনে এই বিষয় বেশ উপভোগ্য লেগেছে—এই শহরে নিজেকে সংখ্যালঘু বা আগন্তুক মনে হয় না; ফলে হীনম্মন্যতা আসে না; যেমনটা ইংল্যান্ডের অন্য শহরগুলোতে কিছুটা অনুভব হয়। শ্বেতাঙ্গ-কৃষ্ণাঙ্গ বা এশীয়দের সমান পদচারণে মুখর এখানকার পাবলিক পরিবহন। চলার পথে কেউ বই পড়ছে, কেউ মোবাইলে গেমস খেলছে, কেউ হেডফোনে গান শুনছে—যে যার জগতে আত্মমগ্ন, কর্মক্লান্ত কেউবা বাসায় ফেরার আগে একটু ঝিম মেরে ঘুমিয়ে নিচ্ছে—গন্তব্যস্থলে পৌঁছামাত্র টুপ করে নেমে পড়ছে। আবার কোনো স্টেশন থেকে এক জোড়া কপোত-কপোতী উঠে সিট না পেয়ে পরস্পরকে আলিঙ্গনরত অবস্থায় দাঁড়িয়ে থেকে জীবনের প্রতিটা মুহূর্তকে উপভোগ করে নিচ্ছে। কারও প্রতি কারও কোনো বিকার-অনুযোগ নেই।
ইমিগ্রেশন শেষ করে লাগেজসহ গেট পেরোতেই বন্ধু জগদীশের দেখা পাই। বেচারা তিন-চার ঘণ্টা ধরে অপেক্ষায় আছে। লন্ডনের বিখ্যাত টিউবে চড়ার অভিজ্ঞতা এই প্রথম। টিউব অনেকটা মেট্রোরেলের মতো—পার্থক্য হলো টিউব মাটির নিচ দিয়ে চলে। হিথরো থেকে বন্ধুর বাসা পূর্ব লন্ডনের ফরেস্ট গেটে আসতে আসতে রাত ১২টা পার হয়ে যায়। মজার ব্যাপার হলো, টিউবে সেই মধ্যরাতেও দেখলাম মেয়েরা নির্বিঘ্নে চলাফেরা করছে। কোথাও কোনো ভয়-শঙ্কার লেশমাত্র নেই। এ ছাড়া লন্ডনে নেমেই একবারের দর্শনে যে বিষয়টা দৃষ্টিগ্রাহ্য হয়, তা হলো টিউবের কামরায় দেখা জাতিগত বৈচিত্র্যের সমাহার। ধরা যাক, একেকটা কামরায় ১০ জন যাত্রী—তাদের আটজনই দেখা যাবে ভিন্ন ভিন্ন জাতির প্রতিনিধিত্ব করছে। কী চুলের বাহার, কী বেশভূষা, গাত্রবর্ণ বা ভাষা ইত্যাদি সব মিলিয়ে মনে হবে একটি আন্তর্জাতিক কামরায় বসে আছি। লন্ডনে এই বিষয় বেশ উপভোগ্য লেগেছে—এই শহরে নিজেকে সংখ্যালঘু বা আগন্তুক মনে হয় না; ফলে হীনম্মন্যতা আসে না; যেমনটা ইংল্যান্ডের অন্য শহরগুলোতে কিছুটা অনুভব হয়। শ্বেতাঙ্গ-কৃষ্ণাঙ্গ বা এশীয়দের সমান পদচারণে মুখর এখানকার পাবলিক পরিবহন। চলার পথে কেউ বই পড়ছে, কেউ মোবাইলে গেমস খেলছে, কেউ হেডফোনে গান শুনছে—যে যার জগতে আত্মমগ্ন, কর্মক্লান্ত কেউবা বাসায় ফেরার আগে একটু ঝিম মেরে ঘুমিয়ে নিচ্ছে—গন্তব্যস্থলে পৌঁছামাত্র টুপ করে নেমে পড়ছে। আবার কোনো স্টেশন থেকে এক জোড়া কপোত-কপোতী উঠে সিট না পেয়ে পরস্পরকে আলিঙ্গনরত অবস্থায় দাঁড়িয়ে থেকে জীবনের প্রতিটা মুহূর্তকে উপভোগ করে নিচ্ছে। কারও প্রতি কারও কোনো বিকার-অনুযোগ নেই।
 মূল সড়ক থেকে পাতাল স্টেশনে যাওয়ার জন্য বেশ কয়েকবার চলন্ত সিঁড়ি বেয়ে নিচে নামতে হয়। আমাদের প্রাথমিক গন্তব্য স্ট্র্যাটফোর্ড ইন্টারন্যাশনাল রেলস্টেশন। সেখান থেকে ট্যাক্সি বা উবার নিয়ে বাসায় যাওয়ার পরিকল্পনা। হিথরো থেকে ফরেস্টগেট যেতে কয়েকবার টিউব পরিবর্তন করতে হয়। এ ছাড়া উপায়ও ছিল না। কারণ, সরাসরি ট্যাক্সিতে গেলে অনেক ভাড়া। এখানকার টিউব স্টেশন মাটির গভীরে অবস্থিত। টিউবে চড়ার জন্য বেশ কয়েকটা চলন্ত সিঁড়ি দিয়ে নামতে হয়। আমাদের দেশের শপিং মলের এস্কেলেটরের চেয়ে প্রায় ১০ গুণ দৈর্ঘ্যের হবে এসব চলন্ত সিঁড়ি। লন্ডনের পাতাল রেললাইন-টিউব ব্যবস্থা এক এলাহি কারবার। এগুলো দেখলে যে কারও মনে হবে মাটির নিচে আরেক লন্ডন শহর অবস্থিত। আক্ষরিক অর্থেই, মাটির ওপরে ট্রাফিক সিগন্যালে দাঁড়িয়ে বা ফুটপাতে হাঁটতে গিয়ে মাটির নিচে টিউব-ট্রেন চলার কম্পন অনুভূত হয়। যদিও এগুলো মাটির নিচে প্রায় ২০-৩০ তলা বিল্ডিংয়ের সমান গভীরে অবস্থিত। দিন নেই, রাত নেই—মাটির ওপরে ও নিচে বিরামহীনভাবে চলে লন্ডনের পাবলিক পরিবহন।
মূল সড়ক থেকে পাতাল স্টেশনে যাওয়ার জন্য বেশ কয়েকবার চলন্ত সিঁড়ি বেয়ে নিচে নামতে হয়। আমাদের প্রাথমিক গন্তব্য স্ট্র্যাটফোর্ড ইন্টারন্যাশনাল রেলস্টেশন। সেখান থেকে ট্যাক্সি বা উবার নিয়ে বাসায় যাওয়ার পরিকল্পনা। হিথরো থেকে ফরেস্টগেট যেতে কয়েকবার টিউব পরিবর্তন করতে হয়। এ ছাড়া উপায়ও ছিল না। কারণ, সরাসরি ট্যাক্সিতে গেলে অনেক ভাড়া। এখানকার টিউব স্টেশন মাটির গভীরে অবস্থিত। টিউবে চড়ার জন্য বেশ কয়েকটা চলন্ত সিঁড়ি দিয়ে নামতে হয়। আমাদের দেশের শপিং মলের এস্কেলেটরের চেয়ে প্রায় ১০ গুণ দৈর্ঘ্যের হবে এসব চলন্ত সিঁড়ি। লন্ডনের পাতাল রেললাইন-টিউব ব্যবস্থা এক এলাহি কারবার। এগুলো দেখলে যে কারও মনে হবে মাটির নিচে আরেক লন্ডন শহর অবস্থিত। আক্ষরিক অর্থেই, মাটির ওপরে ট্রাফিক সিগন্যালে দাঁড়িয়ে বা ফুটপাতে হাঁটতে গিয়ে মাটির নিচে টিউব-ট্রেন চলার কম্পন অনুভূত হয়। যদিও এগুলো মাটির নিচে প্রায় ২০-৩০ তলা বিল্ডিংয়ের সমান গভীরে অবস্থিত। দিন নেই, রাত নেই—মাটির ওপরে ও নিচে বিরামহীনভাবে চলে লন্ডনের পাবলিক পরিবহন।
রাতে বন্ধুর বাসায় আতিথেয়তা গ্রহণ করে পরদিন রওনা দিই নিজ গন্তব্য শহর—ক্যান্টাবরিতে। ক্যান্টাবরি সাহিত্যের ছাত্রদের কাছে এক অবিস্মরণীয় নাম। ইংরেজি সাহিত্যের জনক জিওফ্রে চসারের ‘ক্যান্টাবরি টেলস’-এর সেই ক্যান্টাবরি শহরে কাটে আমার ১১ মাস। এই শহরের আনাচকানাচে ছড়িয়ে আছে ইংল্যান্ডের শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতির হাজার বছরের ইতিহাস।
ক্যান্টাবরিকে বলা হয় ‘লন্ডন বিফোর লন্ডন’। রাজধানী লন্ডন গড়ে ওঠার আগে ইংল্যান্ডের লন্ডন ছিল এই শহর। এই গল্প হবে পরের পর্বে।
(চলবে)

বুড়িগঙ্গার পাড় থেকে টেমসের তীরে আসার প্রায় এক বছর হয়ে এল। গত বছর অক্টোবরে সূর্যালোক উদ্ভাসিত প্রাণচাঞ্চল্যে ভরপুর এক দেশ ছেড়ে সাত সমুদ্র তেরো নদীর পাড়ে হাড়কাঁপানো ধূসর ভূমিতে পদার্পণ করি। আমার আগমনের সময়টায় বিলাতে শীত আসি-আসি করছে—জাঁকিয়ে বসেনি। অভিজ্ঞ ব্যক্তিরা আগেই বলেছিলেন, ইউরোপের শীত কোনো ছেলেখেলা নয়। গরমের দেশ থেকে গিয়ে শীত নিয়ে সামান্য হেলাফেলা করলেই সর্দি-কাশি আর জ্বরে জীবন জেরবার করে দেবে। কনকনে মাঘের ঠান্ডার চেয়েও অধিক হাড়কাঁপানো শুধু নয়, হাড় ফুটা করা শীত এখানে বিরাজ করে। কয়েক পরতের গরম কাপড়েও এই কনকনে ঠান্ডা নিবারণ সম্ভব হয় না। লন্ডনে যেদিন আসি, এয়ারপোর্ট থেকে বের হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ঠান্ডা একটা হালকা ঝাপটা এসে লাগে নাকে-মুখে। আগেভাগে প্রস্তুতির কয়েক প্রস্থ কাপড়ে অবগুণ্ঠিত শরীর টের না পেলেও ঠান্ডার দাপটের ঈষৎ বিজ্ঞাপন নাকের ডগা ছুঁয়ে ঝাঁজের আঁচ দিয়েছিল বৈকি!
আমার ইংল্যান্ডে আসার কারণ, দ্বিতীয় মাস্টার্স করা—একটা ডিগ্রি অর্জনের চেয়ে ইংরেজি শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতিকে কিছুটা ঘনিষ্ঠভাবে অবলোকন-পর্যবেক্ষণ করা। সাহিত্যের ছাত্র হিসেবে—প্রায় দুই শ বছর যারা শাসন করল, যাদের সাংস্কৃতিক প্রভাববলয় কলোনিয়াল দেশগুলোতে এখনো বিরাজমান, তাদের যাপিত জীবনপদ্ধতি ও সমাজকে কাছ থেকে দেখার আগ্রহই আমাকে এখানে নিয়ে আসে।
বাংলাদেশ বিমানের ফ্লাইটে লন্ডনের হিথরো এয়ারপোর্টে নামি রাত ১০টার দিকে। ইমিগ্রেশন, লাগেজ বেল্ট থেকে ব্যাগপত্র নিয়ে বের হতে হতে সাড়ে ১১টা। বাইরে আমার জন্য অপেক্ষা করছিল বন্ধু ও সহকর্মী কিংস কলেজে পিএইচডি ফেলো জগদীশ। হিথরো ইমিগ্রেশনে লম্বা লাইন, ফ্লাইট সরাসরি বিমান বাংলাদেশের হওয়ায় লাইনে সবাই বাংলাদেশি নাগরিকই ছিলেন। নানা পেশার বিভিন্ন বয়সী নারী-পুরুষ লম্বা লাইন দাঁড়িয়ে। ইমিগ্রেশনের কাউন্টার অনেক; মাথার ওপরে বড় করে সাইনবোর্ডে স্থানে স্থানে লেখা ‘ইউকে বর্ডার’। লাইনে দাঁড়িয়ে লেখাটায় চোখ পড়তেই মনে হলো নতুন কোনো দেশে প্রবেশ করতে যাচ্ছি। বাংলাদেশ থেকে উড়াল দেওয়ার আগ পর্যন্ত এমন মনে হয়নি।
লন্ডনে ইমিগ্রেশন অফিসাররা ভিসা-পাসপোর্ট চেক করার সময় যাত্রীদের অনেক ধরনের প্রশ্ন জিজ্ঞেস করেন। এতে এয়ারপোর্ট থেকে বের হতে বেশ সময় লেগে যায়। ইমিগ্রেশনের জেরায় আমার মতো পড়তে আসা শিক্ষার্থী ছাড়াও প্রথমবার যারা ব্রিটেনে এসেছে, সবাইকেই দেখলাম কমবেশি উদ্বিগ্ন হতে। এর পেছনে কারণও আছে বৈকি! কারও প্রশ্নের উত্তর মনঃপূত না হলে তাকে আলাদা করে অন্য একটি রুমে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। কালো উর্দির ওপর পুলিশ লেখা ব্যক্তিরা যখন কাউকে আলাদা করে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য নিয়ে যায়, তখন পেছনে লাইনে দাঁড়ানো যাত্রীদের মানসিক অবস্থা কেমন হয়, তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। ইউএসএ, ইউকের ইমিগ্রেশনের কড়াকড়ি নিয়ে নতুন কিছু বলার নেই আসলে। তবে আমার কাছে যত দূর মনে হয়েছে, ভাষা সমস্যাই ইমিগ্রেশনে ভোগান্তির অন্যতম কারণ। অনেককে দেখলাম দোভাষীর আশ্রয় নিতে। লাইনে দাঁড়ানো ব্যক্তিদের মধ্য থেকেই কেউ দোভাষী হিসেবে সাহায্য করবে কি না, জিজ্ঞেস করা হয়। ইমিগ্রেশন অফিসারদের নিজস্ব ব্রিটিশ উচ্চারণে বলা প্রশ্ন অনেকের পক্ষেই বোঝা কষ্টসাধ্য ব্যাপার। বুঝে বা না বুঝে ‘ইয়েস’, ‘নো’-এর মতো উত্তর দিয়ে কোনোমতে ইমিগ্রেশন পার হওয়ার চিন্তা করতে গিয়েই অনেকে ঝামেলা বাড়ায়। এরা সঠিক উত্তর না পাওয়া পর্যন্ত পাসপোর্টে ছাড়পত্রের সিল দেবেই না। আমার সামনে তখন ৮-১০ জন। এমন সময় জিজ্ঞেস করা হয়, কেউ দোভাষী হবে কি না। দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে পা ব্যথা হওয়ার জোগাড়। যারা দোভাষী হিসেবে সাহায্য করেছে, দেখলাম, তারা তাড়াতাড়ি বের হয়ে গেছে। তাই আমিও এবার সুযোগটা নিই। একজনকে সাহায্য করলাম। তাকে ইউকেতে কে থাকে, কোথায় থাকবে, কী জন্য এসেছে ইত্যাদি কয়েকটা প্রশ্ন করেই ছেড়ে দেয়। এবার আমার পালা। ব্রিটিশদের একটা খুব ভালো দিক আছে। কাউকে সামান্য সাহায্য করলে, ফুটপাতে হাঁটার সময় একটু রাস্তা ছেড়ে দিলে, কোনো লাইনে আগে যেতে দিলে ধন্যবাদ দিতে দিতে মুখে ফেনা তুলে ফেলে। আগের যাত্রীকে সাহায্য করেছি—এ জন্যই হয়তো ইমিগ্রেশন কাউন্টারে বসা প্রায় পঞ্চাশোর্ধ্ব স্থূলকায় শ্বেতাঙ্গ অফিসার আমার পাসপোর্ট হাতে নিয়ে কেবল একটা প্রশ্নই করেন, ‘কোন বিষয়ে পড়তে এসেছ?’ উত্তর দেওয়ার আগেই সিল মেরে পাসপোর্ট ফেরত দিতে দিতে হাস্যোজ্জ্বল ভঙ্গিতে তিনি বলেন, ‘ওয়েলকাম টু ইউনাইটেড কিংডম মাই বয়।’ অপ্রত্যাশিত এমন উষ্ণ অভ্যর্থনায় দীর্ঘ ভ্রমণক্লান্তি নিমেষে উবে গেল।
 ইমিগ্রেশন শেষ করে লাগেজসহ গেট পেরোতেই বন্ধু জগদীশের দেখা পাই। বেচারা তিন-চার ঘণ্টা ধরে অপেক্ষায় আছে। লন্ডনের বিখ্যাত টিউবে চড়ার অভিজ্ঞতা এই প্রথম। টিউব অনেকটা মেট্রোরেলের মতো—পার্থক্য হলো টিউব মাটির নিচ দিয়ে চলে। হিথরো থেকে বন্ধুর বাসা পূর্ব লন্ডনের ফরেস্ট গেটে আসতে আসতে রাত ১২টা পার হয়ে যায়। মজার ব্যাপার হলো, টিউবে সেই মধ্যরাতেও দেখলাম মেয়েরা নির্বিঘ্নে চলাফেরা করছে। কোথাও কোনো ভয়-শঙ্কার লেশমাত্র নেই। এ ছাড়া লন্ডনে নেমেই একবারের দর্শনে যে বিষয়টা দৃষ্টিগ্রাহ্য হয়, তা হলো টিউবের কামরায় দেখা জাতিগত বৈচিত্র্যের সমাহার। ধরা যাক, একেকটা কামরায় ১০ জন যাত্রী—তাদের আটজনই দেখা যাবে ভিন্ন ভিন্ন জাতির প্রতিনিধিত্ব করছে। কী চুলের বাহার, কী বেশভূষা, গাত্রবর্ণ বা ভাষা ইত্যাদি সব মিলিয়ে মনে হবে একটি আন্তর্জাতিক কামরায় বসে আছি। লন্ডনে এই বিষয় বেশ উপভোগ্য লেগেছে—এই শহরে নিজেকে সংখ্যালঘু বা আগন্তুক মনে হয় না; ফলে হীনম্মন্যতা আসে না; যেমনটা ইংল্যান্ডের অন্য শহরগুলোতে কিছুটা অনুভব হয়। শ্বেতাঙ্গ-কৃষ্ণাঙ্গ বা এশীয়দের সমান পদচারণে মুখর এখানকার পাবলিক পরিবহন। চলার পথে কেউ বই পড়ছে, কেউ মোবাইলে গেমস খেলছে, কেউ হেডফোনে গান শুনছে—যে যার জগতে আত্মমগ্ন, কর্মক্লান্ত কেউবা বাসায় ফেরার আগে একটু ঝিম মেরে ঘুমিয়ে নিচ্ছে—গন্তব্যস্থলে পৌঁছামাত্র টুপ করে নেমে পড়ছে। আবার কোনো স্টেশন থেকে এক জোড়া কপোত-কপোতী উঠে সিট না পেয়ে পরস্পরকে আলিঙ্গনরত অবস্থায় দাঁড়িয়ে থেকে জীবনের প্রতিটা মুহূর্তকে উপভোগ করে নিচ্ছে। কারও প্রতি কারও কোনো বিকার-অনুযোগ নেই।
ইমিগ্রেশন শেষ করে লাগেজসহ গেট পেরোতেই বন্ধু জগদীশের দেখা পাই। বেচারা তিন-চার ঘণ্টা ধরে অপেক্ষায় আছে। লন্ডনের বিখ্যাত টিউবে চড়ার অভিজ্ঞতা এই প্রথম। টিউব অনেকটা মেট্রোরেলের মতো—পার্থক্য হলো টিউব মাটির নিচ দিয়ে চলে। হিথরো থেকে বন্ধুর বাসা পূর্ব লন্ডনের ফরেস্ট গেটে আসতে আসতে রাত ১২টা পার হয়ে যায়। মজার ব্যাপার হলো, টিউবে সেই মধ্যরাতেও দেখলাম মেয়েরা নির্বিঘ্নে চলাফেরা করছে। কোথাও কোনো ভয়-শঙ্কার লেশমাত্র নেই। এ ছাড়া লন্ডনে নেমেই একবারের দর্শনে যে বিষয়টা দৃষ্টিগ্রাহ্য হয়, তা হলো টিউবের কামরায় দেখা জাতিগত বৈচিত্র্যের সমাহার। ধরা যাক, একেকটা কামরায় ১০ জন যাত্রী—তাদের আটজনই দেখা যাবে ভিন্ন ভিন্ন জাতির প্রতিনিধিত্ব করছে। কী চুলের বাহার, কী বেশভূষা, গাত্রবর্ণ বা ভাষা ইত্যাদি সব মিলিয়ে মনে হবে একটি আন্তর্জাতিক কামরায় বসে আছি। লন্ডনে এই বিষয় বেশ উপভোগ্য লেগেছে—এই শহরে নিজেকে সংখ্যালঘু বা আগন্তুক মনে হয় না; ফলে হীনম্মন্যতা আসে না; যেমনটা ইংল্যান্ডের অন্য শহরগুলোতে কিছুটা অনুভব হয়। শ্বেতাঙ্গ-কৃষ্ণাঙ্গ বা এশীয়দের সমান পদচারণে মুখর এখানকার পাবলিক পরিবহন। চলার পথে কেউ বই পড়ছে, কেউ মোবাইলে গেমস খেলছে, কেউ হেডফোনে গান শুনছে—যে যার জগতে আত্মমগ্ন, কর্মক্লান্ত কেউবা বাসায় ফেরার আগে একটু ঝিম মেরে ঘুমিয়ে নিচ্ছে—গন্তব্যস্থলে পৌঁছামাত্র টুপ করে নেমে পড়ছে। আবার কোনো স্টেশন থেকে এক জোড়া কপোত-কপোতী উঠে সিট না পেয়ে পরস্পরকে আলিঙ্গনরত অবস্থায় দাঁড়িয়ে থেকে জীবনের প্রতিটা মুহূর্তকে উপভোগ করে নিচ্ছে। কারও প্রতি কারও কোনো বিকার-অনুযোগ নেই।
 মূল সড়ক থেকে পাতাল স্টেশনে যাওয়ার জন্য বেশ কয়েকবার চলন্ত সিঁড়ি বেয়ে নিচে নামতে হয়। আমাদের প্রাথমিক গন্তব্য স্ট্র্যাটফোর্ড ইন্টারন্যাশনাল রেলস্টেশন। সেখান থেকে ট্যাক্সি বা উবার নিয়ে বাসায় যাওয়ার পরিকল্পনা। হিথরো থেকে ফরেস্টগেট যেতে কয়েকবার টিউব পরিবর্তন করতে হয়। এ ছাড়া উপায়ও ছিল না। কারণ, সরাসরি ট্যাক্সিতে গেলে অনেক ভাড়া। এখানকার টিউব স্টেশন মাটির গভীরে অবস্থিত। টিউবে চড়ার জন্য বেশ কয়েকটা চলন্ত সিঁড়ি দিয়ে নামতে হয়। আমাদের দেশের শপিং মলের এস্কেলেটরের চেয়ে প্রায় ১০ গুণ দৈর্ঘ্যের হবে এসব চলন্ত সিঁড়ি। লন্ডনের পাতাল রেললাইন-টিউব ব্যবস্থা এক এলাহি কারবার। এগুলো দেখলে যে কারও মনে হবে মাটির নিচে আরেক লন্ডন শহর অবস্থিত। আক্ষরিক অর্থেই, মাটির ওপরে ট্রাফিক সিগন্যালে দাঁড়িয়ে বা ফুটপাতে হাঁটতে গিয়ে মাটির নিচে টিউব-ট্রেন চলার কম্পন অনুভূত হয়। যদিও এগুলো মাটির নিচে প্রায় ২০-৩০ তলা বিল্ডিংয়ের সমান গভীরে অবস্থিত। দিন নেই, রাত নেই—মাটির ওপরে ও নিচে বিরামহীনভাবে চলে লন্ডনের পাবলিক পরিবহন।
মূল সড়ক থেকে পাতাল স্টেশনে যাওয়ার জন্য বেশ কয়েকবার চলন্ত সিঁড়ি বেয়ে নিচে নামতে হয়। আমাদের প্রাথমিক গন্তব্য স্ট্র্যাটফোর্ড ইন্টারন্যাশনাল রেলস্টেশন। সেখান থেকে ট্যাক্সি বা উবার নিয়ে বাসায় যাওয়ার পরিকল্পনা। হিথরো থেকে ফরেস্টগেট যেতে কয়েকবার টিউব পরিবর্তন করতে হয়। এ ছাড়া উপায়ও ছিল না। কারণ, সরাসরি ট্যাক্সিতে গেলে অনেক ভাড়া। এখানকার টিউব স্টেশন মাটির গভীরে অবস্থিত। টিউবে চড়ার জন্য বেশ কয়েকটা চলন্ত সিঁড়ি দিয়ে নামতে হয়। আমাদের দেশের শপিং মলের এস্কেলেটরের চেয়ে প্রায় ১০ গুণ দৈর্ঘ্যের হবে এসব চলন্ত সিঁড়ি। লন্ডনের পাতাল রেললাইন-টিউব ব্যবস্থা এক এলাহি কারবার। এগুলো দেখলে যে কারও মনে হবে মাটির নিচে আরেক লন্ডন শহর অবস্থিত। আক্ষরিক অর্থেই, মাটির ওপরে ট্রাফিক সিগন্যালে দাঁড়িয়ে বা ফুটপাতে হাঁটতে গিয়ে মাটির নিচে টিউব-ট্রেন চলার কম্পন অনুভূত হয়। যদিও এগুলো মাটির নিচে প্রায় ২০-৩০ তলা বিল্ডিংয়ের সমান গভীরে অবস্থিত। দিন নেই, রাত নেই—মাটির ওপরে ও নিচে বিরামহীনভাবে চলে লন্ডনের পাবলিক পরিবহন।
রাতে বন্ধুর বাসায় আতিথেয়তা গ্রহণ করে পরদিন রওনা দিই নিজ গন্তব্য শহর—ক্যান্টাবরিতে। ক্যান্টাবরি সাহিত্যের ছাত্রদের কাছে এক অবিস্মরণীয় নাম। ইংরেজি সাহিত্যের জনক জিওফ্রে চসারের ‘ক্যান্টাবরি টেলস’-এর সেই ক্যান্টাবরি শহরে কাটে আমার ১১ মাস। এই শহরের আনাচকানাচে ছড়িয়ে আছে ইংল্যান্ডের শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতির হাজার বছরের ইতিহাস।
ক্যান্টাবরিকে বলা হয় ‘লন্ডন বিফোর লন্ডন’। রাজধানী লন্ডন গড়ে ওঠার আগে ইংল্যান্ডের লন্ডন ছিল এই শহর। এই গল্প হবে পরের পর্বে।
(চলবে)

আলসেমি শরীরে এদিক-ওদিক চেয়ে আটকে গেল চোখ পশ্চিমান্তে। রক্তিম সূর্যের বিদায় ধীর গতিতে। খুব লাল হয়েছে, সারা দিনের জ্বলন্ত প্রহরে পেয়েছে এক অপূর্ব রূপ।
২৩ নভেম্বর ২০২৫
হুমায়ূন আহমেদ তখন ক্যানসার আক্রান্ত। যুক্তরাষ্ট্রে কেমোথেরাপি নিচ্ছেন। হঠাৎ চিকিৎসকের কাছ থেকে ছুটি নিয়ে চলে এলেন নুহাশপল্লীতে। নাটক বানাবেন। অভিনেতা ফারুক আহমেদকে ডাকলেন। নুহাশপল্লীতে নাটকের শুটিংয়ের ফাঁকে গল্প করছিলেন হুমায়ূন ও ফারুক। হুমায়ূন আহমেদ বললেন, ‘কী আশ্চর্য, তাই না ফারুক!’
১৩ নভেম্বর ২০২৫
প্রখ্যাত চলচ্চিত্রকার সত্যজিৎ রায়ের ‘হীরক রাজার দেশে’ চলচ্চিত্র মঞ্চস্থ করেছে স্কলাস্টিকার শিক্ষার্থীরা। গতকাল শুক্রবার স্কলাস্টিকা উত্তরা সিনিয়র শাখার নাটক, সংগীত ও নৃত্যকলা ক্লাবের উদ্যোগে দুই দিনব্যাপী বার্ষিক নাট্যানুষ্ঠানে এটি মঞ্চস্থ করা হয়।
০৮ নভেম্বর ২০২৫
জার্মানির ফ্রাঙ্কফুর্ট বইমেলায় উপস্থাপিত আরবি সাহিত্য নিয়ে সাম্প্রতিক এক গবেষণা ইতিহাসের বহুল প্রচলিত ধারণাকে প্রশ্নের মুখে ফেলেছে। এত দিন মনে করা হতো, আব্বাসীয় আমলের (৭৫০-১২৫৮ খ্রিষ্টাব্দ) পর আরবি সাহিত্য প্রায় ৮০০ বছর বছর স্থবির হয়ে ছিল।
২০ অক্টোবর ২০২৫তৌহিদুল হক

রক্ত লাল
আলসেমি শরীরে এদিক-ওদিক চেয়ে আটকে
গেল চোখ পশ্চিমান্তে। রক্তিম সূর্যের বিদায়
ধীর গতিতে। খুব লাল হয়েছে, সারা দিনের
জ্বলন্ত প্রহরে পেয়েছে এক অপূর্ব রূপ।
যা স্বভাববিদ্ধ, তবে কতটা উপকারী বা বাঁচিয়ে
রাখার নিরলস অভিপ্রায়। মানুষের তরে
প্রাণীর অফুরন্ত প্রাচুর্য বিস্তৃতকরণে, কিংবা
উদ্ভিদের অন্তিম প্রেমে বসন্তের অভিষেকে।
কতটা জ্বলতে হয় পরের জন্য, কতটা ফুটন্ত
শরীর নিয়ে চালিয়ে যায় সেবার পরিধি।
এক চিরন্তন শিক্ষা, আবার উদিত হয়
দিনের শুরুতে, বিদায় প্রান্তিক অপূর্ব
মায়ায়-দিনের শেষ প্রান্তে।
এতটুকু কার্পণ্য রেখে যায়নি, হয়তো মুখ
ফিরিয়ে নিবে না কোনো দিন। তবে ভাবনার
অন্তিমে শেষ দৃশ্যের সংলাপে ভেসে
ওঠে জনদরদি রাজার মুখ। যেখানে রক্ত ঝরে
বন্যার বেগে সেখানেও প্রতিদিন ফুল ফোটে ফুল হয়ে।
যত দেখি
যত দেখি তৃপ্ত হই, শীতল হয়ে
জড়িয়ে পড়ি তোমার সমস্ত শরীরে। এক অজানা
শিহরণ ছুঁয়ে যায় হৃদয়ের সমস্ত পৃষ্ঠা জুড়ে।
যেন দীর্ঘদিনের শুষ্কতা ধীরে ধীরে সরে যাচ্ছে দূরে।
হারিয়ে যাওয়া রস ফিরছে মূলে, নিয়ে যাচ্ছে আদিপর্বে।
যেমন নেয় নদীর কূল, জোয়ারের ফেনা।
ভাবনার অতলে অদ্ভুত মায়া, দীর্ঘক্ষণ মোহগ্রস্ত
করে রাখে চোখের পলক, তাকিয়ে থাকি মায়ার মায়ায়। কী অপরূপ মায়া!
সেখানেও দেখি তৃষ্ণার ব্যাকুলতা নিয়ে অপেক্ষারত কান্না।
জীবনের তল্লাটে হারিয়ে খুঁজি আজ
আমারও জীবন ছিল। মায়ায় ভরা নির্বিঘ্ন আয়োজন, কলমিলতার মতো নিষ্পাপ।
তৃপ্ত হই ঘাসে, বাতাসের বেহায়া আঘাতে
অভিমানের মোড়ক ছুড়ে ফেলে হাতে তুলে নেই
কচু পাতায় টলোমলো জলের লজ্জা। এ জীবনের চাহিদা তোমায় দেখার
প্রয়োজনে তপ্ত, হয় উত্তপ্ত অথবা সহ্যের অতীত শীতল।
এ যেন কেমন
গহিন অরণ্যে সবুজ পাতার মতো, মগজে
চিন্তার রাজ্যে ভাবের উদয়, আকুল বিন্যাসে
একটু একটু করে এগিয়ে নেয়, আবার ভরা কলসির
মতো বসিয়ে রাখে-ভবের রাজ্যে। একদিন সমস্ত ভাবনা থেকে মুক্ত হয়ে
এদিক-ওদিক চলন, জীবন্ত মরণ! মানুষ
কেন বাঁচে, কীভাবে বাঁচে-প্রশ্নের সমাধা
আজ তর্কপ্রিয় সন্ধানে, মূর্ত প্রার্থনা।
সকল প্রিয়জন পরিত্যাগে, নিগূঢ় যত্নে হৃদয়ে প্রবেশ করে
নিজের অপরিচিত চেহারা, সব জিজ্ঞাসার
অন্ত-ক্রিয়ার এক উচ্চতম বিলাস।
জীবনের মানে অর্থশুন্য ভবিতব্য! এ কী হয়?
চোখের পলকে নিষ্পাপ দৃশ্যলোক-পেছন ডাকে বারবার
যেখানে থাকে আবার দেখার ইচ্ছা, নামে যে মুক্তকরণ। মিলনকান্তির আবাস।
চতুর্মুখ সমীকরণে খেলে যায় সময়ের ঝাঁজালো সিদ্ধান্ত। কেউ কী অপ্রিয় হয় কারও?
যেখানে ভেসে ওঠে নীলপদ্ম, অতীতের নিটোল কিতাব। সে-তো মানুষের ছবি!
চলে আসুন সবজি বাজারে
মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে দেখেছি অনেক কিছু
যা মানুষের নয়। অ-মানুষের জন্ম-উত্তর বাঁচার
উপায় হতে পারে। পোশাকে সজ্জিত দেহ কতভাবে
হিংস্র হয়, গোপনে, অন্ধের গহনে।
প্রবেশের আগেই পেয়েছি সংকেত। কত নোংরা, পচা, আবর্জনায় ভরা একটি থালার মতো
পড়ে আছে সম্মুখে। কেউ কি দেখেছে?
হয়তো মেনে নিয়েছে সবাই, সবার আগে সে
যে ভেবেছে, কী বা আছে উপায়!
চারপাশে কত কিছুর ঘ্রাণ, চোখ যা বলে তা কি মেনে নেয় স্বাস্থ্যবার্তা
ফুটে আছে ফুলের মতো দোকানের পসরা। খেতে বা কেনায় বারণ বালাই নেই।
যা পাচ্ছে নিচ্ছে, অনেকে। কেউ গায়ে কেউ পেটে।
আহা! দেখার কেউ নেই!
এক অন্ধকারে হাঁটছে আমাদের পা।
কেউ কি আছে কোথাও, আলো নিয়ে হাতে? ভেবেছে কি কেউ
কেন আমাদের আয়োজনে সবাই নেই?
কেউ এসে শুধু একবার বলুক, এই নিন-আপনাদের জীবন টিকিট যা উত্তরণ।
চলে আসুন সবজির বাজারে, সবুজের খোঁজে।
ইতিহাস
আজ স্পষ্ট ঘোষণা, আমার চোখের সামনে কেউ নেই
নেই কেউ ভাবের অন্তিম ঘরে। এক অস্পৃশ্য অনুভব
ছুঁয়ে চলে, ভাসিয়ে দেয় অগণিত স্রোতের তুমুল আলিঙ্গনে।
আজ কিছু ভেবে বলছি না, সরাসরি জবাব---
আমি নই কারও!
সব বাতাসের সাথে মিশে থাকা চোখের প্রেম
ভাবনার বিলাসে জড়িয়ে পড়ার বাসনা----সকলের অগোচরে
অথবা সকলের মাঝে। জীবনের অর্থে হৃদয়ের গুড়গুড় আলাপ
ঘুটঘুটে অন্ধকারে হৃদয়ে খোলা আকাশ, শুধু
এক মুখচ্ছবি।
আজ কোনো ক্ষমা নেই---নিজের প্রতি! নিজের পাপে
হাঁটি আমি, সবার মাঝে একলা হয়ে। বেদনার
কালো রং নিয়ে। শুধু দেখে যাই, শুধু দেখতে যাই।
কত রং বিরাজ করে ভাবনার গরমিলে, স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রই।
দাঁড়িয়ে থেকেও হেঁটে যাই!
আজকের না বলা কথা, কোনো দিন বলা হবে না
হবে না দাঁড়িয়ে আবার ভাবা আর একটু বসলে
ভালো হতো। যে বসিয়ে রাখে যে আশায় বসে থাকে
সবকিছুর-ই সময় থাকে---
এরপর---ইতিহাস!

রক্ত লাল
আলসেমি শরীরে এদিক-ওদিক চেয়ে আটকে
গেল চোখ পশ্চিমান্তে। রক্তিম সূর্যের বিদায়
ধীর গতিতে। খুব লাল হয়েছে, সারা দিনের
জ্বলন্ত প্রহরে পেয়েছে এক অপূর্ব রূপ।
যা স্বভাববিদ্ধ, তবে কতটা উপকারী বা বাঁচিয়ে
রাখার নিরলস অভিপ্রায়। মানুষের তরে
প্রাণীর অফুরন্ত প্রাচুর্য বিস্তৃতকরণে, কিংবা
উদ্ভিদের অন্তিম প্রেমে বসন্তের অভিষেকে।
কতটা জ্বলতে হয় পরের জন্য, কতটা ফুটন্ত
শরীর নিয়ে চালিয়ে যায় সেবার পরিধি।
এক চিরন্তন শিক্ষা, আবার উদিত হয়
দিনের শুরুতে, বিদায় প্রান্তিক অপূর্ব
মায়ায়-দিনের শেষ প্রান্তে।
এতটুকু কার্পণ্য রেখে যায়নি, হয়তো মুখ
ফিরিয়ে নিবে না কোনো দিন। তবে ভাবনার
অন্তিমে শেষ দৃশ্যের সংলাপে ভেসে
ওঠে জনদরদি রাজার মুখ। যেখানে রক্ত ঝরে
বন্যার বেগে সেখানেও প্রতিদিন ফুল ফোটে ফুল হয়ে।
যত দেখি
যত দেখি তৃপ্ত হই, শীতল হয়ে
জড়িয়ে পড়ি তোমার সমস্ত শরীরে। এক অজানা
শিহরণ ছুঁয়ে যায় হৃদয়ের সমস্ত পৃষ্ঠা জুড়ে।
যেন দীর্ঘদিনের শুষ্কতা ধীরে ধীরে সরে যাচ্ছে দূরে।
হারিয়ে যাওয়া রস ফিরছে মূলে, নিয়ে যাচ্ছে আদিপর্বে।
যেমন নেয় নদীর কূল, জোয়ারের ফেনা।
ভাবনার অতলে অদ্ভুত মায়া, দীর্ঘক্ষণ মোহগ্রস্ত
করে রাখে চোখের পলক, তাকিয়ে থাকি মায়ার মায়ায়। কী অপরূপ মায়া!
সেখানেও দেখি তৃষ্ণার ব্যাকুলতা নিয়ে অপেক্ষারত কান্না।
জীবনের তল্লাটে হারিয়ে খুঁজি আজ
আমারও জীবন ছিল। মায়ায় ভরা নির্বিঘ্ন আয়োজন, কলমিলতার মতো নিষ্পাপ।
তৃপ্ত হই ঘাসে, বাতাসের বেহায়া আঘাতে
অভিমানের মোড়ক ছুড়ে ফেলে হাতে তুলে নেই
কচু পাতায় টলোমলো জলের লজ্জা। এ জীবনের চাহিদা তোমায় দেখার
প্রয়োজনে তপ্ত, হয় উত্তপ্ত অথবা সহ্যের অতীত শীতল।
এ যেন কেমন
গহিন অরণ্যে সবুজ পাতার মতো, মগজে
চিন্তার রাজ্যে ভাবের উদয়, আকুল বিন্যাসে
একটু একটু করে এগিয়ে নেয়, আবার ভরা কলসির
মতো বসিয়ে রাখে-ভবের রাজ্যে। একদিন সমস্ত ভাবনা থেকে মুক্ত হয়ে
এদিক-ওদিক চলন, জীবন্ত মরণ! মানুষ
কেন বাঁচে, কীভাবে বাঁচে-প্রশ্নের সমাধা
আজ তর্কপ্রিয় সন্ধানে, মূর্ত প্রার্থনা।
সকল প্রিয়জন পরিত্যাগে, নিগূঢ় যত্নে হৃদয়ে প্রবেশ করে
নিজের অপরিচিত চেহারা, সব জিজ্ঞাসার
অন্ত-ক্রিয়ার এক উচ্চতম বিলাস।
জীবনের মানে অর্থশুন্য ভবিতব্য! এ কী হয়?
চোখের পলকে নিষ্পাপ দৃশ্যলোক-পেছন ডাকে বারবার
যেখানে থাকে আবার দেখার ইচ্ছা, নামে যে মুক্তকরণ। মিলনকান্তির আবাস।
চতুর্মুখ সমীকরণে খেলে যায় সময়ের ঝাঁজালো সিদ্ধান্ত। কেউ কী অপ্রিয় হয় কারও?
যেখানে ভেসে ওঠে নীলপদ্ম, অতীতের নিটোল কিতাব। সে-তো মানুষের ছবি!
চলে আসুন সবজি বাজারে
মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে দেখেছি অনেক কিছু
যা মানুষের নয়। অ-মানুষের জন্ম-উত্তর বাঁচার
উপায় হতে পারে। পোশাকে সজ্জিত দেহ কতভাবে
হিংস্র হয়, গোপনে, অন্ধের গহনে।
প্রবেশের আগেই পেয়েছি সংকেত। কত নোংরা, পচা, আবর্জনায় ভরা একটি থালার মতো
পড়ে আছে সম্মুখে। কেউ কি দেখেছে?
হয়তো মেনে নিয়েছে সবাই, সবার আগে সে
যে ভেবেছে, কী বা আছে উপায়!
চারপাশে কত কিছুর ঘ্রাণ, চোখ যা বলে তা কি মেনে নেয় স্বাস্থ্যবার্তা
ফুটে আছে ফুলের মতো দোকানের পসরা। খেতে বা কেনায় বারণ বালাই নেই।
যা পাচ্ছে নিচ্ছে, অনেকে। কেউ গায়ে কেউ পেটে।
আহা! দেখার কেউ নেই!
এক অন্ধকারে হাঁটছে আমাদের পা।
কেউ কি আছে কোথাও, আলো নিয়ে হাতে? ভেবেছে কি কেউ
কেন আমাদের আয়োজনে সবাই নেই?
কেউ এসে শুধু একবার বলুক, এই নিন-আপনাদের জীবন টিকিট যা উত্তরণ।
চলে আসুন সবজির বাজারে, সবুজের খোঁজে।
ইতিহাস
আজ স্পষ্ট ঘোষণা, আমার চোখের সামনে কেউ নেই
নেই কেউ ভাবের অন্তিম ঘরে। এক অস্পৃশ্য অনুভব
ছুঁয়ে চলে, ভাসিয়ে দেয় অগণিত স্রোতের তুমুল আলিঙ্গনে।
আজ কিছু ভেবে বলছি না, সরাসরি জবাব---
আমি নই কারও!
সব বাতাসের সাথে মিশে থাকা চোখের প্রেম
ভাবনার বিলাসে জড়িয়ে পড়ার বাসনা----সকলের অগোচরে
অথবা সকলের মাঝে। জীবনের অর্থে হৃদয়ের গুড়গুড় আলাপ
ঘুটঘুটে অন্ধকারে হৃদয়ে খোলা আকাশ, শুধু
এক মুখচ্ছবি।
আজ কোনো ক্ষমা নেই---নিজের প্রতি! নিজের পাপে
হাঁটি আমি, সবার মাঝে একলা হয়ে। বেদনার
কালো রং নিয়ে। শুধু দেখে যাই, শুধু দেখতে যাই।
কত রং বিরাজ করে ভাবনার গরমিলে, স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রই।
দাঁড়িয়ে থেকেও হেঁটে যাই!
আজকের না বলা কথা, কোনো দিন বলা হবে না
হবে না দাঁড়িয়ে আবার ভাবা আর একটু বসলে
ভালো হতো। যে বসিয়ে রাখে যে আশায় বসে থাকে
সবকিছুর-ই সময় থাকে---
এরপর---ইতিহাস!

বুড়িগঙ্গার পাড় থেকে টেমসের তীরে আসার প্রায় এক বছর হয়ে এল। গত বছর অক্টোবরে সূর্যালোক উদ্ভাসিত প্রাণচাঞ্চল্যে ভরপুর এক দেশ ছেড়ে সাত সমুদ্র তেরো নদীর পাড়ে হাড়কাঁপানো ধূসর ভূমিতে পদার্পণ করি। আমার আগমনের সময়টায় বিলাতে শীত আসি-আসি করছে—জাঁকিয়ে বসেনি। অভিজ্ঞ ব্যক্তিরা আগেই বলেছিলেন, ইউরোপের শীত কোনো ছেলেখ
১৬ সেপ্টেম্বর ২০২২
হুমায়ূন আহমেদ তখন ক্যানসার আক্রান্ত। যুক্তরাষ্ট্রে কেমোথেরাপি নিচ্ছেন। হঠাৎ চিকিৎসকের কাছ থেকে ছুটি নিয়ে চলে এলেন নুহাশপল্লীতে। নাটক বানাবেন। অভিনেতা ফারুক আহমেদকে ডাকলেন। নুহাশপল্লীতে নাটকের শুটিংয়ের ফাঁকে গল্প করছিলেন হুমায়ূন ও ফারুক। হুমায়ূন আহমেদ বললেন, ‘কী আশ্চর্য, তাই না ফারুক!’
১৩ নভেম্বর ২০২৫
প্রখ্যাত চলচ্চিত্রকার সত্যজিৎ রায়ের ‘হীরক রাজার দেশে’ চলচ্চিত্র মঞ্চস্থ করেছে স্কলাস্টিকার শিক্ষার্থীরা। গতকাল শুক্রবার স্কলাস্টিকা উত্তরা সিনিয়র শাখার নাটক, সংগীত ও নৃত্যকলা ক্লাবের উদ্যোগে দুই দিনব্যাপী বার্ষিক নাট্যানুষ্ঠানে এটি মঞ্চস্থ করা হয়।
০৮ নভেম্বর ২০২৫
জার্মানির ফ্রাঙ্কফুর্ট বইমেলায় উপস্থাপিত আরবি সাহিত্য নিয়ে সাম্প্রতিক এক গবেষণা ইতিহাসের বহুল প্রচলিত ধারণাকে প্রশ্নের মুখে ফেলেছে। এত দিন মনে করা হতো, আব্বাসীয় আমলের (৭৫০-১২৫৮ খ্রিষ্টাব্দ) পর আরবি সাহিত্য প্রায় ৮০০ বছর বছর স্থবির হয়ে ছিল।
২০ অক্টোবর ২০২৫জন্মদিনের শ্রদ্ধাঞ্জলি
নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা

হুমায়ূন আহমেদ তখন ক্যানসার আক্রান্ত। যুক্তরাষ্ট্রে কেমোথেরাপি নিচ্ছেন। হঠাৎ চিকিৎসকের কাছ থেকে ছুটি নিয়ে চলে এলেন নুহাশপল্লীতে। নাটক বানাবেন। অভিনেতা ফারুক আহমেদকে ডাকলেন। নুহাশপল্লীতে নাটকের শুটিংয়ের ফাঁকে গল্প করছিলেন হুমায়ূন ও ফারুক। হুমায়ূন আহমেদ বললেন, ‘কী আশ্চর্য, তাই না ফারুক!’ জবাবে ফারুক বললেন, ‘কী আশ্চর্য ভাই?’ হুমায়ূন আহমেদ বললেন, ‘এই যে প্রকৃতি, জোছনা, বৃষ্টি, নদী— কী সুন্দর! একদিন হয়তো আমি এসব আর দেখতে পারব না। একুশের বইমেলা হবে। লোকেদের ভিড়, আড্ডা; আমি সেখানে থাকব না। এটা কি মেনে নেওয়া যায়! হায় রে জীবন!’
‘আমার না বলা কথা’ বইয়ে ফারুক আহমেদ এই স্মৃতিচারণ করেছেন। লিখেছেন, ‘আমি কিছু না বলে মূর্তির মতো বসে রইলাম। একসময় তাকিয়ে দেখলাম, হুমায়ূন ভাইয়ের দুচোখের কোনায় পানি।’
হুমায়ূন আহমেদ নেই। তবে তিনি রয়েছেন দেশের তরুণদের মনে। যে বইমেলায় তিনি থাকবেন না বলে আক্ষেপ, সেই বইমেলায় তাঁর বইয়ের স্টলে তরুণদের ঢলের মধ্যে আছেন।
নেত্রকোনার মোহনগঞ্জে হুমায়ূন আহমেদের জন্ম এই দিনে (১৩ নভেম্বর); ভারত ভাগের এক বছর পরে ১৯৪৮ সালে। ছোট সময়ে তাঁর নাম ছিল শামসুর রহমান। তাঁর বাবা ছেলেমেয়েদের নাম পাল্টে ফেলতেন। তাঁর নাম পাল্টে রাখেন হুমায়ূন আহমেদ। হিমু, মিসির আলি, শুভ্রর মতো চরিত্রের স্রষ্টা তিনি। শুধু কথাসাহিত্যেই নয়; ‘বহুব্রীহি’, ‘অয়োময়’, ‘কোথাও কেউ নেই’,
‘আজ রবিবার’-এর মতো নাটক বানিয়েছেন, তৈরি করেছেন ‘আগুনের পরশমণি’, ‘শ্যামল ছায়া’র মতো চলচ্চিত্র।
হুমায়ূন আহমেদ বৃষ্টি, জোছনা ভালোবাসতেন। তাঁর লেখায় সেসব উঠে এসেছে বারবার। ২০১২ সালের জুলাইয়ে বর্ষাতেই তিনি পাড়ি জমিয়েছিলেন ওপারে।
তিনি নেই। কিন্তু তাঁর লেখায় উঠে আসা চান্নিপসর, বৃষ্টি বিলাস আজও আছে তরুণদের মনে। ফারুক আহমেদ তাঁর ওই বইয়ে হুমায়ূন আহমেদকে নিয়ে আরেকটি স্মৃতিচারণ করেছিলেন এভাবে—‘এক বিকেলে শুটিং শেষে তাঁর প্রিয় লিচুগাছের দিকে তাকিয়ে আছেন হুমায়ূন। সেখানে ঝুলছে পাকা লিচু। তিনি তাঁর কেয়ারটেকার মুশাররফকে ডেকে গ্রামের ছোট ছেলেমেয়েদের ডেকে নিয়ে এলেন। তাদের বললেন, গাছে উঠে যে যত পারে লিচু খেতে। বাচ্চারা কেউ গাছে উঠে লিচু খাচ্ছে, হইচই করছে। কেউ পকেটে ভরছে। হুমায়ূন আহমেদ অবাক হয়ে সেই লিচু খাওয়া দেখতে লাগলেন।’
ফারুক আহমেদ লিখেছেন, ‘হুমায়ূন ভাই একসময় আমাকে বললেন, এমন সুন্দর দৃশ্য তুমি কখনো দেখেছো? এমন ভালো লাগার অনুভূতি কি অন্য কোনোভাবে পাওয়া যায়? আমি কী বলব বুঝতে পারছিলাম না। হঠাৎ বললাম, না ভাই এমন ভালো লাগার অনুভূতি কোনোভাবেই পাওয়া যায় না।’
হুমায়ূন আহমেদের জন্মদিন ঘিরে রাজধানীসহ জন্মস্থান নেত্রকোনাতে রয়েছে নানা আয়োজন। নেত্রকোনার কেন্দুয়া উপজেলার রোয়াইলবাড়ি ইউনিয়নের কুতুবপুরে হুমায়ূন আহমেদ প্রতিষ্ঠিত শহীদ স্মৃতি বিদ্যাপীঠ এবং এলাকাবাসীর উদ্যোগে এসব কর্মসূচি পালন করা হবে। সকালে বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা কোরআন খতম করবেন। এরপর শহীদ স্মৃতি বিদ্যাপীঠ প্রাঙ্গণ থেকে শিক্ষক-শিক্ষার্থী, এলাকাবাসী এবং হুমায়ূনভক্তদের আনন্দ শোভাযাত্রা বের হবে। পরে লেখকের প্রতিকৃতিতে পুষ্পমাল্য অর্পণ, জন্মদিনের কেক কাটা, বৃক্ষরোপণ, কুইজ, হুমায়ূন আহমেদের রচিত নাটক ও সিনেমার অংশবিশেষ নিয়ে অভিনয়, চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা, পুরস্কার বিতরণ এবং আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হবে। এ ছাড়া রাজধানীতে হুমায়ূন আহমেদের চলচ্চিত্র নিয়ে চলচ্চিত্র সপ্তাহ, হুমায়ূন প্রতিযোগিতা, হুমায়ূন জন্মোৎসব, টেলিভিশন চ্যানেলে নাটক ও অনুষ্ঠান প্রচারসহ নানা আয়োজনে মুখর থাকছে দিনটি।

হুমায়ূন আহমেদ তখন ক্যানসার আক্রান্ত। যুক্তরাষ্ট্রে কেমোথেরাপি নিচ্ছেন। হঠাৎ চিকিৎসকের কাছ থেকে ছুটি নিয়ে চলে এলেন নুহাশপল্লীতে। নাটক বানাবেন। অভিনেতা ফারুক আহমেদকে ডাকলেন। নুহাশপল্লীতে নাটকের শুটিংয়ের ফাঁকে গল্প করছিলেন হুমায়ূন ও ফারুক। হুমায়ূন আহমেদ বললেন, ‘কী আশ্চর্য, তাই না ফারুক!’ জবাবে ফারুক বললেন, ‘কী আশ্চর্য ভাই?’ হুমায়ূন আহমেদ বললেন, ‘এই যে প্রকৃতি, জোছনা, বৃষ্টি, নদী— কী সুন্দর! একদিন হয়তো আমি এসব আর দেখতে পারব না। একুশের বইমেলা হবে। লোকেদের ভিড়, আড্ডা; আমি সেখানে থাকব না। এটা কি মেনে নেওয়া যায়! হায় রে জীবন!’
‘আমার না বলা কথা’ বইয়ে ফারুক আহমেদ এই স্মৃতিচারণ করেছেন। লিখেছেন, ‘আমি কিছু না বলে মূর্তির মতো বসে রইলাম। একসময় তাকিয়ে দেখলাম, হুমায়ূন ভাইয়ের দুচোখের কোনায় পানি।’
হুমায়ূন আহমেদ নেই। তবে তিনি রয়েছেন দেশের তরুণদের মনে। যে বইমেলায় তিনি থাকবেন না বলে আক্ষেপ, সেই বইমেলায় তাঁর বইয়ের স্টলে তরুণদের ঢলের মধ্যে আছেন।
নেত্রকোনার মোহনগঞ্জে হুমায়ূন আহমেদের জন্ম এই দিনে (১৩ নভেম্বর); ভারত ভাগের এক বছর পরে ১৯৪৮ সালে। ছোট সময়ে তাঁর নাম ছিল শামসুর রহমান। তাঁর বাবা ছেলেমেয়েদের নাম পাল্টে ফেলতেন। তাঁর নাম পাল্টে রাখেন হুমায়ূন আহমেদ। হিমু, মিসির আলি, শুভ্রর মতো চরিত্রের স্রষ্টা তিনি। শুধু কথাসাহিত্যেই নয়; ‘বহুব্রীহি’, ‘অয়োময়’, ‘কোথাও কেউ নেই’,
‘আজ রবিবার’-এর মতো নাটক বানিয়েছেন, তৈরি করেছেন ‘আগুনের পরশমণি’, ‘শ্যামল ছায়া’র মতো চলচ্চিত্র।
হুমায়ূন আহমেদ বৃষ্টি, জোছনা ভালোবাসতেন। তাঁর লেখায় সেসব উঠে এসেছে বারবার। ২০১২ সালের জুলাইয়ে বর্ষাতেই তিনি পাড়ি জমিয়েছিলেন ওপারে।
তিনি নেই। কিন্তু তাঁর লেখায় উঠে আসা চান্নিপসর, বৃষ্টি বিলাস আজও আছে তরুণদের মনে। ফারুক আহমেদ তাঁর ওই বইয়ে হুমায়ূন আহমেদকে নিয়ে আরেকটি স্মৃতিচারণ করেছিলেন এভাবে—‘এক বিকেলে শুটিং শেষে তাঁর প্রিয় লিচুগাছের দিকে তাকিয়ে আছেন হুমায়ূন। সেখানে ঝুলছে পাকা লিচু। তিনি তাঁর কেয়ারটেকার মুশাররফকে ডেকে গ্রামের ছোট ছেলেমেয়েদের ডেকে নিয়ে এলেন। তাদের বললেন, গাছে উঠে যে যত পারে লিচু খেতে। বাচ্চারা কেউ গাছে উঠে লিচু খাচ্ছে, হইচই করছে। কেউ পকেটে ভরছে। হুমায়ূন আহমেদ অবাক হয়ে সেই লিচু খাওয়া দেখতে লাগলেন।’
ফারুক আহমেদ লিখেছেন, ‘হুমায়ূন ভাই একসময় আমাকে বললেন, এমন সুন্দর দৃশ্য তুমি কখনো দেখেছো? এমন ভালো লাগার অনুভূতি কি অন্য কোনোভাবে পাওয়া যায়? আমি কী বলব বুঝতে পারছিলাম না। হঠাৎ বললাম, না ভাই এমন ভালো লাগার অনুভূতি কোনোভাবেই পাওয়া যায় না।’
হুমায়ূন আহমেদের জন্মদিন ঘিরে রাজধানীসহ জন্মস্থান নেত্রকোনাতে রয়েছে নানা আয়োজন। নেত্রকোনার কেন্দুয়া উপজেলার রোয়াইলবাড়ি ইউনিয়নের কুতুবপুরে হুমায়ূন আহমেদ প্রতিষ্ঠিত শহীদ স্মৃতি বিদ্যাপীঠ এবং এলাকাবাসীর উদ্যোগে এসব কর্মসূচি পালন করা হবে। সকালে বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা কোরআন খতম করবেন। এরপর শহীদ স্মৃতি বিদ্যাপীঠ প্রাঙ্গণ থেকে শিক্ষক-শিক্ষার্থী, এলাকাবাসী এবং হুমায়ূনভক্তদের আনন্দ শোভাযাত্রা বের হবে। পরে লেখকের প্রতিকৃতিতে পুষ্পমাল্য অর্পণ, জন্মদিনের কেক কাটা, বৃক্ষরোপণ, কুইজ, হুমায়ূন আহমেদের রচিত নাটক ও সিনেমার অংশবিশেষ নিয়ে অভিনয়, চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা, পুরস্কার বিতরণ এবং আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হবে। এ ছাড়া রাজধানীতে হুমায়ূন আহমেদের চলচ্চিত্র নিয়ে চলচ্চিত্র সপ্তাহ, হুমায়ূন প্রতিযোগিতা, হুমায়ূন জন্মোৎসব, টেলিভিশন চ্যানেলে নাটক ও অনুষ্ঠান প্রচারসহ নানা আয়োজনে মুখর থাকছে দিনটি।

বুড়িগঙ্গার পাড় থেকে টেমসের তীরে আসার প্রায় এক বছর হয়ে এল। গত বছর অক্টোবরে সূর্যালোক উদ্ভাসিত প্রাণচাঞ্চল্যে ভরপুর এক দেশ ছেড়ে সাত সমুদ্র তেরো নদীর পাড়ে হাড়কাঁপানো ধূসর ভূমিতে পদার্পণ করি। আমার আগমনের সময়টায় বিলাতে শীত আসি-আসি করছে—জাঁকিয়ে বসেনি। অভিজ্ঞ ব্যক্তিরা আগেই বলেছিলেন, ইউরোপের শীত কোনো ছেলেখ
১৬ সেপ্টেম্বর ২০২২
আলসেমি শরীরে এদিক-ওদিক চেয়ে আটকে গেল চোখ পশ্চিমান্তে। রক্তিম সূর্যের বিদায় ধীর গতিতে। খুব লাল হয়েছে, সারা দিনের জ্বলন্ত প্রহরে পেয়েছে এক অপূর্ব রূপ।
২৩ নভেম্বর ২০২৫
প্রখ্যাত চলচ্চিত্রকার সত্যজিৎ রায়ের ‘হীরক রাজার দেশে’ চলচ্চিত্র মঞ্চস্থ করেছে স্কলাস্টিকার শিক্ষার্থীরা। গতকাল শুক্রবার স্কলাস্টিকা উত্তরা সিনিয়র শাখার নাটক, সংগীত ও নৃত্যকলা ক্লাবের উদ্যোগে দুই দিনব্যাপী বার্ষিক নাট্যানুষ্ঠানে এটি মঞ্চস্থ করা হয়।
০৮ নভেম্বর ২০২৫
জার্মানির ফ্রাঙ্কফুর্ট বইমেলায় উপস্থাপিত আরবি সাহিত্য নিয়ে সাম্প্রতিক এক গবেষণা ইতিহাসের বহুল প্রচলিত ধারণাকে প্রশ্নের মুখে ফেলেছে। এত দিন মনে করা হতো, আব্বাসীয় আমলের (৭৫০-১২৫৮ খ্রিষ্টাব্দ) পর আরবি সাহিত্য প্রায় ৮০০ বছর বছর স্থবির হয়ে ছিল।
২০ অক্টোবর ২০২৫নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা

প্রখ্যাত চলচ্চিত্রকার সত্যজিৎ রায়ের ‘হীরক রাজার দেশে’ চলচ্চিত্র মঞ্চস্থ করেছে স্কলাস্টিকার শিক্ষার্থীরা। গতকাল শুক্রবার স্কলাস্টিকা উত্তরা সিনিয়র শাখার নাটক, সংগীত ও নৃত্যকলা ক্লাবের উদ্যোগে দুই দিনব্যাপী বার্ষিক নাট্যানুষ্ঠানে এটি মঞ্চস্থ করা হয়।
মঞ্চনাট্যটি স্কলাস্টিকার প্রতিষ্ঠাতা ইয়াসমিন মুরশেদকে উৎসর্গ করা হয়।

স্কুলের এসটিএম মিলনায়তন প্রতিষ্ঠার রজতজয়ন্তী উদ্যাপনকে সামনে রেখে আয়োজিত এ নাট্যানুষ্ঠানের সমাপনী দিনে বিশেষ অতিথি ছিলেন নাট্যব্যক্তিত্ব আবুল হায়াত, দিলারা জামান ও আফজাল হোসেন। অনুষ্ঠানে আরও বক্তব্য দেন স্কলাস্টিকা উত্তরা সিনিয়র শাখার অধ্যক্ষ ফারাহ্ সোফিয়া আহমেদ।
হীরক রাজার দেশে নাটকটির নির্দেশনায় ছিলেন কাজী তৌফিকুল ইসলাম ইমন। প্রোডাকশন ম্যানেজারের দায়িত্ব পালন করেন শৈলী পারমিতা নীলপদ্ম। সংগীত পরিচালনা করেন গাজী মুন্নোফ, ইলিয়াস খান ও পলাশ নাথ লোচন। নৃত্য পরিচালনায় ছিলেন শাম্মী ইয়াসমিন ঝিনুক ও ফরহাদ আহমেদ শামিম।
নাটকের বিভিন্ন চরিত্রে অভিনয় করেন নাজিফা ওয়াযিহা আহমেদ, আরিয়াদ রহমান, আজিয়াদ রহমান, বাজনীন রহমান, মোহম্মদ সফির চৌধুরী, ফাহিম আহম্মেদ, সৈয়দ কাফশাত তাইয়ুশ হামদ ও তাজরীবা নওফাত প্রমুখ।
শিক্ষার্থী, অভিভাবক ও শিক্ষকেরা অনুষ্ঠানে শিক্ষার্থীদের পরিবেশিত অভিনয়, গান ও নাচ উপভোগ করেন।

প্রখ্যাত চলচ্চিত্রকার সত্যজিৎ রায়ের ‘হীরক রাজার দেশে’ চলচ্চিত্র মঞ্চস্থ করেছে স্কলাস্টিকার শিক্ষার্থীরা। গতকাল শুক্রবার স্কলাস্টিকা উত্তরা সিনিয়র শাখার নাটক, সংগীত ও নৃত্যকলা ক্লাবের উদ্যোগে দুই দিনব্যাপী বার্ষিক নাট্যানুষ্ঠানে এটি মঞ্চস্থ করা হয়।
মঞ্চনাট্যটি স্কলাস্টিকার প্রতিষ্ঠাতা ইয়াসমিন মুরশেদকে উৎসর্গ করা হয়।

স্কুলের এসটিএম মিলনায়তন প্রতিষ্ঠার রজতজয়ন্তী উদ্যাপনকে সামনে রেখে আয়োজিত এ নাট্যানুষ্ঠানের সমাপনী দিনে বিশেষ অতিথি ছিলেন নাট্যব্যক্তিত্ব আবুল হায়াত, দিলারা জামান ও আফজাল হোসেন। অনুষ্ঠানে আরও বক্তব্য দেন স্কলাস্টিকা উত্তরা সিনিয়র শাখার অধ্যক্ষ ফারাহ্ সোফিয়া আহমেদ।
হীরক রাজার দেশে নাটকটির নির্দেশনায় ছিলেন কাজী তৌফিকুল ইসলাম ইমন। প্রোডাকশন ম্যানেজারের দায়িত্ব পালন করেন শৈলী পারমিতা নীলপদ্ম। সংগীত পরিচালনা করেন গাজী মুন্নোফ, ইলিয়াস খান ও পলাশ নাথ লোচন। নৃত্য পরিচালনায় ছিলেন শাম্মী ইয়াসমিন ঝিনুক ও ফরহাদ আহমেদ শামিম।
নাটকের বিভিন্ন চরিত্রে অভিনয় করেন নাজিফা ওয়াযিহা আহমেদ, আরিয়াদ রহমান, আজিয়াদ রহমান, বাজনীন রহমান, মোহম্মদ সফির চৌধুরী, ফাহিম আহম্মেদ, সৈয়দ কাফশাত তাইয়ুশ হামদ ও তাজরীবা নওফাত প্রমুখ।
শিক্ষার্থী, অভিভাবক ও শিক্ষকেরা অনুষ্ঠানে শিক্ষার্থীদের পরিবেশিত অভিনয়, গান ও নাচ উপভোগ করেন।

বুড়িগঙ্গার পাড় থেকে টেমসের তীরে আসার প্রায় এক বছর হয়ে এল। গত বছর অক্টোবরে সূর্যালোক উদ্ভাসিত প্রাণচাঞ্চল্যে ভরপুর এক দেশ ছেড়ে সাত সমুদ্র তেরো নদীর পাড়ে হাড়কাঁপানো ধূসর ভূমিতে পদার্পণ করি। আমার আগমনের সময়টায় বিলাতে শীত আসি-আসি করছে—জাঁকিয়ে বসেনি। অভিজ্ঞ ব্যক্তিরা আগেই বলেছিলেন, ইউরোপের শীত কোনো ছেলেখ
১৬ সেপ্টেম্বর ২০২২
আলসেমি শরীরে এদিক-ওদিক চেয়ে আটকে গেল চোখ পশ্চিমান্তে। রক্তিম সূর্যের বিদায় ধীর গতিতে। খুব লাল হয়েছে, সারা দিনের জ্বলন্ত প্রহরে পেয়েছে এক অপূর্ব রূপ।
২৩ নভেম্বর ২০২৫
হুমায়ূন আহমেদ তখন ক্যানসার আক্রান্ত। যুক্তরাষ্ট্রে কেমোথেরাপি নিচ্ছেন। হঠাৎ চিকিৎসকের কাছ থেকে ছুটি নিয়ে চলে এলেন নুহাশপল্লীতে। নাটক বানাবেন। অভিনেতা ফারুক আহমেদকে ডাকলেন। নুহাশপল্লীতে নাটকের শুটিংয়ের ফাঁকে গল্প করছিলেন হুমায়ূন ও ফারুক। হুমায়ূন আহমেদ বললেন, ‘কী আশ্চর্য, তাই না ফারুক!’
১৩ নভেম্বর ২০২৫
জার্মানির ফ্রাঙ্কফুর্ট বইমেলায় উপস্থাপিত আরবি সাহিত্য নিয়ে সাম্প্রতিক এক গবেষণা ইতিহাসের বহুল প্রচলিত ধারণাকে প্রশ্নের মুখে ফেলেছে। এত দিন মনে করা হতো, আব্বাসীয় আমলের (৭৫০-১২৫৮ খ্রিষ্টাব্দ) পর আরবি সাহিত্য প্রায় ৮০০ বছর বছর স্থবির হয়ে ছিল।
২০ অক্টোবর ২০২৫আজকের পত্রিকা ডেস্ক

জার্মানির ফ্রাঙ্কফুর্ট বইমেলায় উপস্থাপিত আরবি সাহিত্য নিয়ে সাম্প্রতিক এক গবেষণা ইতিহাসের বহুল প্রচলিত ধারণাকে প্রশ্নের মুখে ফেলেছে। এত দিন মনে করা হতো, আব্বাসীয় আমলের (৭৫০-১২৫৮ খ্রিষ্টাব্দ) পর আরবি সাহিত্য প্রায় ৮০০ বছর বছর স্থবির হয়ে ছিল। কিন্তু ভাষাবিদ ও সাহিত্য ইতিহাসবিদদের মতে, এই ধারণা আসলে পশ্চিমা দৃষ্টিকোণ থেকে তৈরি এক ‘ঔপনিবেশিক কল্পনা’ মাত্র। বাস্তবে আরবি সাহিত্য কখনোই থেমে যায়নি।
প্রচলিত ধারণা অনুযায়ী, অষ্টম শতাব্দীতে আব্বাসীয় খলিফাদের অধীনে বিজ্ঞান, দর্শন ও কবিতার কেন্দ্র হয়ে উঠেছিল বাগদাদ। আবু নুয়াস, আল-মুতানাব্বি, আল-ফারাবি ও ইবনে সিনার মতো কবি ও দার্শনিকদের হাত ধরে শুরু হয়েছিল এক স্বর্ণযুগ। ঊনবিংশ শতাব্দীর ইউরোপীয় গবেষকেরা—যেমন ফরাসি চিন্তাবিদ আর্নেস্ট রেনাঁ ও ডাচ ইতিহাসবিদ রেইনহার্ট দোজি সেই আমলটিকেই আরবি বুদ্ধিবৃত্তিক জীবনের শিখর বলে স্বীকার করেছিলেন এবং দাবি করেছিলেন, একাদশ শতাব্দীর পর এই ধারাবাহিকতার পতন ঘটে। তাঁদের মতে, এরপর প্রায় ৮০০ বছর আরবে আর কোনো গুরুত্বপূর্ণ সাহিত্যিক বা দার্শনিক কাজ হয়নি—যতক্ষণ না ইউরোপে রেনেসাঁ শুরু হয়।
কিন্তু আধুনিক গবেষকেরা বলছেন, এই ধারণা সরলীকৃত ও পক্ষপাতদুষ্ট। ফ্রাঙ্কফুর্ট আন্তর্জাতিক বইমেলায় শেখ জায়েদ বুক অ্যাওয়ার্ডের আয়োজিত এক আলোচনায় ভাষাবিদেরা দাবি করেছেন, আরবি রচনা শৈলী কখনো বিলুপ্ত হয়নি; বরং তা ধারাবাহিকভাবে কপি, অনুবাদ ও পাঠের মাধ্যমে বেঁচে ছিল।
জার্মান গবেষক বেয়াট্রিস গ্রুন্ডলার তাঁর ‘দ্য রাইজ অব দ্য অ্যারাবিক বুক’ গ্রন্থে দাবি করেছেন, আরবি সাহিত্যে ‘হারানো শতাব্দী’ হিসেবে যে ধারণাটি প্রচলিত আছে তা আসলে গাল-গল্প। এই বইটি এবারের শেখ জায়েদ পুরস্কারের শর্টলিস্টে রয়েছে। গ্রুন্ডলার এতে দেখিয়েছেন, নবম শতাব্দীর বাগদাদে বইয়ের ব্যবসা, কপিকারদের প্রতিযোগিতা, জনসম্মুখে পাঠ ও লেখার প্রচলন—সবই ছিল আধুনিক প্রকাশনা সংস্কৃতির পূর্বসূরি। তিনি মত দিয়েছেন, ‘বাগদাদের রাস্তায় হাঁটলে আপনি দেখতেন লোকেরা হস্তলিপি বিক্রি করছে, বিরামচিহ্ন নিয়ে তর্ক করছে—এ যেন এক জীবন্ত প্রকাশনা বাজার।’
গবেষণা বলছে, আরবি সাহিত্য আসলে কখনো এক জায়গায় স্থির থাকেনি। এর কেন্দ্র এক সময় বাগদাদ থেকে কায়রো, দামেস্ক ও আন্দালুসিয়ায় স্থানান্তরিত হয়। কিন্তু ধারাটি অব্যাহতই থাকে। নতুন ঘরানা তৈরি হয়, পুরোনো ঘরানা রূপান্তরিত হয়।
ফরাসি অধ্যাপক হাকান ওজকান তাঁর গবেষণায় দেখিয়েছেন, ‘জাজাল’ নামের কথ্য ছন্দভিত্তিক কবিতার ধারা আব্বাসীয় যুগের পরও বিকশিত হতে থাকে। তাঁর মতে, ‘এই কবিরা নিয়ম ভেঙে নতুন রূপ দিয়েছে—তাঁদের ছন্দ ও ব্যঙ্গ আধুনিক র্যাপের মতো প্রাণবন্ত।’
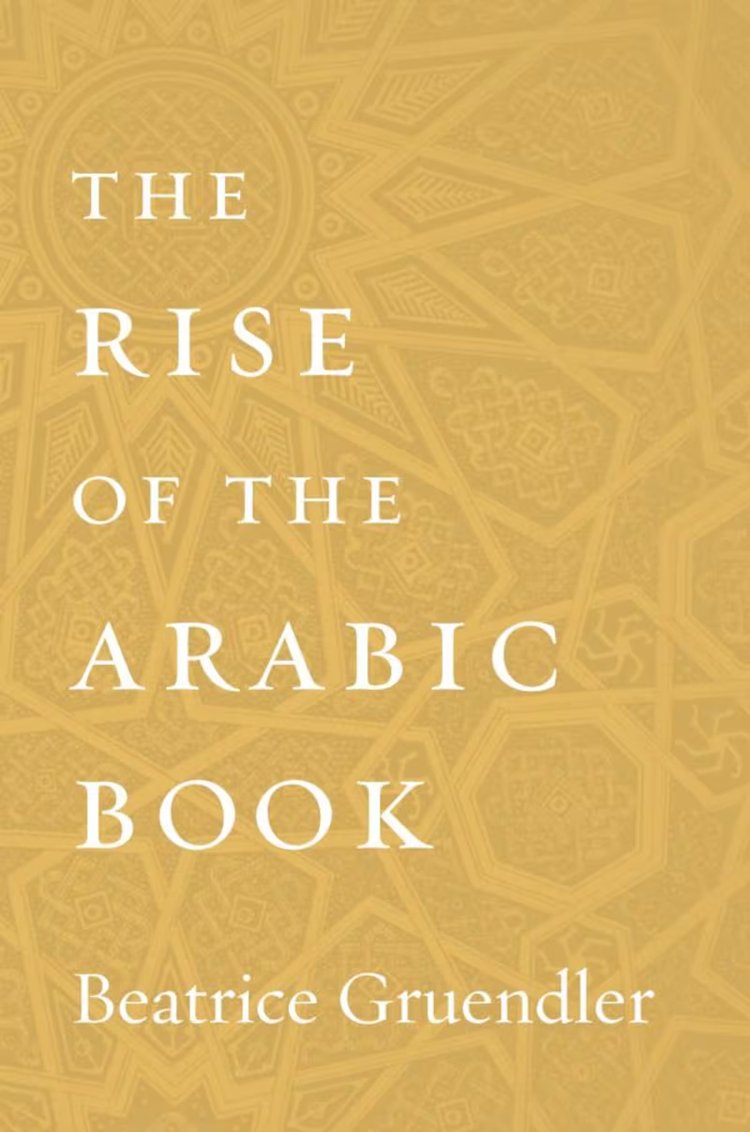
এদিকে এই বিষয়ে এক প্রতিবেদনে সোমবার (২০ অক্টোবর) আমিরাতভিত্তিক সংবাদমাধ্যম দ্য ন্যাশনাল জানিয়েছে, আবুধাবির নিউইয়র্ক ইউনিভার্সিটির ‘আরবি সাহিত্য লাইব্রেরি’ প্রকল্প ইতিমধ্যেই ‘হারানো শতাব্দী’ বলে বিবেচিত সময়ের ৬০ টিরও বেশি আরবি সাহিত্যকর্ম পুনরুদ্ধার করেছে। প্রকল্পটির সম্পাদক অধ্যাপক মরিস পোমেরান্টজ বলেছেন, ‘এই বইগুলো সম্পাদনা করা মানে এক চলমান সংলাপে অংশ নেওয়া—যেখানে প্রজন্মের পর প্রজন্ম লেখক, অনুবাদক ও সমালোচকেরা একে অপরকে উত্তর দিয়ে গেছেন।’
মরিস মনে করেন, আরবি সাহিত্য স্থবির হয়ে যাওয়ার ধারণাটি মূলত অনুবাদের অভাব থেকেই জন্ম নিয়েছে। তিনি বলেন, ‘যখন কোনো লেখা অনুবাদ করা হয় না, তখন সেটি বৈশ্বিক অস্তিত্ব হারায়।’
মরিসের মতে, এখন সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হলো এই সাহিত্যকে আবার জনসাধারণের কল্পনায় ফিরিয়ে আনা—স্কুলে পড়ানো, মঞ্চে উপস্থাপন করা, অনুবাদের মাধ্যমে বিশ্বে ছড়িয়ে দেওয়া। তা না হলে আরবি সাহিত্যের ‘হারানো শতাব্দী’ হিসেবে চিহ্নিত সময়টি অধরাই থেকে যাবে।

জার্মানির ফ্রাঙ্কফুর্ট বইমেলায় উপস্থাপিত আরবি সাহিত্য নিয়ে সাম্প্রতিক এক গবেষণা ইতিহাসের বহুল প্রচলিত ধারণাকে প্রশ্নের মুখে ফেলেছে। এত দিন মনে করা হতো, আব্বাসীয় আমলের (৭৫০-১২৫৮ খ্রিষ্টাব্দ) পর আরবি সাহিত্য প্রায় ৮০০ বছর বছর স্থবির হয়ে ছিল। কিন্তু ভাষাবিদ ও সাহিত্য ইতিহাসবিদদের মতে, এই ধারণা আসলে পশ্চিমা দৃষ্টিকোণ থেকে তৈরি এক ‘ঔপনিবেশিক কল্পনা’ মাত্র। বাস্তবে আরবি সাহিত্য কখনোই থেমে যায়নি।
প্রচলিত ধারণা অনুযায়ী, অষ্টম শতাব্দীতে আব্বাসীয় খলিফাদের অধীনে বিজ্ঞান, দর্শন ও কবিতার কেন্দ্র হয়ে উঠেছিল বাগদাদ। আবু নুয়াস, আল-মুতানাব্বি, আল-ফারাবি ও ইবনে সিনার মতো কবি ও দার্শনিকদের হাত ধরে শুরু হয়েছিল এক স্বর্ণযুগ। ঊনবিংশ শতাব্দীর ইউরোপীয় গবেষকেরা—যেমন ফরাসি চিন্তাবিদ আর্নেস্ট রেনাঁ ও ডাচ ইতিহাসবিদ রেইনহার্ট দোজি সেই আমলটিকেই আরবি বুদ্ধিবৃত্তিক জীবনের শিখর বলে স্বীকার করেছিলেন এবং দাবি করেছিলেন, একাদশ শতাব্দীর পর এই ধারাবাহিকতার পতন ঘটে। তাঁদের মতে, এরপর প্রায় ৮০০ বছর আরবে আর কোনো গুরুত্বপূর্ণ সাহিত্যিক বা দার্শনিক কাজ হয়নি—যতক্ষণ না ইউরোপে রেনেসাঁ শুরু হয়।
কিন্তু আধুনিক গবেষকেরা বলছেন, এই ধারণা সরলীকৃত ও পক্ষপাতদুষ্ট। ফ্রাঙ্কফুর্ট আন্তর্জাতিক বইমেলায় শেখ জায়েদ বুক অ্যাওয়ার্ডের আয়োজিত এক আলোচনায় ভাষাবিদেরা দাবি করেছেন, আরবি রচনা শৈলী কখনো বিলুপ্ত হয়নি; বরং তা ধারাবাহিকভাবে কপি, অনুবাদ ও পাঠের মাধ্যমে বেঁচে ছিল।
জার্মান গবেষক বেয়াট্রিস গ্রুন্ডলার তাঁর ‘দ্য রাইজ অব দ্য অ্যারাবিক বুক’ গ্রন্থে দাবি করেছেন, আরবি সাহিত্যে ‘হারানো শতাব্দী’ হিসেবে যে ধারণাটি প্রচলিত আছে তা আসলে গাল-গল্প। এই বইটি এবারের শেখ জায়েদ পুরস্কারের শর্টলিস্টে রয়েছে। গ্রুন্ডলার এতে দেখিয়েছেন, নবম শতাব্দীর বাগদাদে বইয়ের ব্যবসা, কপিকারদের প্রতিযোগিতা, জনসম্মুখে পাঠ ও লেখার প্রচলন—সবই ছিল আধুনিক প্রকাশনা সংস্কৃতির পূর্বসূরি। তিনি মত দিয়েছেন, ‘বাগদাদের রাস্তায় হাঁটলে আপনি দেখতেন লোকেরা হস্তলিপি বিক্রি করছে, বিরামচিহ্ন নিয়ে তর্ক করছে—এ যেন এক জীবন্ত প্রকাশনা বাজার।’
গবেষণা বলছে, আরবি সাহিত্য আসলে কখনো এক জায়গায় স্থির থাকেনি। এর কেন্দ্র এক সময় বাগদাদ থেকে কায়রো, দামেস্ক ও আন্দালুসিয়ায় স্থানান্তরিত হয়। কিন্তু ধারাটি অব্যাহতই থাকে। নতুন ঘরানা তৈরি হয়, পুরোনো ঘরানা রূপান্তরিত হয়।
ফরাসি অধ্যাপক হাকান ওজকান তাঁর গবেষণায় দেখিয়েছেন, ‘জাজাল’ নামের কথ্য ছন্দভিত্তিক কবিতার ধারা আব্বাসীয় যুগের পরও বিকশিত হতে থাকে। তাঁর মতে, ‘এই কবিরা নিয়ম ভেঙে নতুন রূপ দিয়েছে—তাঁদের ছন্দ ও ব্যঙ্গ আধুনিক র্যাপের মতো প্রাণবন্ত।’
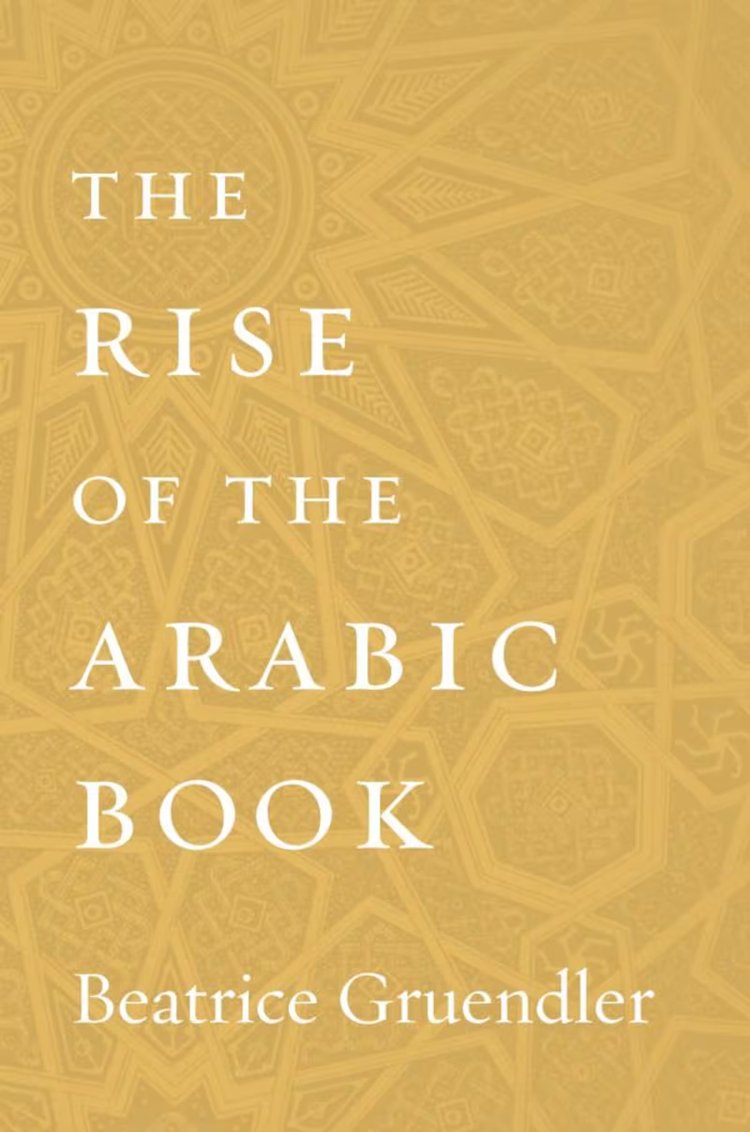
এদিকে এই বিষয়ে এক প্রতিবেদনে সোমবার (২০ অক্টোবর) আমিরাতভিত্তিক সংবাদমাধ্যম দ্য ন্যাশনাল জানিয়েছে, আবুধাবির নিউইয়র্ক ইউনিভার্সিটির ‘আরবি সাহিত্য লাইব্রেরি’ প্রকল্প ইতিমধ্যেই ‘হারানো শতাব্দী’ বলে বিবেচিত সময়ের ৬০ টিরও বেশি আরবি সাহিত্যকর্ম পুনরুদ্ধার করেছে। প্রকল্পটির সম্পাদক অধ্যাপক মরিস পোমেরান্টজ বলেছেন, ‘এই বইগুলো সম্পাদনা করা মানে এক চলমান সংলাপে অংশ নেওয়া—যেখানে প্রজন্মের পর প্রজন্ম লেখক, অনুবাদক ও সমালোচকেরা একে অপরকে উত্তর দিয়ে গেছেন।’
মরিস মনে করেন, আরবি সাহিত্য স্থবির হয়ে যাওয়ার ধারণাটি মূলত অনুবাদের অভাব থেকেই জন্ম নিয়েছে। তিনি বলেন, ‘যখন কোনো লেখা অনুবাদ করা হয় না, তখন সেটি বৈশ্বিক অস্তিত্ব হারায়।’
মরিসের মতে, এখন সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হলো এই সাহিত্যকে আবার জনসাধারণের কল্পনায় ফিরিয়ে আনা—স্কুলে পড়ানো, মঞ্চে উপস্থাপন করা, অনুবাদের মাধ্যমে বিশ্বে ছড়িয়ে দেওয়া। তা না হলে আরবি সাহিত্যের ‘হারানো শতাব্দী’ হিসেবে চিহ্নিত সময়টি অধরাই থেকে যাবে।

বুড়িগঙ্গার পাড় থেকে টেমসের তীরে আসার প্রায় এক বছর হয়ে এল। গত বছর অক্টোবরে সূর্যালোক উদ্ভাসিত প্রাণচাঞ্চল্যে ভরপুর এক দেশ ছেড়ে সাত সমুদ্র তেরো নদীর পাড়ে হাড়কাঁপানো ধূসর ভূমিতে পদার্পণ করি। আমার আগমনের সময়টায় বিলাতে শীত আসি-আসি করছে—জাঁকিয়ে বসেনি। অভিজ্ঞ ব্যক্তিরা আগেই বলেছিলেন, ইউরোপের শীত কোনো ছেলেখ
১৬ সেপ্টেম্বর ২০২২
আলসেমি শরীরে এদিক-ওদিক চেয়ে আটকে গেল চোখ পশ্চিমান্তে। রক্তিম সূর্যের বিদায় ধীর গতিতে। খুব লাল হয়েছে, সারা দিনের জ্বলন্ত প্রহরে পেয়েছে এক অপূর্ব রূপ।
২৩ নভেম্বর ২০২৫
হুমায়ূন আহমেদ তখন ক্যানসার আক্রান্ত। যুক্তরাষ্ট্রে কেমোথেরাপি নিচ্ছেন। হঠাৎ চিকিৎসকের কাছ থেকে ছুটি নিয়ে চলে এলেন নুহাশপল্লীতে। নাটক বানাবেন। অভিনেতা ফারুক আহমেদকে ডাকলেন। নুহাশপল্লীতে নাটকের শুটিংয়ের ফাঁকে গল্প করছিলেন হুমায়ূন ও ফারুক। হুমায়ূন আহমেদ বললেন, ‘কী আশ্চর্য, তাই না ফারুক!’
১৩ নভেম্বর ২০২৫
প্রখ্যাত চলচ্চিত্রকার সত্যজিৎ রায়ের ‘হীরক রাজার দেশে’ চলচ্চিত্র মঞ্চস্থ করেছে স্কলাস্টিকার শিক্ষার্থীরা। গতকাল শুক্রবার স্কলাস্টিকা উত্তরা সিনিয়র শাখার নাটক, সংগীত ও নৃত্যকলা ক্লাবের উদ্যোগে দুই দিনব্যাপী বার্ষিক নাট্যানুষ্ঠানে এটি মঞ্চস্থ করা হয়।
০৮ নভেম্বর ২০২৫