সেলিম জাহান

এত জোরে এবং এমন অভদ্র ভাষায় ভদ্রলোক ধমক দিলেন তাঁর স্ত্রীকে যে ঘরের নানান কোণের আলাপের গুঞ্জন সঙ্গে সঙ্গে হঠাৎ করেই থেমে গেল। অদ্ভুত এক স্তব্ধতা নেমে এল সারা ঘরে। আমরা হতবাক—নিজেদের কানকেই কেউ আমরা বিশ্বাস করতে পারছিলাম না। ভদ্রলোক শুধু ধনাঢ্য নন, শিক্ষিত ও অমায়িক বলে বাইরে তাঁর খ্যাতি আছে, কিন্তু এ মুহূর্তে তাঁকে বীভৎস দানবের মতো মনে হচ্ছিল। এতক্ষণের একটি সুন্দর পরিবেশ যেন ভেঙে খানখান হয়ে গেল। একধরনের বিমূঢ়তা যেন আমাদের আচ্ছন্ন করে ফেলল।
অভ্যাগতদের কেউই আমরা ভদ্রমহিলার মুখের দিকে তাকাতে পারছিলাম না। অপমানে, দুঃখে মুখ ক্লিষ্ট, আশাহত এবং সবচেয়ে বড় কথা বেদনাহতও বটে। মাটির দিকে তাকিয়ে তিনি উঠে দাঁড়ালেন, শাড়ির আঁচলটি একটু টেনে গায়ে জড়িয়ে নিলেন, যেন অপমানের সবটুকু চিহ্ন তিনি মুছে দিতে চাইছেন। বুঝতে পারছিলাম যে তিনি প্রাণপণে কান্না চাপতে চেষ্টা করছেন। ধীর পায়ে তিনি ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। অন্য সবাই স্তব্ধ, কিন্তু তাঁর স্বামীটির কোনো বিকার নেই। যেন কিছুই হয়নি, তেমন একটা দেঁতো হাসি হেসে তিনি তাঁর কথায় ফিরে গেলেন।
আমার মনে হতে লাগল, এইমাত্র এখানে একটি ধর্ষণ ঘটে গেল। কেউ জানল না, কেউ বুঝল না, তবু একটি নারী-নিপীড়ন সংঘটিত হলো। এ ধর্ষণ শারীরিক নয়, এ ধর্ষণ মানসিক; এ ধর্ষণ স্থূল নয়, এ ধর্ষণ সূক্ষ্ম; এ ধর্ষণ দেখার নয়, এ ধর্ষণ উপলব্ধির; এ ধর্ষণ দৃশ্যমান নয়, এ ধর্ষণ প্রচ্ছন্ন। এ ঘটনায় ভদ্রমহিলার ব্যক্তিত্ব, নারীত্ব ধর্ষিত হলো, তাঁর স্বাধীনতা ধর্ষিত হলো, ধর্ষিত হলো তাঁর আত্মসম্মান। ধর্ষণ শুধু দেহের হয় না, ধর্ষণ হতে পারে মনের; ধর্ষণ শুধু স্পর্শের মাধ্যমে হয় না, সেটা হতে পারে কথার। ধর্ষণ শুধু দৃশ্যমান হয় না, সেটা ঘটতে পারে অদৃশ্যভাবেও।
গৃহাভ্যন্তরে নারী এ-জাতীয় নিপীড়নের শিকার প্রতিনিয়ত—কখনো কখনো পিতা, ভ্রাতা, স্বামী, পুত্রের মতো প্রিয়জনদের দ্বারাও বটে। ‘মেয়েমানুষ, কী জানো?, মেয়েছেলে, চুপ করে থাকবে; বড় বাড় বেড়েছে তোমার, মেয়ে হয়ে বেশি কথা বলো না; মেয়ে হয়ে জন্মেছ, চুপ করে থাকবে’—এমন কথা অনবরতই নারীর আপন পুরুষদের মুখে উচ্চারিত হয়
আর দশটা স্বাভাবিক বাক্যের মতো। যেন এটাই নিয়ম,
এটাই ন্যায্য, এটার মধ্যে কোনো দোষ নেই। ঘরের বাইরে পথেঘাটে, স্কুল-কলেজে কথা-নিপীড়নের শিকার হন নারীরা। ‘বাসে-ট্রেনে আলাদা সিট পেয়েছেন বলে কি আমাদের মাথা কিনে নিয়েছেন আপনারা’, কিংবা ‘রান্নাঘরেই আপনাদের জায়গা, সেটা ছেড়ে বাইরে কাজ করতে এসেছেন কেন’ অথবা ‘সাজগোজের তো কমতি দেখি না, পড়াশোনার বেলায় তো অষ্টরম্ভা’—নারীর জীবনের নানান বাঁকে এমন সব নিপীড়িত বাক্য শুনেই তাঁদের বেড়ে ওঠা।
আমাদের, পুরুষদের কাছে মনে হয় নারীরা পৃথিবী সম্পর্কে অজ্ঞ, তাঁদের বুদ্ধিশুদ্ধি কম, এবং এ-জাতীয় কথা তাঁদের নির্দ্বিধায় বলা যায়। অথচ আমরা ভাবি না, এ-জাতীয় কথার মাধ্যমে আমরা তাঁদের বুদ্ধি ও মেধাকে কটাক্ষ করছি, তাঁদের সক্ষমতা সম্পর্কে প্রশ্ন তুলছি এবং তাঁদের অভিজ্ঞতা সম্পর্কে সন্দিহান হচ্ছি। নারীরা যদি পুরুষদের সম্পর্কে এমন কথা বলেন, তবে তাঁরা পুরুষের তথাকথিত পৌরুষের কাছে নির্যাতনের শিকার হবেন নিশ্চিতভাবে। এমন ধারা মানসিক নিপীড়ন চলতে থাকলে নারীর আত্মসম্মানই শুধু নয়, একদিন তাঁর আত্মবিশ্বাসও ধর্ষিত হবে। আমরা পুরুষেরা মনে করি, আমরা নারীদের চেয়ে উচ্চতর প্রাণী, সুতরাং নারীদের সব রকমের নিপীড়ন করা আমাদের জন্মগত অধিকার। অনেকে আবার মনে করেন, নারীরা পুরুষের ব্যক্তিগত সম্পত্তি, সুতরাং তাঁদের ওপরে আমরা সব রকমের জোর খাটাতে পারি।
কথার ধর্ষণের অন্য নগ্নরূপও তো দেখেছি। পুরুষদের জমানো আড্ডায় নারীর কথা উঠলে সে গল্পের প্রকৃতি, স্বরূপ আর ধারা কোনদিকে মোড় নেয়, তা অভাবনীয়। নারীর শরীরের অশালীন বর্ণনা, তাঁদের চরিত্রের প্রতি কটাক্ষ, তাঁদের নিয়ে খিস্তিখেউড়ই সেসব গল্পের সারবস্তু। এ সবই নাকি ‘রসালো গল্প’! সত্যিকার অর্থে, পুরুষদের আড্ডার ‘রসালো গল্প’ মেয়েদের সম্পূর্ণ নগ্ন করে ছেড়ে দেয়। আশ্চর্যের কথা, এ প্রক্রিয়ায় পুরুষেরা চেনা-অচেনার বালাই করেন না, বালাই করেন না বয়সের। নারী তখন পুরুষের আদি রসাত্মক গল্পের খোরাকমাত্র। অনেকে বলে থাকেন, এ-জাতীয় গালগল্প ছেলে-ছোকরারাই করে রকে বসে, চা-খানার আড্ডায় কফি-হাউসের টেবিলে। এ কথা ঠিক নয়। খুব উচ্চপদস্থ, বাহ্যত ভদ্রলোক, তথাকথিত পরিশীলিত মধ্যবয়সী ও প্রৌঢ় মানুষের আড্ডায় নারীবিষয়ক আলোচনা কোনো অংশে কম উলঙ্গ নয়। পাড়ায় একজন নারী একা থাকেন, কিংবা ব্যাংকে চাকরিরত একজন নারী একটু রাত করে কাজ থেকে ঘরে ফেরেন, অথবা বিবাহবিচ্ছেদের কারণে একজন মা একহাতে দুটো বাচ্চাকে মানুষ করছেন—এরা সবাই ওইসব আড্ডার ‘রসালো গল্পের’ খোরাক, রটনার সোনার খনি। কথার এ ধর্ষণের তুলনা কোথায়?
রাস্তায় পথ চলতে নারীরা অনবরত শিকার হন বাক্য আর দৃষ্টি ধর্ষণের। পথচলতি নারীরা অনবরত লক্ষ্য হন বাক্য ধর্ষণের আর দৃষ্টি লেহনের। রাস্তায় হেঁটে যাওয়া নারীদের শুনতেই হয় তাঁদের প্রতি পুরুষের ছুড়ে দেওয়া অশালীন শব্দ বা শব্দমালা। মনে আছে, আমার এক বন্ধু বলেছিলেন যে বহু বছর আগে তিনি তাঁর তরুণী কন্যাকে নিয়ে বেরিয়েছিলেন লস অ্যাঞ্জেলেসের রাস্তায়। বিভিন্ন সময়ে রাস্তার বিভিন্ন জায়গা থেকে ছুড়ে দেওয়া অশালীন বাক্যবাণে বড় বিচলিত হচ্ছিলেন সেই পিতা। রাগান্বিত হচ্ছিলেনও বলা চলে। তখন তাঁর তরুণী কন্যাটি হেসে পিতার হাত ধরেছিলেন। বলেছিলেন, ‘বাবা, রাগ করে নিজের শরীর খারাপ কোরো না। এটাই আমার জীবনের প্রতিদিনের বাস্তবতা।’ এমন সত্যি কথা বড় একটা শুনিনি।
কথা-নিপীড়নের সঙ্গে সঙ্গে ঘটে যায় দৃষ্টি-ধর্ষণের। রাস্তাঘাটে, স্কুল-কলেজে, অফিস-আদালতে নারীদের শিকার হতে হয় অনাকাঙ্ক্ষিত দৃষ্টি লেহনের, যার অন্য নাম ‘চোখ দিয়ে গিলে খাওয়া’। অনেকেই বলেন, রাস্তায় এসব ঘটনা অশিক্ষিত শ্রমজীবী শ্রেণির লোকজনই করে থাকেন। কথাটা পুরোপুরি সত্যি নয়। বরং তাঁরা নারীকে মান্য করেন। এ কাজটি বেশি প্রকাশ্য তথাকথিত শিক্ষিত বিত্তবান মানুষের মধ্যে। এবং এটা প্রকাশ্য সর্বত্রই। শিক্ষিত মানুষের ক্ষেত্রে এটা ঘটে আড়ে আড়ে, কিন্তু সব নারীই এটা টের পান হাড়ে হাড়ে। আশ্চর্যের ব্যাপার হচ্ছে যে এসব ক্ষেত্রে পুরুষ তাঁর নিজের মা-বোন সম্পর্কে সুরক্ষিত মনোভাব নেন, কিন্তু অন্যের মা-বোনের ক্ষেত্রে তাঁর মানদণ্ড ভিন্নতর—দ্বৈত মানদণ্ড বললেও ব্যত্যয় হয় না।
চূড়ান্ত বিচারে নারীজীবনের বহু নির্মম বাস্তবতা নির্ধারিত হয় পুরুষের কর্মকাণ্ডের দ্বারা। সব রকমের নারী নির্যাতন, নিপীড়ন ও ধর্ষণ এর সবচেয়ে বড় উদাহরণ। এর শুরু পুরুষেই, এর সমাপ্তিও হতে হবে পুরুষেই।
লেখক: অর্থনীতিবিদ

এত জোরে এবং এমন অভদ্র ভাষায় ভদ্রলোক ধমক দিলেন তাঁর স্ত্রীকে যে ঘরের নানান কোণের আলাপের গুঞ্জন সঙ্গে সঙ্গে হঠাৎ করেই থেমে গেল। অদ্ভুত এক স্তব্ধতা নেমে এল সারা ঘরে। আমরা হতবাক—নিজেদের কানকেই কেউ আমরা বিশ্বাস করতে পারছিলাম না। ভদ্রলোক শুধু ধনাঢ্য নন, শিক্ষিত ও অমায়িক বলে বাইরে তাঁর খ্যাতি আছে, কিন্তু এ মুহূর্তে তাঁকে বীভৎস দানবের মতো মনে হচ্ছিল। এতক্ষণের একটি সুন্দর পরিবেশ যেন ভেঙে খানখান হয়ে গেল। একধরনের বিমূঢ়তা যেন আমাদের আচ্ছন্ন করে ফেলল।
অভ্যাগতদের কেউই আমরা ভদ্রমহিলার মুখের দিকে তাকাতে পারছিলাম না। অপমানে, দুঃখে মুখ ক্লিষ্ট, আশাহত এবং সবচেয়ে বড় কথা বেদনাহতও বটে। মাটির দিকে তাকিয়ে তিনি উঠে দাঁড়ালেন, শাড়ির আঁচলটি একটু টেনে গায়ে জড়িয়ে নিলেন, যেন অপমানের সবটুকু চিহ্ন তিনি মুছে দিতে চাইছেন। বুঝতে পারছিলাম যে তিনি প্রাণপণে কান্না চাপতে চেষ্টা করছেন। ধীর পায়ে তিনি ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। অন্য সবাই স্তব্ধ, কিন্তু তাঁর স্বামীটির কোনো বিকার নেই। যেন কিছুই হয়নি, তেমন একটা দেঁতো হাসি হেসে তিনি তাঁর কথায় ফিরে গেলেন।
আমার মনে হতে লাগল, এইমাত্র এখানে একটি ধর্ষণ ঘটে গেল। কেউ জানল না, কেউ বুঝল না, তবু একটি নারী-নিপীড়ন সংঘটিত হলো। এ ধর্ষণ শারীরিক নয়, এ ধর্ষণ মানসিক; এ ধর্ষণ স্থূল নয়, এ ধর্ষণ সূক্ষ্ম; এ ধর্ষণ দেখার নয়, এ ধর্ষণ উপলব্ধির; এ ধর্ষণ দৃশ্যমান নয়, এ ধর্ষণ প্রচ্ছন্ন। এ ঘটনায় ভদ্রমহিলার ব্যক্তিত্ব, নারীত্ব ধর্ষিত হলো, তাঁর স্বাধীনতা ধর্ষিত হলো, ধর্ষিত হলো তাঁর আত্মসম্মান। ধর্ষণ শুধু দেহের হয় না, ধর্ষণ হতে পারে মনের; ধর্ষণ শুধু স্পর্শের মাধ্যমে হয় না, সেটা হতে পারে কথার। ধর্ষণ শুধু দৃশ্যমান হয় না, সেটা ঘটতে পারে অদৃশ্যভাবেও।
গৃহাভ্যন্তরে নারী এ-জাতীয় নিপীড়নের শিকার প্রতিনিয়ত—কখনো কখনো পিতা, ভ্রাতা, স্বামী, পুত্রের মতো প্রিয়জনদের দ্বারাও বটে। ‘মেয়েমানুষ, কী জানো?, মেয়েছেলে, চুপ করে থাকবে; বড় বাড় বেড়েছে তোমার, মেয়ে হয়ে বেশি কথা বলো না; মেয়ে হয়ে জন্মেছ, চুপ করে থাকবে’—এমন কথা অনবরতই নারীর আপন পুরুষদের মুখে উচ্চারিত হয়
আর দশটা স্বাভাবিক বাক্যের মতো। যেন এটাই নিয়ম,
এটাই ন্যায্য, এটার মধ্যে কোনো দোষ নেই। ঘরের বাইরে পথেঘাটে, স্কুল-কলেজে কথা-নিপীড়নের শিকার হন নারীরা। ‘বাসে-ট্রেনে আলাদা সিট পেয়েছেন বলে কি আমাদের মাথা কিনে নিয়েছেন আপনারা’, কিংবা ‘রান্নাঘরেই আপনাদের জায়গা, সেটা ছেড়ে বাইরে কাজ করতে এসেছেন কেন’ অথবা ‘সাজগোজের তো কমতি দেখি না, পড়াশোনার বেলায় তো অষ্টরম্ভা’—নারীর জীবনের নানান বাঁকে এমন সব নিপীড়িত বাক্য শুনেই তাঁদের বেড়ে ওঠা।
আমাদের, পুরুষদের কাছে মনে হয় নারীরা পৃথিবী সম্পর্কে অজ্ঞ, তাঁদের বুদ্ধিশুদ্ধি কম, এবং এ-জাতীয় কথা তাঁদের নির্দ্বিধায় বলা যায়। অথচ আমরা ভাবি না, এ-জাতীয় কথার মাধ্যমে আমরা তাঁদের বুদ্ধি ও মেধাকে কটাক্ষ করছি, তাঁদের সক্ষমতা সম্পর্কে প্রশ্ন তুলছি এবং তাঁদের অভিজ্ঞতা সম্পর্কে সন্দিহান হচ্ছি। নারীরা যদি পুরুষদের সম্পর্কে এমন কথা বলেন, তবে তাঁরা পুরুষের তথাকথিত পৌরুষের কাছে নির্যাতনের শিকার হবেন নিশ্চিতভাবে। এমন ধারা মানসিক নিপীড়ন চলতে থাকলে নারীর আত্মসম্মানই শুধু নয়, একদিন তাঁর আত্মবিশ্বাসও ধর্ষিত হবে। আমরা পুরুষেরা মনে করি, আমরা নারীদের চেয়ে উচ্চতর প্রাণী, সুতরাং নারীদের সব রকমের নিপীড়ন করা আমাদের জন্মগত অধিকার। অনেকে আবার মনে করেন, নারীরা পুরুষের ব্যক্তিগত সম্পত্তি, সুতরাং তাঁদের ওপরে আমরা সব রকমের জোর খাটাতে পারি।
কথার ধর্ষণের অন্য নগ্নরূপও তো দেখেছি। পুরুষদের জমানো আড্ডায় নারীর কথা উঠলে সে গল্পের প্রকৃতি, স্বরূপ আর ধারা কোনদিকে মোড় নেয়, তা অভাবনীয়। নারীর শরীরের অশালীন বর্ণনা, তাঁদের চরিত্রের প্রতি কটাক্ষ, তাঁদের নিয়ে খিস্তিখেউড়ই সেসব গল্পের সারবস্তু। এ সবই নাকি ‘রসালো গল্প’! সত্যিকার অর্থে, পুরুষদের আড্ডার ‘রসালো গল্প’ মেয়েদের সম্পূর্ণ নগ্ন করে ছেড়ে দেয়। আশ্চর্যের কথা, এ প্রক্রিয়ায় পুরুষেরা চেনা-অচেনার বালাই করেন না, বালাই করেন না বয়সের। নারী তখন পুরুষের আদি রসাত্মক গল্পের খোরাকমাত্র। অনেকে বলে থাকেন, এ-জাতীয় গালগল্প ছেলে-ছোকরারাই করে রকে বসে, চা-খানার আড্ডায় কফি-হাউসের টেবিলে। এ কথা ঠিক নয়। খুব উচ্চপদস্থ, বাহ্যত ভদ্রলোক, তথাকথিত পরিশীলিত মধ্যবয়সী ও প্রৌঢ় মানুষের আড্ডায় নারীবিষয়ক আলোচনা কোনো অংশে কম উলঙ্গ নয়। পাড়ায় একজন নারী একা থাকেন, কিংবা ব্যাংকে চাকরিরত একজন নারী একটু রাত করে কাজ থেকে ঘরে ফেরেন, অথবা বিবাহবিচ্ছেদের কারণে একজন মা একহাতে দুটো বাচ্চাকে মানুষ করছেন—এরা সবাই ওইসব আড্ডার ‘রসালো গল্পের’ খোরাক, রটনার সোনার খনি। কথার এ ধর্ষণের তুলনা কোথায়?
রাস্তায় পথ চলতে নারীরা অনবরত শিকার হন বাক্য আর দৃষ্টি ধর্ষণের। পথচলতি নারীরা অনবরত লক্ষ্য হন বাক্য ধর্ষণের আর দৃষ্টি লেহনের। রাস্তায় হেঁটে যাওয়া নারীদের শুনতেই হয় তাঁদের প্রতি পুরুষের ছুড়ে দেওয়া অশালীন শব্দ বা শব্দমালা। মনে আছে, আমার এক বন্ধু বলেছিলেন যে বহু বছর আগে তিনি তাঁর তরুণী কন্যাকে নিয়ে বেরিয়েছিলেন লস অ্যাঞ্জেলেসের রাস্তায়। বিভিন্ন সময়ে রাস্তার বিভিন্ন জায়গা থেকে ছুড়ে দেওয়া অশালীন বাক্যবাণে বড় বিচলিত হচ্ছিলেন সেই পিতা। রাগান্বিত হচ্ছিলেনও বলা চলে। তখন তাঁর তরুণী কন্যাটি হেসে পিতার হাত ধরেছিলেন। বলেছিলেন, ‘বাবা, রাগ করে নিজের শরীর খারাপ কোরো না। এটাই আমার জীবনের প্রতিদিনের বাস্তবতা।’ এমন সত্যি কথা বড় একটা শুনিনি।
কথা-নিপীড়নের সঙ্গে সঙ্গে ঘটে যায় দৃষ্টি-ধর্ষণের। রাস্তাঘাটে, স্কুল-কলেজে, অফিস-আদালতে নারীদের শিকার হতে হয় অনাকাঙ্ক্ষিত দৃষ্টি লেহনের, যার অন্য নাম ‘চোখ দিয়ে গিলে খাওয়া’। অনেকেই বলেন, রাস্তায় এসব ঘটনা অশিক্ষিত শ্রমজীবী শ্রেণির লোকজনই করে থাকেন। কথাটা পুরোপুরি সত্যি নয়। বরং তাঁরা নারীকে মান্য করেন। এ কাজটি বেশি প্রকাশ্য তথাকথিত শিক্ষিত বিত্তবান মানুষের মধ্যে। এবং এটা প্রকাশ্য সর্বত্রই। শিক্ষিত মানুষের ক্ষেত্রে এটা ঘটে আড়ে আড়ে, কিন্তু সব নারীই এটা টের পান হাড়ে হাড়ে। আশ্চর্যের ব্যাপার হচ্ছে যে এসব ক্ষেত্রে পুরুষ তাঁর নিজের মা-বোন সম্পর্কে সুরক্ষিত মনোভাব নেন, কিন্তু অন্যের মা-বোনের ক্ষেত্রে তাঁর মানদণ্ড ভিন্নতর—দ্বৈত মানদণ্ড বললেও ব্যত্যয় হয় না।
চূড়ান্ত বিচারে নারীজীবনের বহু নির্মম বাস্তবতা নির্ধারিত হয় পুরুষের কর্মকাণ্ডের দ্বারা। সব রকমের নারী নির্যাতন, নিপীড়ন ও ধর্ষণ এর সবচেয়ে বড় উদাহরণ। এর শুরু পুরুষেই, এর সমাপ্তিও হতে হবে পুরুষেই।
লেখক: অর্থনীতিবিদ

অন্তর্বর্তী সরকারপ্রধান অধ্যাপক ইউনূসের জাতির উদ্দেশে ভাষণের পর ফেব্রুয়ারিতে নির্বাচনের একটি আবহ তৈরি হয়েছে। জামায়াতে ইসলামী আর এনসিপি জুলাই সনদের ব্যাপারে একটা ফয়সালা না হলে নির্বাচনে যাবে না, এ রকম যে অবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল, প্রধান উপদেষ্টার ভাষণের পর সে অবস্থার পরিবর্তন হয়েছে বলে মনে হচ্ছে।
৮ ঘণ্টা আগে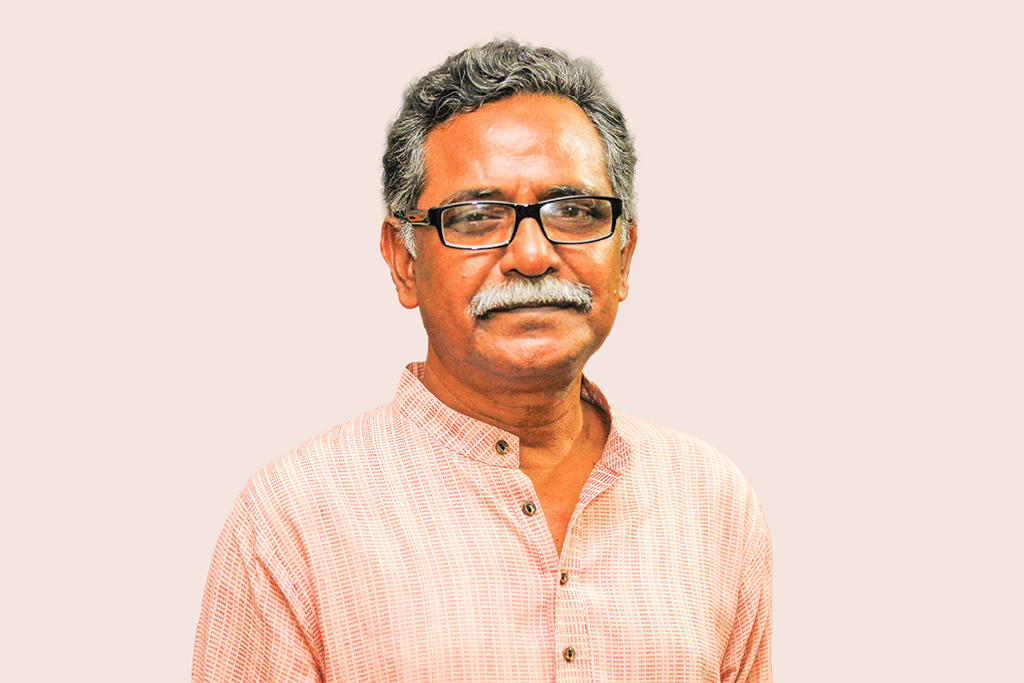
আনু মুহাম্মদ জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের সাবেক অধ্যাপক। তিনি ‘সর্বজনকথা’ পত্রিকার সম্পাদক। দীর্ঘদিন তেল-গ্যাস-খনিজ সম্পদ ও বিদ্যুৎ-বন্দর রক্ষা জাতীয় কমিটির সদস্যসচিব হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। বর্তমানে ‘গণতান্ত্রিক অধিকার কমিটি’র কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের দায়িত্ব পালন করছেন।
৮ ঘণ্টা আগে
একটা সময় মাছ মানেই ছিল রুই, কাতলা বা ইলিশ। কিন্তু এখন দেশের গ্রামীণ পুকুর থেকে শুরু করে শহরের হাটবাজার পর্যন্ত এক নতুন তারকার উত্থান—তেলাপিয়া। দ্রুত বৃদ্ধি, সহজ চাষপদ্ধতি এবং সাশ্রয়ী মূল্যের কারণে তেলাপিয়াকে বিশ্বের অনেক দেশেই বলা হয় ‘জলজ মুরগি’, কেউ বলে ‘গ্রামের রুপালি সম্পদ...
৮ ঘণ্টা আগে
এক নতুন সামরিক–রাজনৈতিক বাস্তবতায় প্রবেশ করল পাকিস্তান। ইসলামাবাদের পার্লামেন্ট ভবনে যেদিন সংবিধানের ২৭তম সংশোধনী পাস হলো। সিনেটে সামান্য হই হই চই এবং দুজন বিচারকের পদত্যাগ ছাড়া অনেকটা নিরবেই পাকিস্তানের ক্ষমতা কাঠামোয় ঐতিহাসিক রূপান্তর ঘটে গেল।
২০ ঘণ্টা আগেসম্পাদকীয়

অন্তর্বর্তী সরকারপ্রধান অধ্যাপক ইউনূসের জাতির উদ্দেশে ভাষণের পর ফেব্রুয়ারিতে নির্বাচনের একটি আবহ তৈরি হয়েছে। জামায়াতে ইসলামী আর এনসিপি জুলাই সনদের ব্যাপারে একটা ফয়সালা না হলে নির্বাচনে যাবে না, এ রকম যে অবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল, প্রধান উপদেষ্টার ভাষণের পর সে অবস্থার পরিবর্তন হয়েছে বলে মনে হচ্ছে। নির্বাচনের দিনই গণভোট হবে—এটাও মেনে নিয়েছে ভোটের আগে গণভোটের দাবিদারেরা। প্রধান উপদেষ্টার বক্তব্যে বর্তমানে আলোচনায় থাকা দলগুলোর সবার জন্যই কিছু না কিছু ছিল। ফলে রাজনৈতিক দলগুলো প্রাথমিক প্রতিক্রিয়ায় কিছুটা উষ্মা প্রকাশ করলেও দলীয় আলোচনার পর প্রধান উপদেষ্টাকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেছে দলগুলো। আশা করা যাচ্ছে, দেশ এখন নির্বাচনের মহাসড়কে উঠতে পারে।
মুশকিল হলো, যে ঐক্যের জন্য এত কিছু করা হলো, সেই ঐক্যের কি দেখা মিলছে? বিভক্ত জাতিকে এক মোহনায় মেলানোর যে অঙ্গীকার ছিল, সে অঙ্গীকার পালন করা দিন দিন কঠিন হয়ে পড়ছে। হিংসা, অবিশ্বাস, পেশিশক্তি, দুর্নীতি, চাঁদাবাজি, মুদ্রাস্ফীতি, বেকারত্বসহ চতুর্দিকে ছড়িয়ে থাকা অনিয়ম দূর করা কতটা সম্ভব, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। একটি ভালো নির্বাচন হলে ধীরে ধীরে একটা শৃঙ্খলার দিকে এগোবে দেশ—এ রকম আশা অনেকের। কিন্তু শুধু একটি নির্বাচনই সবকিছু জায়গামতো নিয়ে আসতে পারে না, যদি না ভালো কিছু করার সদিচ্ছা থাকে। নির্বাচিত দলকে ভালো কাজে বিরোধী দলের পক্ষ থেকে সহায়তা করা, বিরোধী দলের মতামতকে সরকারি দলের গুরুত্ব দেওয়া—এখন সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। নিজেদের ব্যর্থতাকে অন্যের ব্যর্থতা বলে চালিয়ে দেওয়ার চেষ্টা হিতে বিপরীত হবে। গত বছরের আগস্ট মাসের পর থেকে নানা ধরনের ঘটনায় মনে হয়েছে, এই অস্থিরতা সামাল দিতে না পারলে সংস্কার, নির্বাচন—কোনো কিছুই জনমনে স্বস্তি দেবে না। এদিকে নজর দেওয়া দরকার।
নতুন যুগে দেয়াললিখনের চেয়ে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে লেখালেখির গুরুত্ব বেশি। এমনকি প্রতিষ্ঠিত প্রচারমাধ্যমের চেয়ে কোনো কোনো ক্ষেত্রে তা বড় হয়ে দেখা দিচ্ছে। ফলে, দেয়াললিখনের জায়গায় সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে মানুষ কী বলছে, সেদিকেও চোখ রাখা জরুরি। জরুরি রাস্তাঘাটে সাধারণ মানুষ কী বলছে, তা শোনা। এই বার্তা কানের মাধ্যমে মনে পৌঁছালেই সিদ্ধান্ত নেওয়া সহজ হবে।
সরকার পরিচালনা করবে বিজয়ী দল। কিন্তু নির্বাচিত হওয়ার পরেই সে দল দেশের সকল মানুষের প্রতিনিধি হিসেবেই দেশ পরিচালনা করবে। সুতরাং দেশের সকল মানুষের প্রত্যাশার সঙ্গে তাদের যোগ থাকতে হবে। সমুন্নত রাখতে হবে দেশের স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব। আমাদের জাতির ইতিহাস কীভাবে রচিত হয়েছে, তার তথ্য-উপাত্ত লিপিবদ্ধ আছে। কালের স্রোত কীভাবে আমাদের জাতিকে স্বাধিকার আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত করেছিল, কোন আকাঙ্ক্ষা পূরণ করার জন্য জাতি ছিল অঙ্গীকারবদ্ধ, সে কথাগুলো নতুন করে ভাবা দরকার। জাতিরাষ্ট্র গঠনের অঙ্গীকারগুলো বাস্তবায়নের জন্য নির্বাচিত দল আন্তরিক হবে, সেটাই কাম্য। তবে সবার আগে দরকার একটি সুষ্ঠু, প্রতিনিধিত্বশীল নির্বাচন, সে কথা যেন আমরা ভুলে না যাই।

অন্তর্বর্তী সরকারপ্রধান অধ্যাপক ইউনূসের জাতির উদ্দেশে ভাষণের পর ফেব্রুয়ারিতে নির্বাচনের একটি আবহ তৈরি হয়েছে। জামায়াতে ইসলামী আর এনসিপি জুলাই সনদের ব্যাপারে একটা ফয়সালা না হলে নির্বাচনে যাবে না, এ রকম যে অবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল, প্রধান উপদেষ্টার ভাষণের পর সে অবস্থার পরিবর্তন হয়েছে বলে মনে হচ্ছে। নির্বাচনের দিনই গণভোট হবে—এটাও মেনে নিয়েছে ভোটের আগে গণভোটের দাবিদারেরা। প্রধান উপদেষ্টার বক্তব্যে বর্তমানে আলোচনায় থাকা দলগুলোর সবার জন্যই কিছু না কিছু ছিল। ফলে রাজনৈতিক দলগুলো প্রাথমিক প্রতিক্রিয়ায় কিছুটা উষ্মা প্রকাশ করলেও দলীয় আলোচনার পর প্রধান উপদেষ্টাকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেছে দলগুলো। আশা করা যাচ্ছে, দেশ এখন নির্বাচনের মহাসড়কে উঠতে পারে।
মুশকিল হলো, যে ঐক্যের জন্য এত কিছু করা হলো, সেই ঐক্যের কি দেখা মিলছে? বিভক্ত জাতিকে এক মোহনায় মেলানোর যে অঙ্গীকার ছিল, সে অঙ্গীকার পালন করা দিন দিন কঠিন হয়ে পড়ছে। হিংসা, অবিশ্বাস, পেশিশক্তি, দুর্নীতি, চাঁদাবাজি, মুদ্রাস্ফীতি, বেকারত্বসহ চতুর্দিকে ছড়িয়ে থাকা অনিয়ম দূর করা কতটা সম্ভব, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। একটি ভালো নির্বাচন হলে ধীরে ধীরে একটা শৃঙ্খলার দিকে এগোবে দেশ—এ রকম আশা অনেকের। কিন্তু শুধু একটি নির্বাচনই সবকিছু জায়গামতো নিয়ে আসতে পারে না, যদি না ভালো কিছু করার সদিচ্ছা থাকে। নির্বাচিত দলকে ভালো কাজে বিরোধী দলের পক্ষ থেকে সহায়তা করা, বিরোধী দলের মতামতকে সরকারি দলের গুরুত্ব দেওয়া—এখন সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। নিজেদের ব্যর্থতাকে অন্যের ব্যর্থতা বলে চালিয়ে দেওয়ার চেষ্টা হিতে বিপরীত হবে। গত বছরের আগস্ট মাসের পর থেকে নানা ধরনের ঘটনায় মনে হয়েছে, এই অস্থিরতা সামাল দিতে না পারলে সংস্কার, নির্বাচন—কোনো কিছুই জনমনে স্বস্তি দেবে না। এদিকে নজর দেওয়া দরকার।
নতুন যুগে দেয়াললিখনের চেয়ে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে লেখালেখির গুরুত্ব বেশি। এমনকি প্রতিষ্ঠিত প্রচারমাধ্যমের চেয়ে কোনো কোনো ক্ষেত্রে তা বড় হয়ে দেখা দিচ্ছে। ফলে, দেয়াললিখনের জায়গায় সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে মানুষ কী বলছে, সেদিকেও চোখ রাখা জরুরি। জরুরি রাস্তাঘাটে সাধারণ মানুষ কী বলছে, তা শোনা। এই বার্তা কানের মাধ্যমে মনে পৌঁছালেই সিদ্ধান্ত নেওয়া সহজ হবে।
সরকার পরিচালনা করবে বিজয়ী দল। কিন্তু নির্বাচিত হওয়ার পরেই সে দল দেশের সকল মানুষের প্রতিনিধি হিসেবেই দেশ পরিচালনা করবে। সুতরাং দেশের সকল মানুষের প্রত্যাশার সঙ্গে তাদের যোগ থাকতে হবে। সমুন্নত রাখতে হবে দেশের স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব। আমাদের জাতির ইতিহাস কীভাবে রচিত হয়েছে, তার তথ্য-উপাত্ত লিপিবদ্ধ আছে। কালের স্রোত কীভাবে আমাদের জাতিকে স্বাধিকার আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত করেছিল, কোন আকাঙ্ক্ষা পূরণ করার জন্য জাতি ছিল অঙ্গীকারবদ্ধ, সে কথাগুলো নতুন করে ভাবা দরকার। জাতিরাষ্ট্র গঠনের অঙ্গীকারগুলো বাস্তবায়নের জন্য নির্বাচিত দল আন্তরিক হবে, সেটাই কাম্য। তবে সবার আগে দরকার একটি সুষ্ঠু, প্রতিনিধিত্বশীল নির্বাচন, সে কথা যেন আমরা ভুলে না যাই।

এত জোরে এবং এমন অভদ্র ভাষায় ভদ্রলোক ধমক দিলেন তাঁর স্ত্রীকে যে ঘরের নানান কোণের আলাপের গুঞ্জন সঙ্গে সঙ্গে হঠাৎ করেই থেমে গেল। অদ্ভুত এক স্তব্ধতা নেমে এল সারা ঘরে। আমরা হতবাক—নিজেদের কানকেই কেউ আমরা বিশ্বাস করতে পারছিলাম না।
০৬ নভেম্বর ২০২৪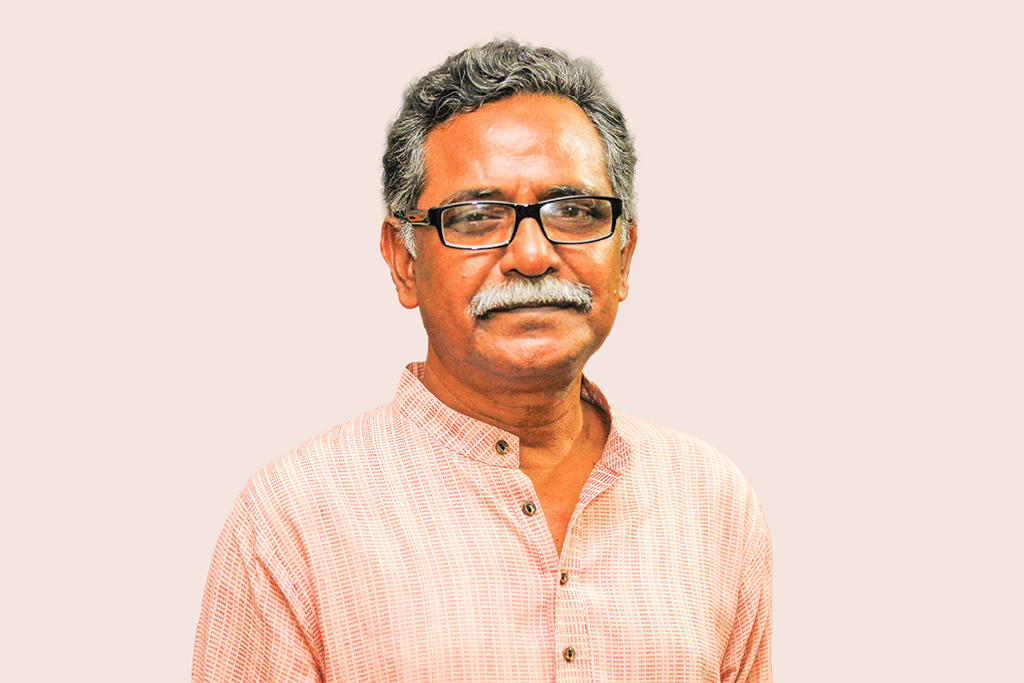
আনু মুহাম্মদ জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের সাবেক অধ্যাপক। তিনি ‘সর্বজনকথা’ পত্রিকার সম্পাদক। দীর্ঘদিন তেল-গ্যাস-খনিজ সম্পদ ও বিদ্যুৎ-বন্দর রক্ষা জাতীয় কমিটির সদস্যসচিব হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। বর্তমানে ‘গণতান্ত্রিক অধিকার কমিটি’র কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের দায়িত্ব পালন করছেন।
৮ ঘণ্টা আগে
একটা সময় মাছ মানেই ছিল রুই, কাতলা বা ইলিশ। কিন্তু এখন দেশের গ্রামীণ পুকুর থেকে শুরু করে শহরের হাটবাজার পর্যন্ত এক নতুন তারকার উত্থান—তেলাপিয়া। দ্রুত বৃদ্ধি, সহজ চাষপদ্ধতি এবং সাশ্রয়ী মূল্যের কারণে তেলাপিয়াকে বিশ্বের অনেক দেশেই বলা হয় ‘জলজ মুরগি’, কেউ বলে ‘গ্রামের রুপালি সম্পদ...
৮ ঘণ্টা আগে
এক নতুন সামরিক–রাজনৈতিক বাস্তবতায় প্রবেশ করল পাকিস্তান। ইসলামাবাদের পার্লামেন্ট ভবনে যেদিন সংবিধানের ২৭তম সংশোধনী পাস হলো। সিনেটে সামান্য হই হই চই এবং দুজন বিচারকের পদত্যাগ ছাড়া অনেকটা নিরবেই পাকিস্তানের ক্ষমতা কাঠামোয় ঐতিহাসিক রূপান্তর ঘটে গেল।
২০ ঘণ্টা আগে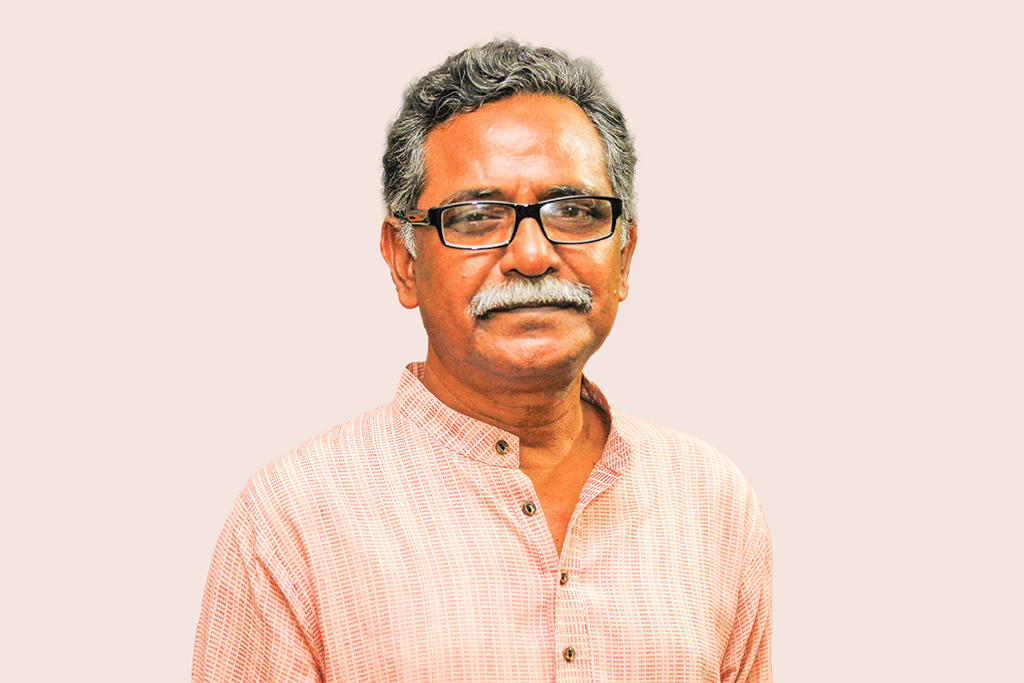
আনু মুহাম্মদ জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের সাবেক অধ্যাপক। তিনি ‘সর্বজনকথা’ পত্রিকার সম্পাদক। দীর্ঘদিন তেল-গ্যাস-খনিজ সম্পদ ও বিদ্যুৎ-বন্দর রক্ষা জাতীয় কমিটির সদস্যসচিব হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। বর্তমানে ‘গণতান্ত্রিক অধিকার কমিটি’র কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের দায়িত্ব পালন করছেন। চট্টগ্রাম সমুদ্রবন্দর বিদেশি কোম্পানিকে দেওয়া হলে দেশের বিভিন্ন ক্ষেত্রে কী প্রভাব পড়তে পারে, এ নিয়ে তাঁর সঙ্গে কথা বলেছেন আজকের পত্রিকার মাসুদ রানা।
মাসুদ রানা
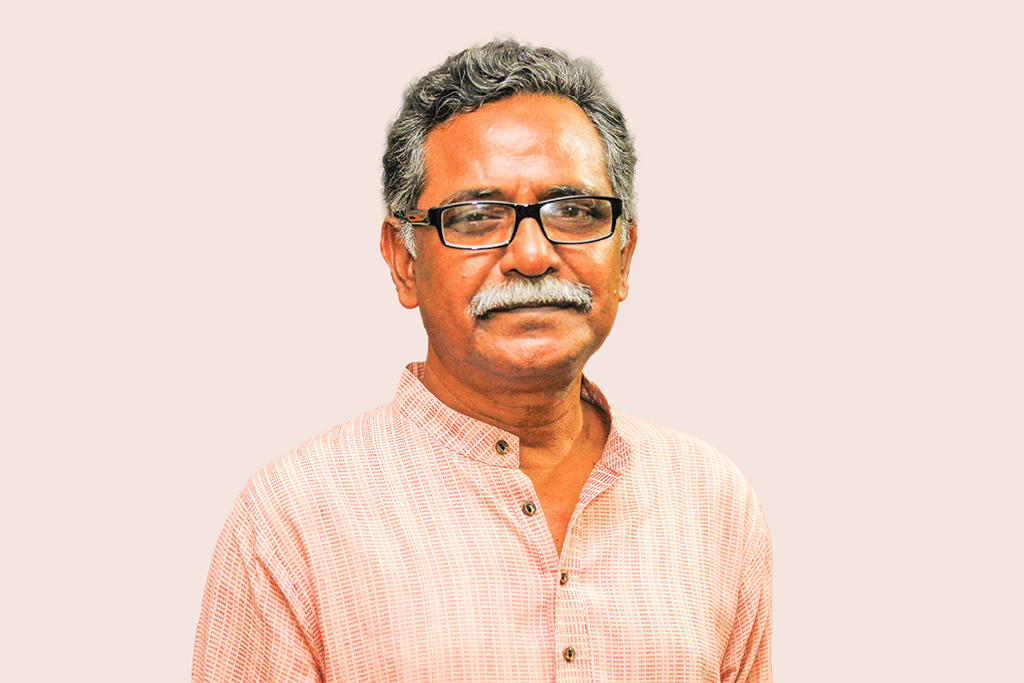
চট্টগ্রাম বন্দর দেশের আমদানি-রপ্তানির ৯০ শতাংশের বেশি পরিচালনা করে এবং লোকসানও হয় না। তারপরও কেন এটা বিদেশি কোম্পানিকে দেওয়া হচ্ছে?
সেটা আমাদেরও একটা প্রশ্ন। দেশের মধ্যে এ রকম কোনো প্রতিষ্ঠান নেই বা বন্দর কর্তৃপক্ষের যথেষ্ট লোকজন নেই—এ রকম যদি কোনো অসহায় পরিস্থিতি তৈরি হতো এবং যারা এটা পরিচালনার সঙ্গে যুক্ত, তারা এটাকে লোকসানি প্রতিষ্ঠানে পরিণত করেছে—এ রকম পরিস্থিতি থাকলে তার একটা যুক্তি থাকত। কিংবা যদি নতুন প্রযুক্তি, যন্ত্রপাতি নেই এবং সেগুলো কেনার অর্থ নেই, এভাবে কথা বলে সরকার একটা যুক্তি সাজাতে পারত। কিন্তু এগুলোর কোনোটিরই ঠিক নেই। কারণ, চট্টগ্রাম বন্দরের নিউমুরিং টার্মিনাল একটা লাভজনক প্রতিষ্ঠান। শুধু লাভজনক নয়, এখন যত খরচ হয়, তার আয় হয় দ্বিগুণ। মানে উদ্বৃত্ত বিপুল পরিমাণ অর্থ আছে। এরপর নতুন নতুন যন্ত্রপাতি কেনার জন্য কয়েক হাজার কোটি টাকা বিনিয়োগ করা হয়েছে।
আগে যে বেসরকারি কোম্পানি এবং এখন নৌবাহিনী এটা খুব দক্ষতার সঙ্গে পরিচালনা করছে। এ বন্দরের নিউমুরিং টার্মিনালের অপারেটর হিসেবে এখন পর্যন্ত কার্যক্রম পরিচালনায় কোনো ধরনের সমস্যা দেখা যায়নি। বর্তমান সরকার যে উদ্যোগটা নিচ্ছে, তাতে বড় ধরনের একটা অসংগতির জায়গা তৈরি করছে। তারা বলছে, এই বন্দরের আরও দক্ষতা বাড়াতে হবে, সে জন্য আমরা মাশুল বাড়াচ্ছি। মাশুল বাড়াতে হয় আয় বাড়ানোর জন্য। কিন্তু বন্দরের তো উদ্বৃত্ত অর্থ আছে। এ মাশুল বাড়ানো হচ্ছে আসলে বিদেশি কোম্পানির স্বার্থে। যে বিদেশি কোম্পানি এটা পরিচালনার দায়িত্ব নেবে, তাদের উদ্দেশ্য হলো মুনাফা বৃদ্ধি করা। সেই মুনাফা যাতে অনেক বেশি করা যায়, সরকার অনেক আগে থেকে তাদের নির্দেশে এবং বিশ্বব্যাংকের সুপারিশে এর মাশুল বৃদ্ধি করেছে। এর পরিণাম কী হতে পারে, সেটা আমরা এর মাশুল বৃদ্ধি থেকে দেখতে পাচ্ছি।
চট্টগ্রাম বন্দর শুধু বাণিজ্যিক কেন্দ্র নয়, এটি দক্ষিণ এশিয়ার একটি কৌশলগত গুরুত্বপূর্ণ সমুদ্রবন্দর। এর ব্যবস্থাপনায় বিদেশিরা সম্পৃক্ত হলে আঞ্চলিক ভূরাজনীতিতে কোনো প্রভাব ফেলতে পারে?
এটা খুব গুরুতর প্রশ্ন। বিদেশি কোম্পানি তো অনেক দেশেই কাজ করে। কিন্তু চট্টগ্রাম বন্দর হলো পুরো দেশের অর্থনীতির প্রাণকেন্দ্র। এখান দিয়ে দেশের ৯০ শতাংশ আমদানি-রপ্তানি হয়। মোংলা বন্দর সেভাবে কাজ করে না। চট্টগ্রাম বন্দরের অন্য অনেক টার্মিনাল চালুই করা যায়নি। একটা ছোট টার্মিনাল আছে, সেটা একটা সৌদি কোম্পানিকে দায়িত্ব দিয়েছে শেখ হাসিনা সরকার। সেটাও ঠিকভাবে কাজ করছে না। সেখানে নিউমুরিং টার্মিনাল বিদেশি কোম্পানিকে অযৌক্তিকভাবে দেওয়ার যে তাগিদ বর্তমান সরকারের মধ্যে দেখা যাচ্ছে, সেটা নিয়ে আমাদের বড় আশঙ্কার জায়গা তৈরি হয়েছে। বন্দরের সক্ষমতা বাড়ার কথাটা আসলে কোনোভাবে গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। এটার একমাত্র কারণ কোনো গোষ্ঠীর কৌশলগত স্বার্থরক্ষা বা কোনো গোষ্ঠীর চাহিদা পূরণ। আবার এই সরকারের কারও কারও মধ্যে বাধ্য থাকার কারণ হতে পারে।
সংযুক্ত আরব আমিরাতের রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান ডিবি ওয়ার্ল্ডকে এ সরকার টেন্ডার ছাড়া দিতে চাইছে। শেখ হাসিনার সরকার এই কোম্পানিকে টেন্ডার ছাড়া দিতে চেয়েছিল। আরব আমিরাত হলো মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পকেটের একটা রাষ্ট্র। এটি কোনো স্বাধীন রাষ্ট্র নয়। পকেট রাষ্ট্র হওয়া সত্ত্বেও ডিবি ওয়ার্ল্ড কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রের বন্দর নিতে পারেনি। কারণ, যুক্তরাষ্ট্রের কংগ্রেসে এটা নিয়ে বিরোধিতা হয়েছিল। এ কোম্পানি বিশ্বের যেখানে কাজ করতে গেছে, সেখানে নানা ধরনের সমস্যা তৈরি করেছে।
তারপরও ডিবি ওয়ার্ল্ডকে দিতেই হবে, তার জন্য প্রধান উপদেষ্টা থেকে শুরু করে বিভিন্ন উপদেষ্টার মধ্যে আগ্রহ দেখে আমার মধ্যে আশঙ্কা, অর্থনৈতিক ক্ষতির পাশাপাশি দেশকে ভৌগোলিক, সামরিক কৌশলগত নিরাপত্তাহীনতার মধ্যে ফেলতে পারে।
একটি গুরুত্বপূর্ণ সমুদ্রবন্দরের সম্পূর্ণ বা আংশিক নিয়ন্ত্রণ বিদেশি শক্তির হাতে যাওয়াটা কি জাতীয় নিরাপত্তার জন্য হুমকি তৈরি করবে না?
হ্যাঁ, অবশ্যই হুমকি তৈরি করবে। এখন বাংলাদেশের প্রধান বন্দর, যার সঙ্গে আমাদের জাতীয় নিরাপত্তা, কৌশলগত নিরাপত্তা, অর্থনৈতিক নিরাপত্তা ও সচলতা—সবকিছু নির্ভর করছে। সেই সমুদ্রবন্দর যখন বিদেশি কোম্পানিকে দরপত্র, যাচাই-বাছাই ছাড়া এবং জনসম্মতি ছাড়া দিয়ে দেওয়া হয়, সেটা তো কোনোভাবেই গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। এই সরকার যে এটা দেওয়ার জন্য জোরজবরদস্তি করছে, তাতে আমার আশঙ্কা হচ্ছে, সরকারের সঙ্গে অন্য কোনো অ্যাজেন্ডা জড়িয়ে আছে।
বন্দর বিদেশি কোম্পানিকে দেওয়া হলে এখনকার অনেক লোকের চাকরি চলে যেতে পারে। তখন কী হবে?
ডিবি ওয়ার্ল্ডের পুরোনো রেকর্ড হলো, বিশ্বের যেসব দেশে গেছে, সেখানে লোকবল ছাঁটাই করেছে। তাদের দিক থেকে সেটা যৌক্তিক। কারণ, তারা তো মুনাফা করতে চাইবে। মুনাফা করার জন্য দুটি জিনিস দরকার। একটা হলো, মুনাফার জন্য মাশুল বৃদ্ধি করা। আর অন্যটা হলো, লোক কমিয়ে ফেলা। ডিবি ওয়ার্ল্ড মুনাফা বৃদ্ধির জন্য খরচ কমাবে। এই খরচ কমানোর জন্য তারা যে কাজ করানোর জন্য ১০ জন লোকের দরকার, সেটা তারা ৫ জন দিয়ে করাতে চাইবে। আর বাকি ৫ জনকে ছাঁটাই করে ফেলবে। এ জন্য বলা যায়, ছাঁটাই অবশ্যম্ভাবী হবে।
মাশুল বৃদ্ধি করার কারণে আমদানি করা জিনিসের মূল্য বৃদ্ধি পাবে এবং রপ্তানি করার জিনিস পাঠানোর খরচও বাড়বে। তাতে রপ্তানিকারক ব্যবসায়ীদের সক্ষমতা এবং প্রতিযোগিতা করার ক্ষমতা কমে যাবে। আর আমদানির ব্যয় বেড়ে যাওয়ার কারণে দেশের সব ধরনের জিনিসপত্রের দাম বেড়ে যাবে। পুরো অর্থনীতির জন্য সেটা বিপর্যয় ডেকে আনবে। এগুলো কিন্তু বিদেশি কোম্পানির স্বার্থে করা হবে। সেটার কারণে আমাদের দেশের অর্থনীতি বিপদের মধ্যে পড়বে। তাতে বলা যায়, সরকার যে কারণে এটাকে বিদেশি কোম্পানিকে দিচ্ছে, তাতে দেশের পরিণতির কী হবে, তার একটা নমুনা হচ্ছে মাশুল বৃদ্ধি।
বিদেশি কোম্পানিনির্ভর, ঋণনির্ভর, আমদানিনির্ভর নানা চুক্তি করতে আগ্রহ দেখাচ্ছে অন্তর্বর্তী সরকার। এ এখতিয়ার কি অন্তর্বর্তী সরকারের আছে?
এই এখতিয়ার অন্তর্বর্তী সরকারের নেই। কারণ, শিক্ষকসহ নানা পেশার মানুষেরা যখন তাঁদের ন্যায্য দাবি-দাওয়া নিয়ে আন্দোলন করেন, তখন সরকারের উপদেষ্টারা বলেন যে আমরা তো অন্তর্বর্তী সরকার। আমরা তো এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত দিতে পারি না। সেসব হলো নির্বাচিত সরকারের কাজ। কিন্তু এই কথাটা তাঁদের স্মরণে থাকে না, যখন এ ধরনের চুক্তি তাঁরা করেন।
তারা অন্তর্বর্তী সরকার—তাদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ হলো নির্বাচনের জন্য যতটুকু সংস্কার করা দরকার, সেটাই তাদের প্রধান কাজ। এ ছাড়া তাদের আর কোনো কিছু করার দরকার নেই। ৩০ বছর মেয়াদি একটা চুক্তি করতে চাইছে সরকার, কিন্তু তারা দায়িত্ব ছেড়ে দেবে কয়েক মাসের মধ্যে। ৩০ বছর মেয়াদি চুক্তির প্রভাব এ দেশের মধ্যে যখন পড়বে, তখন সেটার জন্য জবাবদিহি কে করবে সে সময়? সে সময় তো এদের কাউকেই খুঁজে পাওয়া যাবে না। কারণ, এদের মধ্যে বেশির ভাগই দেশে থাকবেন না। এরপরও এই সরকার এই সর্বনাশা চুক্তি করার চেষ্টা করছে। এর আগে স্টারলিংকের সঙ্গে চুক্তি করেছে। এই চুক্তি কেন করা হয়েছিল, তার কোনো যুক্তি পাওয়া যায় না। আবার তারা এলএনজি আমদানি করার চুক্তি করেছে। সেটাও যথাযথ প্রতিষ্ঠানকে না জানিয়ে।
এই সরকারের কিছু ব্যক্তির ভূমিকা দেখে মনে হয়, তাঁরা বিদেশি বড় বড় কোম্পানির লবিস্ট হিসেবে কাজ করছেন! এসব হলো একটা বড় দুশ্চিন্তার বিষয়। এই সরকারের এগুলো করার কোনো এখতিয়ার নেই। তাদের একমাত্র কাজ হচ্ছে, একটা গ্রহণযোগ্য নির্বাচন করে বিদায় নেওয়া।
চট্টগ্রাম বন্দর অব্যবস্থাপনা নিয়ে সমালোচনা আছে, সেটাকে আমরা কীভাবে ত্রুটিমুক্ত করতে পারি?
অব্যবস্থাপনা নিয়ে সমস্যা আছে। তবে সেটা অপারেটর বদল করে সমাধান করা যাবে না। প্রধান সমস্যার একটা হলো কাস্টমস। বিদেশি কোম্পানিকে অপারেটর হিসেবে দায়িত্ব দেওয়া হচ্ছে, কিন্তু কাস্টমস, পরিবহনব্যবস্থা, কনটেইনার রাখার জায়গা যদি অপরিবর্তিত থাকে, তাহলে পরিস্থিতির তেমন কোনো পরিবর্তন হবে না।
মালামাল লোড-আনলোড করতে সময় যে বেশি লাগে, বন্দরের যে অদক্ষতার সমস্যা, সেটা কিন্তু যাবে না। সেই সমস্যা থেকেই যাবে। এখনকার দায়িত্বপ্রাপ্ত অপারেটর সফল ও দক্ষতার সঙ্গে কাজ করছে। সরকার যদি কাস্টমস, আমলাতন্ত্র, পরিবহন ও যোগাযোগ সমস্যা দূর করার জন্য প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নিত, তাহলে অনেক ভালো হতো। এতে জট কমত এবং সক্ষমতাও বাড়ত।
ভাটার সময় এখানে বড় জাহাজ আসতে পারে না, সেটার জন্য মালামাল নামাতে বেশি সময় লাগে, সেটার জন্য টেকনিক্যাল সমস্যা দূর করতে হবে। এটা তো অপারেটরের সমস্যা না।
সময় দেওয়ার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ।
আজকের পত্রিকাকেও ধন্যবাদ।
চট্টগ্রাম বন্দর দেশের আমদানি-রপ্তানির ৯০ শতাংশের বেশি পরিচালনা করে এবং লোকসানও হয় না। তারপরও কেন এটা বিদেশি কোম্পানিকে দেওয়া হচ্ছে?
সেটা আমাদেরও একটা প্রশ্ন। দেশের মধ্যে এ রকম কোনো প্রতিষ্ঠান নেই বা বন্দর কর্তৃপক্ষের যথেষ্ট লোকজন নেই—এ রকম যদি কোনো অসহায় পরিস্থিতি তৈরি হতো এবং যারা এটা পরিচালনার সঙ্গে যুক্ত, তারা এটাকে লোকসানি প্রতিষ্ঠানে পরিণত করেছে—এ রকম পরিস্থিতি থাকলে তার একটা যুক্তি থাকত। কিংবা যদি নতুন প্রযুক্তি, যন্ত্রপাতি নেই এবং সেগুলো কেনার অর্থ নেই, এভাবে কথা বলে সরকার একটা যুক্তি সাজাতে পারত। কিন্তু এগুলোর কোনোটিরই ঠিক নেই। কারণ, চট্টগ্রাম বন্দরের নিউমুরিং টার্মিনাল একটা লাভজনক প্রতিষ্ঠান। শুধু লাভজনক নয়, এখন যত খরচ হয়, তার আয় হয় দ্বিগুণ। মানে উদ্বৃত্ত বিপুল পরিমাণ অর্থ আছে। এরপর নতুন নতুন যন্ত্রপাতি কেনার জন্য কয়েক হাজার কোটি টাকা বিনিয়োগ করা হয়েছে।
আগে যে বেসরকারি কোম্পানি এবং এখন নৌবাহিনী এটা খুব দক্ষতার সঙ্গে পরিচালনা করছে। এ বন্দরের নিউমুরিং টার্মিনালের অপারেটর হিসেবে এখন পর্যন্ত কার্যক্রম পরিচালনায় কোনো ধরনের সমস্যা দেখা যায়নি। বর্তমান সরকার যে উদ্যোগটা নিচ্ছে, তাতে বড় ধরনের একটা অসংগতির জায়গা তৈরি করছে। তারা বলছে, এই বন্দরের আরও দক্ষতা বাড়াতে হবে, সে জন্য আমরা মাশুল বাড়াচ্ছি। মাশুল বাড়াতে হয় আয় বাড়ানোর জন্য। কিন্তু বন্দরের তো উদ্বৃত্ত অর্থ আছে। এ মাশুল বাড়ানো হচ্ছে আসলে বিদেশি কোম্পানির স্বার্থে। যে বিদেশি কোম্পানি এটা পরিচালনার দায়িত্ব নেবে, তাদের উদ্দেশ্য হলো মুনাফা বৃদ্ধি করা। সেই মুনাফা যাতে অনেক বেশি করা যায়, সরকার অনেক আগে থেকে তাদের নির্দেশে এবং বিশ্বব্যাংকের সুপারিশে এর মাশুল বৃদ্ধি করেছে। এর পরিণাম কী হতে পারে, সেটা আমরা এর মাশুল বৃদ্ধি থেকে দেখতে পাচ্ছি।
চট্টগ্রাম বন্দর শুধু বাণিজ্যিক কেন্দ্র নয়, এটি দক্ষিণ এশিয়ার একটি কৌশলগত গুরুত্বপূর্ণ সমুদ্রবন্দর। এর ব্যবস্থাপনায় বিদেশিরা সম্পৃক্ত হলে আঞ্চলিক ভূরাজনীতিতে কোনো প্রভাব ফেলতে পারে?
এটা খুব গুরুতর প্রশ্ন। বিদেশি কোম্পানি তো অনেক দেশেই কাজ করে। কিন্তু চট্টগ্রাম বন্দর হলো পুরো দেশের অর্থনীতির প্রাণকেন্দ্র। এখান দিয়ে দেশের ৯০ শতাংশ আমদানি-রপ্তানি হয়। মোংলা বন্দর সেভাবে কাজ করে না। চট্টগ্রাম বন্দরের অন্য অনেক টার্মিনাল চালুই করা যায়নি। একটা ছোট টার্মিনাল আছে, সেটা একটা সৌদি কোম্পানিকে দায়িত্ব দিয়েছে শেখ হাসিনা সরকার। সেটাও ঠিকভাবে কাজ করছে না। সেখানে নিউমুরিং টার্মিনাল বিদেশি কোম্পানিকে অযৌক্তিকভাবে দেওয়ার যে তাগিদ বর্তমান সরকারের মধ্যে দেখা যাচ্ছে, সেটা নিয়ে আমাদের বড় আশঙ্কার জায়গা তৈরি হয়েছে। বন্দরের সক্ষমতা বাড়ার কথাটা আসলে কোনোভাবে গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। এটার একমাত্র কারণ কোনো গোষ্ঠীর কৌশলগত স্বার্থরক্ষা বা কোনো গোষ্ঠীর চাহিদা পূরণ। আবার এই সরকারের কারও কারও মধ্যে বাধ্য থাকার কারণ হতে পারে।
সংযুক্ত আরব আমিরাতের রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান ডিবি ওয়ার্ল্ডকে এ সরকার টেন্ডার ছাড়া দিতে চাইছে। শেখ হাসিনার সরকার এই কোম্পানিকে টেন্ডার ছাড়া দিতে চেয়েছিল। আরব আমিরাত হলো মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পকেটের একটা রাষ্ট্র। এটি কোনো স্বাধীন রাষ্ট্র নয়। পকেট রাষ্ট্র হওয়া সত্ত্বেও ডিবি ওয়ার্ল্ড কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রের বন্দর নিতে পারেনি। কারণ, যুক্তরাষ্ট্রের কংগ্রেসে এটা নিয়ে বিরোধিতা হয়েছিল। এ কোম্পানি বিশ্বের যেখানে কাজ করতে গেছে, সেখানে নানা ধরনের সমস্যা তৈরি করেছে।
তারপরও ডিবি ওয়ার্ল্ডকে দিতেই হবে, তার জন্য প্রধান উপদেষ্টা থেকে শুরু করে বিভিন্ন উপদেষ্টার মধ্যে আগ্রহ দেখে আমার মধ্যে আশঙ্কা, অর্থনৈতিক ক্ষতির পাশাপাশি দেশকে ভৌগোলিক, সামরিক কৌশলগত নিরাপত্তাহীনতার মধ্যে ফেলতে পারে।
একটি গুরুত্বপূর্ণ সমুদ্রবন্দরের সম্পূর্ণ বা আংশিক নিয়ন্ত্রণ বিদেশি শক্তির হাতে যাওয়াটা কি জাতীয় নিরাপত্তার জন্য হুমকি তৈরি করবে না?
হ্যাঁ, অবশ্যই হুমকি তৈরি করবে। এখন বাংলাদেশের প্রধান বন্দর, যার সঙ্গে আমাদের জাতীয় নিরাপত্তা, কৌশলগত নিরাপত্তা, অর্থনৈতিক নিরাপত্তা ও সচলতা—সবকিছু নির্ভর করছে। সেই সমুদ্রবন্দর যখন বিদেশি কোম্পানিকে দরপত্র, যাচাই-বাছাই ছাড়া এবং জনসম্মতি ছাড়া দিয়ে দেওয়া হয়, সেটা তো কোনোভাবেই গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। এই সরকার যে এটা দেওয়ার জন্য জোরজবরদস্তি করছে, তাতে আমার আশঙ্কা হচ্ছে, সরকারের সঙ্গে অন্য কোনো অ্যাজেন্ডা জড়িয়ে আছে।
বন্দর বিদেশি কোম্পানিকে দেওয়া হলে এখনকার অনেক লোকের চাকরি চলে যেতে পারে। তখন কী হবে?
ডিবি ওয়ার্ল্ডের পুরোনো রেকর্ড হলো, বিশ্বের যেসব দেশে গেছে, সেখানে লোকবল ছাঁটাই করেছে। তাদের দিক থেকে সেটা যৌক্তিক। কারণ, তারা তো মুনাফা করতে চাইবে। মুনাফা করার জন্য দুটি জিনিস দরকার। একটা হলো, মুনাফার জন্য মাশুল বৃদ্ধি করা। আর অন্যটা হলো, লোক কমিয়ে ফেলা। ডিবি ওয়ার্ল্ড মুনাফা বৃদ্ধির জন্য খরচ কমাবে। এই খরচ কমানোর জন্য তারা যে কাজ করানোর জন্য ১০ জন লোকের দরকার, সেটা তারা ৫ জন দিয়ে করাতে চাইবে। আর বাকি ৫ জনকে ছাঁটাই করে ফেলবে। এ জন্য বলা যায়, ছাঁটাই অবশ্যম্ভাবী হবে।
মাশুল বৃদ্ধি করার কারণে আমদানি করা জিনিসের মূল্য বৃদ্ধি পাবে এবং রপ্তানি করার জিনিস পাঠানোর খরচও বাড়বে। তাতে রপ্তানিকারক ব্যবসায়ীদের সক্ষমতা এবং প্রতিযোগিতা করার ক্ষমতা কমে যাবে। আর আমদানির ব্যয় বেড়ে যাওয়ার কারণে দেশের সব ধরনের জিনিসপত্রের দাম বেড়ে যাবে। পুরো অর্থনীতির জন্য সেটা বিপর্যয় ডেকে আনবে। এগুলো কিন্তু বিদেশি কোম্পানির স্বার্থে করা হবে। সেটার কারণে আমাদের দেশের অর্থনীতি বিপদের মধ্যে পড়বে। তাতে বলা যায়, সরকার যে কারণে এটাকে বিদেশি কোম্পানিকে দিচ্ছে, তাতে দেশের পরিণতির কী হবে, তার একটা নমুনা হচ্ছে মাশুল বৃদ্ধি।
বিদেশি কোম্পানিনির্ভর, ঋণনির্ভর, আমদানিনির্ভর নানা চুক্তি করতে আগ্রহ দেখাচ্ছে অন্তর্বর্তী সরকার। এ এখতিয়ার কি অন্তর্বর্তী সরকারের আছে?
এই এখতিয়ার অন্তর্বর্তী সরকারের নেই। কারণ, শিক্ষকসহ নানা পেশার মানুষেরা যখন তাঁদের ন্যায্য দাবি-দাওয়া নিয়ে আন্দোলন করেন, তখন সরকারের উপদেষ্টারা বলেন যে আমরা তো অন্তর্বর্তী সরকার। আমরা তো এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত দিতে পারি না। সেসব হলো নির্বাচিত সরকারের কাজ। কিন্তু এই কথাটা তাঁদের স্মরণে থাকে না, যখন এ ধরনের চুক্তি তাঁরা করেন।
তারা অন্তর্বর্তী সরকার—তাদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ হলো নির্বাচনের জন্য যতটুকু সংস্কার করা দরকার, সেটাই তাদের প্রধান কাজ। এ ছাড়া তাদের আর কোনো কিছু করার দরকার নেই। ৩০ বছর মেয়াদি একটা চুক্তি করতে চাইছে সরকার, কিন্তু তারা দায়িত্ব ছেড়ে দেবে কয়েক মাসের মধ্যে। ৩০ বছর মেয়াদি চুক্তির প্রভাব এ দেশের মধ্যে যখন পড়বে, তখন সেটার জন্য জবাবদিহি কে করবে সে সময়? সে সময় তো এদের কাউকেই খুঁজে পাওয়া যাবে না। কারণ, এদের মধ্যে বেশির ভাগই দেশে থাকবেন না। এরপরও এই সরকার এই সর্বনাশা চুক্তি করার চেষ্টা করছে। এর আগে স্টারলিংকের সঙ্গে চুক্তি করেছে। এই চুক্তি কেন করা হয়েছিল, তার কোনো যুক্তি পাওয়া যায় না। আবার তারা এলএনজি আমদানি করার চুক্তি করেছে। সেটাও যথাযথ প্রতিষ্ঠানকে না জানিয়ে।
এই সরকারের কিছু ব্যক্তির ভূমিকা দেখে মনে হয়, তাঁরা বিদেশি বড় বড় কোম্পানির লবিস্ট হিসেবে কাজ করছেন! এসব হলো একটা বড় দুশ্চিন্তার বিষয়। এই সরকারের এগুলো করার কোনো এখতিয়ার নেই। তাদের একমাত্র কাজ হচ্ছে, একটা গ্রহণযোগ্য নির্বাচন করে বিদায় নেওয়া।
চট্টগ্রাম বন্দর অব্যবস্থাপনা নিয়ে সমালোচনা আছে, সেটাকে আমরা কীভাবে ত্রুটিমুক্ত করতে পারি?
অব্যবস্থাপনা নিয়ে সমস্যা আছে। তবে সেটা অপারেটর বদল করে সমাধান করা যাবে না। প্রধান সমস্যার একটা হলো কাস্টমস। বিদেশি কোম্পানিকে অপারেটর হিসেবে দায়িত্ব দেওয়া হচ্ছে, কিন্তু কাস্টমস, পরিবহনব্যবস্থা, কনটেইনার রাখার জায়গা যদি অপরিবর্তিত থাকে, তাহলে পরিস্থিতির তেমন কোনো পরিবর্তন হবে না।
মালামাল লোড-আনলোড করতে সময় যে বেশি লাগে, বন্দরের যে অদক্ষতার সমস্যা, সেটা কিন্তু যাবে না। সেই সমস্যা থেকেই যাবে। এখনকার দায়িত্বপ্রাপ্ত অপারেটর সফল ও দক্ষতার সঙ্গে কাজ করছে। সরকার যদি কাস্টমস, আমলাতন্ত্র, পরিবহন ও যোগাযোগ সমস্যা দূর করার জন্য প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নিত, তাহলে অনেক ভালো হতো। এতে জট কমত এবং সক্ষমতাও বাড়ত।
ভাটার সময় এখানে বড় জাহাজ আসতে পারে না, সেটার জন্য মালামাল নামাতে বেশি সময় লাগে, সেটার জন্য টেকনিক্যাল সমস্যা দূর করতে হবে। এটা তো অপারেটরের সমস্যা না।
সময় দেওয়ার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ।
আজকের পত্রিকাকেও ধন্যবাদ।

এত জোরে এবং এমন অভদ্র ভাষায় ভদ্রলোক ধমক দিলেন তাঁর স্ত্রীকে যে ঘরের নানান কোণের আলাপের গুঞ্জন সঙ্গে সঙ্গে হঠাৎ করেই থেমে গেল। অদ্ভুত এক স্তব্ধতা নেমে এল সারা ঘরে। আমরা হতবাক—নিজেদের কানকেই কেউ আমরা বিশ্বাস করতে পারছিলাম না।
০৬ নভেম্বর ২০২৪
অন্তর্বর্তী সরকারপ্রধান অধ্যাপক ইউনূসের জাতির উদ্দেশে ভাষণের পর ফেব্রুয়ারিতে নির্বাচনের একটি আবহ তৈরি হয়েছে। জামায়াতে ইসলামী আর এনসিপি জুলাই সনদের ব্যাপারে একটা ফয়সালা না হলে নির্বাচনে যাবে না, এ রকম যে অবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল, প্রধান উপদেষ্টার ভাষণের পর সে অবস্থার পরিবর্তন হয়েছে বলে মনে হচ্ছে।
৮ ঘণ্টা আগে
একটা সময় মাছ মানেই ছিল রুই, কাতলা বা ইলিশ। কিন্তু এখন দেশের গ্রামীণ পুকুর থেকে শুরু করে শহরের হাটবাজার পর্যন্ত এক নতুন তারকার উত্থান—তেলাপিয়া। দ্রুত বৃদ্ধি, সহজ চাষপদ্ধতি এবং সাশ্রয়ী মূল্যের কারণে তেলাপিয়াকে বিশ্বের অনেক দেশেই বলা হয় ‘জলজ মুরগি’, কেউ বলে ‘গ্রামের রুপালি সম্পদ...
৮ ঘণ্টা আগে
এক নতুন সামরিক–রাজনৈতিক বাস্তবতায় প্রবেশ করল পাকিস্তান। ইসলামাবাদের পার্লামেন্ট ভবনে যেদিন সংবিধানের ২৭তম সংশোধনী পাস হলো। সিনেটে সামান্য হই হই চই এবং দুজন বিচারকের পদত্যাগ ছাড়া অনেকটা নিরবেই পাকিস্তানের ক্ষমতা কাঠামোয় ঐতিহাসিক রূপান্তর ঘটে গেল।
২০ ঘণ্টা আগেড. মো. শরীফুল ইসলাম

একটা সময় মাছ মানেই ছিল রুই, কাতলা বা ইলিশ। কিন্তু এখন দেশের গ্রামীণ পুকুর থেকে শুরু করে শহরের হাটবাজার পর্যন্ত এক নতুন তারকার উত্থান—তেলাপিয়া। দ্রুত বৃদ্ধি, সহজ চাষপদ্ধতি এবং সাশ্রয়ী মূল্যের কারণে তেলাপিয়াকে বিশ্বের অনেক দেশেই বলা হয় ‘জলজ মুরগি’, কেউ বলে ‘গ্রামের রুপালি সম্পদ’—যে যেভাবেই ডাকুন না কেন, এই মাছ এখন বাংলাদেশের নীল অর্থনীতি ও খাদ্যনিরাপত্তার এক গুরুত্বপূর্ণ স্তম্ভ।
তেলাপিয়া চাষ আজ আর কেবল মাছ চাষ নয়—এ যেন গ্রামীণ অর্থনীতির এক নতুন গল্প। একসময়ের অকাজের পুকুর এখন চাষির জন্য হয়ে উঠেছে টাকার ব্যাংক। মাত্র চার থেকে পাঁচ মাসে ফসল তোলা যায়, খরচ কম, ঝুঁকি সামান্য—ফলাফল, বছরে দুই থেকে তিনবার আয়! ময়মনসিংহ, যশোর, খুলনা, কুমিল্লা কিংবা বরিশালের হাজারো পরিবার এখন তেলাপিয়ার চাষের ওপর নির্ভরশীল। এক মাছের ঢেউ ছড়িয়ে পড়েছে চাষি, ফিড মিল, হ্যাচারি, বাজার আর রেস্টুরেন্টে—গড়ে তুলেছে হাজারো কর্মসংস্থানের সুযোগ।
বিশ্বে তেলাপিয়ার রাজত্ব
তেলাপিয়া এখন বিশ্বের অন্যতম জনপ্রিয় মাছ। পৃথিবীর ১৫০টির বেশি দেশে এই মাছের চাষ হচ্ছে। ২০২৩ সালে বিশ্বজুড়ে তেলাপিয়া উৎপাদন ছিল প্রায় ৬ দশমিক ৭ মিলিয়ন টন। আর বিশেষজ্ঞদের পূর্বাভাস, ২০২৫ সালের মধ্যে তা ছাড়াবে ৭ মিলিয়ন টন! চীন, ইন্দোনেশিয়া, মিসর ও ফিলিপাইন এখন তেলাপিয়ার গ্লোবাল পাওয়ারহাউস। বিশ্বের মোট উৎপাদনের প্রায় ৬৭ শতাংশই আসে এশিয়া থেকে, যেখানে বাংলাদেশও দ্রুত উঠে আসছে নতুন শক্তি হিসেবে। তেলাপিয়া এখন শুধু একটি খাবার নয়—এটি বৈশ্বিক খাদ্যনিরাপত্তা, কর্মসংস্থান ও গ্রামীণ অর্থনীতির নতুন প্রতীক।
বাংলাদেশ ফিশারিজ রিসার্চ ইনস্টিটিউট (বিএফআরআই), মৎস্য অধিদপ্তর এবং সরকারি-বেসরকারি নানাবিধ উদ্যোগে এখন দেশ বিশ্বের শীর্ষ তেলাপিয়া উৎপাদকদের কাতারে। ২০১০-১১ অর্থবছরে যেখানে উৎপাদন ছিল মাত্র ৯৭ হাজার ৯০৯ টন, ২০২১-২২ সালে তা লাফিয়ে বেড়ে দাঁড়ায় ৩.২৯ লাখ টনে। ২০২৩-২৪ সালে দেশের মোট মাছ উৎপাদন ছিল প্রায় ৫০.১৮ লাখ টন। এর মধ্যে তেলাপিয়ার উৎপাদন প্রায় ৪ লাখ টন। বাংলাদেশ এখন বিশ্বের চতুর্থ বৃহত্তম তেলাপিয়া উৎপাদক দেশ, আর এশিয়ায় আমাদের অবস্থান তৃতীয়।
তেলাপিয়ার পুষ্টিগুণ
তেলাপিয়ার নরম মাংস, মৃদু স্বাদ এবং উচ্চ প্রোটিন উপাদান একে জনপ্রিয় করে তুলেছে। ভাজা, ঝোল বা গ্রিল—যেভাবেই রান্না করা হোক, এটি খেতে সহজ ও সুস্বাদু। তেলাপিয়ার প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো এর উচ্চ প্রোটিন ও নিম্ন চর্বি। প্রতি ১০০ গ্রাম রান্না করা তেলাপিয়ায় থাকে প্রায় ২০-২১ গ্রাম প্রোটিন, যা শরীরের কোষ গঠন ও ক্ষয়পূরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। একই পরিমাণ মাছ থেকে মাত্র ১.৭ থেকে ২ গ্রাম চর্বি পাওয়া যায়, ফলে এটি হৃদ্রোগীদের জন্যও নিরাপদ। তেলাপিয়ায় রয়েছে ভিটামিন বি-১২, নিয়াসিন (বি-৩), সেলেনিয়াম, পটাশিয়াম ও ফসফরাস—যেগুলো শরীরের শক্তি উৎপাদন, রক্তকণিকা গঠন, স্নায়ু ও হাড়ের সুস্থতা বজায় রাখতে অপরিহার্য। বিশেষ করে সেলেনিয়াম দেহে অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট হিসেবে কাজ করে, যা কোষকে ক্ষয় থেকে রক্ষা করে এবং রোগ প্রতিরোধক্ষমতা বাড়ায়। তেলাপিয়া মাছের মধ্যে রয়েছে ওমেগা-৩ ফ্যাটি অ্যাসিড, যা মস্তিষ্কের বিকাশ, স্মৃতিশক্তি বৃদ্ধি এবং হৃৎপিণ্ডের সুস্থতায় সাহায্য করে। যদিও তেলাপিয়ায় সামুদ্রিক মাছের তুলনায় ওমেগা-৩ কম, তবু এর পরিমাণ শরীরের জন্য যথেষ্ট উপকারী মাত্রায় রয়েছে। তেলাপিয়া সহজপাচ্য ও স্বাদে মৃদু হওয়ায় এটি শিশু, বৃদ্ধ এবং গর্ভবতী মায়েদের জন্য আদর্শ মাছ। এতে পারদের মাত্রা (মারকিউরি লেভেল) অনেক কম থাকায় এটি নিরাপদ খাদ্য হিসেবেও বিবেচিত। দিনে একবার খাবারে তেলাপিয়া রাখলে শরীর পায় প্রোটিন, ভিটামিন ও খনিজের চমৎকার ভারসাম্য।
নীল নদ থেকে ময়মনসিংহ-কুমিল্লায়
মাছের জগতে তেলাপিয়া আজ এক পরিচিত নাম। কিন্তু এই মাছের গল্প শুরু হয় হাজার বছরের পুরোনো সভ্যতা প্রাচীন মিসরের নীল নদে। প্রাচীনকালে মিসরীয়রা তেলাপিয়াকে শুধু আহার হিসেবে দেখেনি, এটি তাদের জন্য ছিল উর্বরতা ও সমৃদ্ধির প্রতীক। নীল নদে জন্মানো নাইল তেলাপিয়া (Oreochromis niloticus) দ্রুত জনপ্রিয় হয়ে ওঠে, কারণ এটি সহজে বংশ বিস্তার করে, দ্রুত বৃদ্ধি পায় এবং পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে পারে। নীল নদে জন্ম হলেও তেলাপিয়া ধীরে ধীরে ছড়িয়ে পড়ে সাব-সাহারা আফ্রিকার নদী, হ্রদ ও জলাভূমিতে। এটি এমন এক মাছ যা কম অক্সিজেনযুক্ত পানি, পরিবর্তনশীল তাপমাত্রা ও সামান্য লবণাক্ত পানি সহ্য করতে পারে। ফলে ছোট ও মাঝারি মাপের চাষের জন্য এটি আদর্শ হয়ে ওঠে। বিশ শতকে আফ্রিকান দেশগুলো পুকুরে তেলাপিয়ার সফল চাষ শুরু করে, যা পরবর্তী সময়ে বিশ্বব্যাপী এক বিপ্লবের সূচনা করে।
বিশ শতকের মধ্যভাগে তেলাপিয়া পৌঁছায় এশিয়ায়। থাইল্যান্ড, ফিলিপাইন, চীনসহ বিভিন্ন দেশে তেলাপিয়া বাণিজ্যিক চাষে জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। ১৯৭০-এর দশকে এটি গবেষণার উদ্দেশে বাংলাদেশে আনা হয়। তবে আসল পরিবর্তন আসে ২০০০ সালের পর, যখন ‘জেনেটিক্যালি ইমপ্রুভড ফার্মড তেলাপিয়া’ (জিআইএফটি) জাত দেশে ছড়িয়ে পড়ে। জিআইএফটি হচ্ছে জেনেটিক্যালি উন্নত তেলাপিয়ার জাত, যা দ্রুত বাড়ে, টিকে থাকে, আর দেয় তিন গুণ উৎপাদন।
তবে এই সাফল্যের গল্পেও আছে সতর্কতার ছায়া। মানহীন পোনা, পানিদূষণ, বাজারে মূল্যপতন আর জলবায়ুর প্রভাব—সব মিলিয়ে চাষিদের সামনে রয়েছে নতুন চ্যালেঞ্জ। সময় এসেছে উন্নত ব্যবস্থাপনা, টেকসই চাষপদ্ধতি এবং আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারের। আমাদের উচিত উন্নত চাষপ্রকরণ, মান নিয়ন্ত্রণ, বাজার সংগঠন ও রপ্তানিতে মনোযোগ দিয়ে তেলাপিয়া চাষকে আরও গতিশীল ও টেকসই করা। কারণ, এই মাছ শুধুই পুকুরের মাছ নয়—এটি আমাদের ভবিষ্যতের খাদ্য ও জীবিকা পরিকল্পনার এক অংশ।
লেখক: ঊর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট

একটা সময় মাছ মানেই ছিল রুই, কাতলা বা ইলিশ। কিন্তু এখন দেশের গ্রামীণ পুকুর থেকে শুরু করে শহরের হাটবাজার পর্যন্ত এক নতুন তারকার উত্থান—তেলাপিয়া। দ্রুত বৃদ্ধি, সহজ চাষপদ্ধতি এবং সাশ্রয়ী মূল্যের কারণে তেলাপিয়াকে বিশ্বের অনেক দেশেই বলা হয় ‘জলজ মুরগি’, কেউ বলে ‘গ্রামের রুপালি সম্পদ’—যে যেভাবেই ডাকুন না কেন, এই মাছ এখন বাংলাদেশের নীল অর্থনীতি ও খাদ্যনিরাপত্তার এক গুরুত্বপূর্ণ স্তম্ভ।
তেলাপিয়া চাষ আজ আর কেবল মাছ চাষ নয়—এ যেন গ্রামীণ অর্থনীতির এক নতুন গল্প। একসময়ের অকাজের পুকুর এখন চাষির জন্য হয়ে উঠেছে টাকার ব্যাংক। মাত্র চার থেকে পাঁচ মাসে ফসল তোলা যায়, খরচ কম, ঝুঁকি সামান্য—ফলাফল, বছরে দুই থেকে তিনবার আয়! ময়মনসিংহ, যশোর, খুলনা, কুমিল্লা কিংবা বরিশালের হাজারো পরিবার এখন তেলাপিয়ার চাষের ওপর নির্ভরশীল। এক মাছের ঢেউ ছড়িয়ে পড়েছে চাষি, ফিড মিল, হ্যাচারি, বাজার আর রেস্টুরেন্টে—গড়ে তুলেছে হাজারো কর্মসংস্থানের সুযোগ।
বিশ্বে তেলাপিয়ার রাজত্ব
তেলাপিয়া এখন বিশ্বের অন্যতম জনপ্রিয় মাছ। পৃথিবীর ১৫০টির বেশি দেশে এই মাছের চাষ হচ্ছে। ২০২৩ সালে বিশ্বজুড়ে তেলাপিয়া উৎপাদন ছিল প্রায় ৬ দশমিক ৭ মিলিয়ন টন। আর বিশেষজ্ঞদের পূর্বাভাস, ২০২৫ সালের মধ্যে তা ছাড়াবে ৭ মিলিয়ন টন! চীন, ইন্দোনেশিয়া, মিসর ও ফিলিপাইন এখন তেলাপিয়ার গ্লোবাল পাওয়ারহাউস। বিশ্বের মোট উৎপাদনের প্রায় ৬৭ শতাংশই আসে এশিয়া থেকে, যেখানে বাংলাদেশও দ্রুত উঠে আসছে নতুন শক্তি হিসেবে। তেলাপিয়া এখন শুধু একটি খাবার নয়—এটি বৈশ্বিক খাদ্যনিরাপত্তা, কর্মসংস্থান ও গ্রামীণ অর্থনীতির নতুন প্রতীক।
বাংলাদেশ ফিশারিজ রিসার্চ ইনস্টিটিউট (বিএফআরআই), মৎস্য অধিদপ্তর এবং সরকারি-বেসরকারি নানাবিধ উদ্যোগে এখন দেশ বিশ্বের শীর্ষ তেলাপিয়া উৎপাদকদের কাতারে। ২০১০-১১ অর্থবছরে যেখানে উৎপাদন ছিল মাত্র ৯৭ হাজার ৯০৯ টন, ২০২১-২২ সালে তা লাফিয়ে বেড়ে দাঁড়ায় ৩.২৯ লাখ টনে। ২০২৩-২৪ সালে দেশের মোট মাছ উৎপাদন ছিল প্রায় ৫০.১৮ লাখ টন। এর মধ্যে তেলাপিয়ার উৎপাদন প্রায় ৪ লাখ টন। বাংলাদেশ এখন বিশ্বের চতুর্থ বৃহত্তম তেলাপিয়া উৎপাদক দেশ, আর এশিয়ায় আমাদের অবস্থান তৃতীয়।
তেলাপিয়ার পুষ্টিগুণ
তেলাপিয়ার নরম মাংস, মৃদু স্বাদ এবং উচ্চ প্রোটিন উপাদান একে জনপ্রিয় করে তুলেছে। ভাজা, ঝোল বা গ্রিল—যেভাবেই রান্না করা হোক, এটি খেতে সহজ ও সুস্বাদু। তেলাপিয়ার প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো এর উচ্চ প্রোটিন ও নিম্ন চর্বি। প্রতি ১০০ গ্রাম রান্না করা তেলাপিয়ায় থাকে প্রায় ২০-২১ গ্রাম প্রোটিন, যা শরীরের কোষ গঠন ও ক্ষয়পূরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। একই পরিমাণ মাছ থেকে মাত্র ১.৭ থেকে ২ গ্রাম চর্বি পাওয়া যায়, ফলে এটি হৃদ্রোগীদের জন্যও নিরাপদ। তেলাপিয়ায় রয়েছে ভিটামিন বি-১২, নিয়াসিন (বি-৩), সেলেনিয়াম, পটাশিয়াম ও ফসফরাস—যেগুলো শরীরের শক্তি উৎপাদন, রক্তকণিকা গঠন, স্নায়ু ও হাড়ের সুস্থতা বজায় রাখতে অপরিহার্য। বিশেষ করে সেলেনিয়াম দেহে অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট হিসেবে কাজ করে, যা কোষকে ক্ষয় থেকে রক্ষা করে এবং রোগ প্রতিরোধক্ষমতা বাড়ায়। তেলাপিয়া মাছের মধ্যে রয়েছে ওমেগা-৩ ফ্যাটি অ্যাসিড, যা মস্তিষ্কের বিকাশ, স্মৃতিশক্তি বৃদ্ধি এবং হৃৎপিণ্ডের সুস্থতায় সাহায্য করে। যদিও তেলাপিয়ায় সামুদ্রিক মাছের তুলনায় ওমেগা-৩ কম, তবু এর পরিমাণ শরীরের জন্য যথেষ্ট উপকারী মাত্রায় রয়েছে। তেলাপিয়া সহজপাচ্য ও স্বাদে মৃদু হওয়ায় এটি শিশু, বৃদ্ধ এবং গর্ভবতী মায়েদের জন্য আদর্শ মাছ। এতে পারদের মাত্রা (মারকিউরি লেভেল) অনেক কম থাকায় এটি নিরাপদ খাদ্য হিসেবেও বিবেচিত। দিনে একবার খাবারে তেলাপিয়া রাখলে শরীর পায় প্রোটিন, ভিটামিন ও খনিজের চমৎকার ভারসাম্য।
নীল নদ থেকে ময়মনসিংহ-কুমিল্লায়
মাছের জগতে তেলাপিয়া আজ এক পরিচিত নাম। কিন্তু এই মাছের গল্প শুরু হয় হাজার বছরের পুরোনো সভ্যতা প্রাচীন মিসরের নীল নদে। প্রাচীনকালে মিসরীয়রা তেলাপিয়াকে শুধু আহার হিসেবে দেখেনি, এটি তাদের জন্য ছিল উর্বরতা ও সমৃদ্ধির প্রতীক। নীল নদে জন্মানো নাইল তেলাপিয়া (Oreochromis niloticus) দ্রুত জনপ্রিয় হয়ে ওঠে, কারণ এটি সহজে বংশ বিস্তার করে, দ্রুত বৃদ্ধি পায় এবং পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে পারে। নীল নদে জন্ম হলেও তেলাপিয়া ধীরে ধীরে ছড়িয়ে পড়ে সাব-সাহারা আফ্রিকার নদী, হ্রদ ও জলাভূমিতে। এটি এমন এক মাছ যা কম অক্সিজেনযুক্ত পানি, পরিবর্তনশীল তাপমাত্রা ও সামান্য লবণাক্ত পানি সহ্য করতে পারে। ফলে ছোট ও মাঝারি মাপের চাষের জন্য এটি আদর্শ হয়ে ওঠে। বিশ শতকে আফ্রিকান দেশগুলো পুকুরে তেলাপিয়ার সফল চাষ শুরু করে, যা পরবর্তী সময়ে বিশ্বব্যাপী এক বিপ্লবের সূচনা করে।
বিশ শতকের মধ্যভাগে তেলাপিয়া পৌঁছায় এশিয়ায়। থাইল্যান্ড, ফিলিপাইন, চীনসহ বিভিন্ন দেশে তেলাপিয়া বাণিজ্যিক চাষে জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। ১৯৭০-এর দশকে এটি গবেষণার উদ্দেশে বাংলাদেশে আনা হয়। তবে আসল পরিবর্তন আসে ২০০০ সালের পর, যখন ‘জেনেটিক্যালি ইমপ্রুভড ফার্মড তেলাপিয়া’ (জিআইএফটি) জাত দেশে ছড়িয়ে পড়ে। জিআইএফটি হচ্ছে জেনেটিক্যালি উন্নত তেলাপিয়ার জাত, যা দ্রুত বাড়ে, টিকে থাকে, আর দেয় তিন গুণ উৎপাদন।
তবে এই সাফল্যের গল্পেও আছে সতর্কতার ছায়া। মানহীন পোনা, পানিদূষণ, বাজারে মূল্যপতন আর জলবায়ুর প্রভাব—সব মিলিয়ে চাষিদের সামনে রয়েছে নতুন চ্যালেঞ্জ। সময় এসেছে উন্নত ব্যবস্থাপনা, টেকসই চাষপদ্ধতি এবং আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারের। আমাদের উচিত উন্নত চাষপ্রকরণ, মান নিয়ন্ত্রণ, বাজার সংগঠন ও রপ্তানিতে মনোযোগ দিয়ে তেলাপিয়া চাষকে আরও গতিশীল ও টেকসই করা। কারণ, এই মাছ শুধুই পুকুরের মাছ নয়—এটি আমাদের ভবিষ্যতের খাদ্য ও জীবিকা পরিকল্পনার এক অংশ।
লেখক: ঊর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট

এত জোরে এবং এমন অভদ্র ভাষায় ভদ্রলোক ধমক দিলেন তাঁর স্ত্রীকে যে ঘরের নানান কোণের আলাপের গুঞ্জন সঙ্গে সঙ্গে হঠাৎ করেই থেমে গেল। অদ্ভুত এক স্তব্ধতা নেমে এল সারা ঘরে। আমরা হতবাক—নিজেদের কানকেই কেউ আমরা বিশ্বাস করতে পারছিলাম না।
০৬ নভেম্বর ২০২৪
অন্তর্বর্তী সরকারপ্রধান অধ্যাপক ইউনূসের জাতির উদ্দেশে ভাষণের পর ফেব্রুয়ারিতে নির্বাচনের একটি আবহ তৈরি হয়েছে। জামায়াতে ইসলামী আর এনসিপি জুলাই সনদের ব্যাপারে একটা ফয়সালা না হলে নির্বাচনে যাবে না, এ রকম যে অবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল, প্রধান উপদেষ্টার ভাষণের পর সে অবস্থার পরিবর্তন হয়েছে বলে মনে হচ্ছে।
৮ ঘণ্টা আগে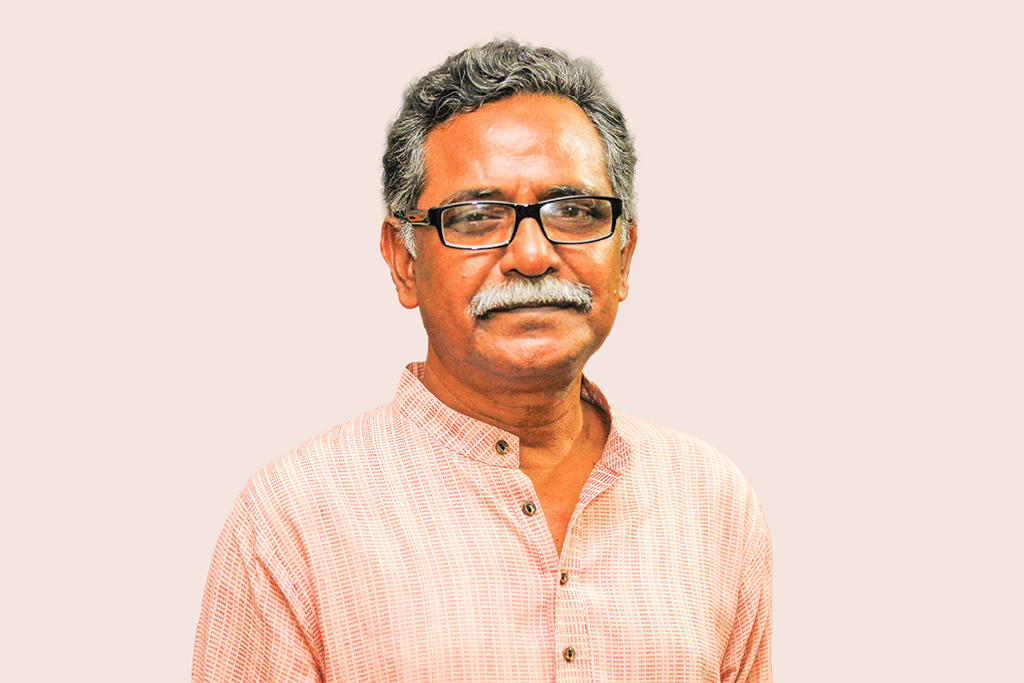
আনু মুহাম্মদ জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের সাবেক অধ্যাপক। তিনি ‘সর্বজনকথা’ পত্রিকার সম্পাদক। দীর্ঘদিন তেল-গ্যাস-খনিজ সম্পদ ও বিদ্যুৎ-বন্দর রক্ষা জাতীয় কমিটির সদস্যসচিব হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। বর্তমানে ‘গণতান্ত্রিক অধিকার কমিটি’র কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের দায়িত্ব পালন করছেন।
৮ ঘণ্টা আগে
এক নতুন সামরিক–রাজনৈতিক বাস্তবতায় প্রবেশ করল পাকিস্তান। ইসলামাবাদের পার্লামেন্ট ভবনে যেদিন সংবিধানের ২৭তম সংশোধনী পাস হলো। সিনেটে সামান্য হই হই চই এবং দুজন বিচারকের পদত্যাগ ছাড়া অনেকটা নিরবেই পাকিস্তানের ক্ষমতা কাঠামোয় ঐতিহাসিক রূপান্তর ঘটে গেল।
২০ ঘণ্টা আগেহুসাইন আহমদ

এক নতুন সামরিক–রাজনৈতিক বাস্তবতায় প্রবেশ করল পাকিস্তান। ইসলামাবাদের পার্লামেন্ট ভবনে যেদিন সংবিধানের ২৭তম সংশোধনী পাস হলো। সিনেটে সামান্য হই হই চই এবং দুজন বিচারকের পদত্যাগ ছাড়া অনেকটা নিরবেই পাকিস্তানের ক্ষমতা কাঠামোয় ঐতিহাসিক রূপান্তর ঘটে গেল।
যৌথতা, আধুনিকায়ন ও কার্যকারিতার নামে একটি রাষ্ট্রকে এক ব্যক্তিকেন্দ্রিক সামরিক আধিপত্যের দিকে ঠেলে দেওয়ার লিখিত অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। জনসাধারণের সামনে ‘সামরিক পুনর্গঠন’ হিসেবে তুলে ধরা হলেও পরিবর্তনকে একেবারে ‘সংবিধানপ্রণোদিত সামরিক একনায়কতন্ত্রের সূচনা’ বলছেন বিশ্লেষকেরা।
গত বৃহস্পতিবার আইনে পরিণত হওয়া সংবিধানের এই সংশোধনীর মাধ্যমে পাকিস্তানের সেনাপ্রধান ফিল্ড মার্শাল আসিম মুনিরকে সর্বময় সামরিক ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। গ্রেপ্তার ও বিচার থেকে আজীবন দায়মুক্তি পেয়েছেন তিনি। শুধু তাই নয়, গণতান্ত্রিকভাবে দুর্বল পাকিস্তানের জনগণের জন্য কিছুটা ভরসার জায়গা বিচার বিভাগকেও দুর্বল করে দেওয়া হয়েছে।
পারমাণবিক ক্ষমতাধর পাকিস্তানে রাজনীতিতে সেনাবাহিনীর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নতুন নয়। অভ্যুত্থানের মাধ্যমে ক্ষমতা দখল এবং পর্দার আড়ালে থেকে কলকাঠি নাড়ার নজির বহু আছে। জেনারেল পারভেজ মোশাররফ ও জেনারেল জিয়া-উল-হক তাঁর উদাহরণ। কিন্তু গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া অনুসরণ করে সামরিক ক্ষমতাকে গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানের ওপর স্থান দেওয়ার এই ঘটনা নজিরবিহীন ও সুদূরপ্রসারী।
১. সংবিধানের এই সংশোধীর ফলে সেনাপ্রধান আসিম মুনির প্রতিরক্ষা বাহিনীর প্রধান (সিডিএফ) হলেন। অর্থাৎ তিন বাহিনী, কৌশলগত কমান্ড, এমনকি পারমাণবিক বাহিনী তত্ত্বাবধানকারী কাঠামোর ওপরও তাঁর পূর্ণ কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হলো। এর ফলে কার্যত তিন বাহিনীর ভেতরের ভারসাম্য ভেঙে গেল। তিন বাহিনীর যৌথ নেতৃত্বের দীর্ঘ ৫ দশকের প্রাতিষ্ঠানিক ভূমিকা বাতিল হয়ে সেনাপ্রধানের একনায়ক হওয়ার পথ তৈরি হলো।
এই পরিবর্তনকে ‘আধুনিক যুদ্ধের প্রয়োজনে নেওয়া পদক্ষেপ’ বলে দাবি করছে পাকিস্তান সরকার। কিন্তু বাস্তবে এর মাধ্যমে সর্বময় ক্ষমতা পেয়েছেন সেনাপ্রধান— প্রতিরক্ষা বাহিনীর প্রধানের ভূমিকা, ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব অত্যন্ত উন্মুক্ত রাখা হয়েছে; তাঁর সিদ্ধান্তের ওপর পার্লামেন্টের কার্যত কোনো নিয়ন্ত্রণ রাখা হয়নি এবং এই পদের দায়িত্ব ও বাহিনীর কাঠামো ঠিক নির্ধারণের দায়িত্ব স্পষ্ট করা হয়নি। এই পরিবর্তন পাকিস্তানের ‘চেক অ্যান্ড ব্যালান্স’ ব্যবস্থা দুর্বল করে সামরিক কাঠামোকে আরও বেশি ব্যক্তিনির্ভর করে তুলেছে।
বিমানবাহিনীর সাবেক প্রধান এয়ার চিফ মার্শাল আব্বাস খট্টাক ডনকে বলেছেন, আধুনিক যুদ্ধের বাস্তবতা বলে, বিমান, নৌ ও স্থল বাহিনীর স্বাধীনতা ও সমন্বয়ই শক্তির উৎস। কিন্তু পাকিস্তান উল্টোপথে হাঁটছে। তিনি বলেন, ‘আমরা যদি বিশ্বমানের চর্চা থেকে সরে যাই, তাহলে এককেন্দ্রিক ক্ষমতা ভবিষ্যতে কৌশলগত ভুলের ঝুঁকি বাড়াবে।’
বিশেষ করে নতুন ন্যাশনাল স্ট্র্যাটেজিক কমান্ডের অধীনে তিন বাহিনীর পারমাণবিক ডেলিভারি সিস্টেম এক ছাতার নিচে আনা হলে বিমান ও নৌবাহিনীর কৌশলগত স্বাধীনতা আরও কমে যাওয়ার শঙ্কা দেখা দিয়েছে।
জর্জটাউন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক আকিল শাহ খোলাখুলি বলেছেন, ‘এটি মুনিরের ক্ষমতার দখলকে আরও পাকাপোক্ত করেছে। পার্লামেন্ট এমনভাবে একজন সামরিক প্রধানের আধিপত্যকে বৈধতা দিয়েছে, যা আমরা আগে কখনও দেখিনি।’ (দ্য গার্ডিয়ান) শাহের মতে, বিচার বিভাগ ও সংসদ উভয়কেই ঠেলে দেওয়া হয়েছে প্রান্তে—যা গণতন্ত্রের স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্য নয়।
২. পাকিস্তানের পারমাণবিক কাঠামো এখনো রাজনৈতিক নেতৃত্ব থাকলেও সংবিধান সংশোধনীর মাধ্যমে কর্তৃত্বের ভারসাম্য বদলে গেছে। ন্যাশনাল কমান্ড অথরিটি–এনসিএ কাঠামোগতভাবে এখনও বেসামরিক নেতৃত্বাধীন। কিন্তু ন্যাশনাল স্ট্র্যাটেজিক কমান্ডারের (সিএনএসসি) নিয়োগ, পুনঃনিয়োগ ও মেয়াদ বৃদ্ধির সিদ্ধান্ত এখন নির্ভর করবে কেবলমাত্র সিডিএফের সুপারিশের ওপর।
কেবল তাই নয়, কফিনে শেষ পেরেক ঠুকার মতো এই সিদ্ধান্তের ওপর বিচার বিভাগীয় পর্যালোচনা নিষিদ্ধ করা হয়েছে। সংশোধিত সংবিধানের ধারা ৮ই (২) অনুযায়ী, সিএনএসসির নিয়োগ বা মেয়াদ বৃদ্ধির বিষয়টি কোনো আদালতে চ্যালেঞ্জ করা যাবে না। আইন বিশেষজ্ঞরা বলছেন—এটা পাকিস্তানের সংবিধানের ৪, ৯ ও ১৯৯ অনুচ্ছেদের সঙ্গে সাংঘর্ষিক। কারণ, রাষ্ট্রের সকল নাগরিক আইনের সামনে সমান এবং প্রশাসনিক সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আইনি প্রতিকার সাংবিধানিক অধিকার।
পাকিস্তানের সাবেক সামরিক আইন কর্মকর্তা ইনাম-উর-রহিম বলেন, ‘সশস্ত্র বাহিনীর যেকোনো সিদ্ধান্ত, যদি তা অনিয়ম বা কর্তৃত্ববহির্ভূত হয়, তা উচ্চ আদালতে বিচারযোগ্য— এটাই সুপ্রতিষ্ঠিত নীতি।’
এটা পাকিস্তানের পারমাণবিক স্থাপত্যে সেনাবাহিনীর প্রভাবকে আরও স্থায়ী করে তুলছে, যা আইনের শাসনের জন্য বড় চ্যালেঞ্জ।
৩. সামরিক কাঠামোর এই পুনর্গঠনের অন্যতম ফল হলো ক্ষমতার চূড়ান্ত কেন্দ্রে একজন ব্যক্তির দীর্ঘায়িত মেয়াদ। প্রতিরক্ষা বাহিনী তথা সেনাবাহিনীর প্রধানের মেয়াদ ২০৩০ সাল পর্যন্ত বাড়ানো এবং নির্দিষ্ট পরিস্থিতিতে তা ২০৩৫ পর্যন্ত যাওয়ার সুযোগ তৈরি করা। অর্থাৎ পাকিস্তানের পুরো প্রতিরক্ষা কাঠামো প্রায় এক দশকজুড়ে এক ব্যক্তির সিদ্ধান্ত, দৃষ্টিভঙ্গি ও রাজনৈতিক অবস্থানের ওপর নির্ভরশীল হবে।
সেনাপ্রধান ফিল্ড মার্শাল আসিম মুনিরকে দীর্ঘায়িত ও সর্বময় ক্ষমতার পাশাপাশি কোনো অপরাধে গ্রেপ্তর ও বিচার থেকেও আজীবন দায়মুক্তি দেওয়া হয়েছে।
পাকিস্তানের সাবেক প্রতিরক্ষা সচিব লেফটেন্যান্ট জেনারেল (অব) আসিফ ইয়াসিন মালিক এই বিষয়ে কড়া মন্তব্য দিয়েছেন। তিনি বলেন, ‘মনে হচ্ছে এক ব্যক্তির জন্য আইন করা হলো, প্রাতিষ্ঠানিক কল্যাণের জন্য নয়।’ (ডন)
তাঁর মতে, তিন বাহিনীর প্রয়োজনে নয়, একজন ব্যক্তিকে সামনে রেখে এই আইন প্রণীত হলো। পাকিস্তানের সাবেক রাষ্ট্রদূত মালিহা লোধির মতে, ‘এই আইনি পুনর্গঠন শুধু সামরিক ক্ষমতা বাড়ায়নি, পাকিস্তানের বিচার কাঠামোকেও দুর্বল করে দিয়েছে।’
৪. নিজ বাহিনীর ভেতরে পদোন্নতি-বদলির বিষয়ে বিমান ও নৌবাহিনী প্রধানের ক্ষমতা খর্ব হলো। এখন এই বাহিনী প্রধানদের হাতে কেবল থ্রি স্টার অর্থাৎ লেফটেন্যান্ট জেনারেল ও নিচের পদমর্যাদার পদোন্নতি-বদলির ওপর ক্ষমতা থাকল। ফোর স্টার সব নিয়োগ ভবিষ্যতে প্রতিরক্ষা বাহিনীর প্রধানের সঙ্গে ‘আনুষ্ঠানিক বা অনানুষ্ঠানিক পরামর্শে’ হবে। অর্থাৎ বাকি দুই বাহিনী প্রধানদের ভূমিকা ও প্রভাব কমল।
বিশ্লেষকেরা বলছেন, পাকিস্তানের সামরিক বাহিনীর পুরনো কাঠামোতে সমস্যা থাকলেও নতুন কাঠামো কোনো সমাধান নয়। সিজেসিএসসি বহু বছর ধরেই আনুষ্ঠানিক পদ হিসেবে ছিল এবং তিন বাহিনী কার্যত সমান্তরাল আমলাতন্ত্রের মতো চলত। কিন্তু যেভাবে পাকিস্তানে সেনাপ্রধানকে সর্বোচ্চ ক্ষমতা দেওয়া হলো, সেই পথটি উল্টো। যুক্তরাষ্ট্র বা ভারতের মতো দেশও তিন বাহিনীতে যৌথতা এনেছে, তবে স্বাধীন যৌথ কমান্ড গড়ে তুলে।
বাস্তবে ফিল্ড মার্শাল আসিম মুনিরের অধীনে সামরিক কাঠামো এখন এমন এক অবস্থায় পৌঁছেছে যেখানে— বাহিনীসমূহের ভারসাম্য দুর্বল, বিচার বিভাগের ভূমিকা সংকুচিত, পারমাণবিক স্থাপত্যে সেনাবাহিনীর আধিপত্য সুসংহত, এবং প্রতিরক্ষা নীতি-পরিকল্পনা কার্যত একজন ব্যক্তির পছন্দ-অপছন্দের ওপর নির্ভরশীল।
এমন পরিবর্তনে উদ্বেগ তুলে ধরে পাকিস্তানের নিরাপত্তা বিশ্লেষক মজিদ নিজামী আল জাজিরাকে বলেন, সিডিএফের নতুন ভূমিকা অস্পষ্ট এবং তিন বাহিনীর কৌশলগত সমন্বয় বিপর্যস্ত হতে পারে। কাঠামোর অস্পষ্টতা ভবিষ্যতের সংঘাতে সিদ্ধান্ত বিভ্রান্তি ডেকে আনতে পারে বলে তিনি সতর্ক করেন।
সিদ্ধান্ত গ্রহণ, নিয়োগ–বদলি ও কৌশলগত বাহিনীর নিয়ন্ত্রণ এক ব্যক্তির হাতে কেন্দ্রীভূত হলে রাষ্ট্র প্রাতিষ্ঠানিক শক্তি হারাবে। সেই মুহূর্তে একনায়কতন্ত্র আর সম্ভাবনার পর্যায়ে থাকে না, তা বাস্তবে পরিণত হওয়ার ঝুঁকি তৈরি করে। পাকিস্তান সেই রূপান্তরের দুয়ারে দাঁড়িয়ে। কারণ, পার্লামেন্ট যে আইন পাস করেছে, তা শুধু প্রশাসনিক কাঠামো পাল্টায়নি, রাষ্ট্রকে কার্যত এক ব্যক্তিনির্ভর সামরিক সিদ্ধান্তপ্রক্রিয়ার দিকে ঠেলে দিয়েছে।
পাকিস্তানের বেসামরিক সরকার কি তার কার্যক্ষমতা ধরে রাখতে পারবে? সেনাবাহিনীর তিন শাখার মধ্যে ভারসাম্য কি বজায় থাকবে? বিচার বিভাগ ও সংসদ কি একনায়কতান্ত্রিক প্রবণতার বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়তে সক্ষম হবে? সময় জবাব দেবে এসব প্রশ্নের।

এক নতুন সামরিক–রাজনৈতিক বাস্তবতায় প্রবেশ করল পাকিস্তান। ইসলামাবাদের পার্লামেন্ট ভবনে যেদিন সংবিধানের ২৭তম সংশোধনী পাস হলো। সিনেটে সামান্য হই হই চই এবং দুজন বিচারকের পদত্যাগ ছাড়া অনেকটা নিরবেই পাকিস্তানের ক্ষমতা কাঠামোয় ঐতিহাসিক রূপান্তর ঘটে গেল।
যৌথতা, আধুনিকায়ন ও কার্যকারিতার নামে একটি রাষ্ট্রকে এক ব্যক্তিকেন্দ্রিক সামরিক আধিপত্যের দিকে ঠেলে দেওয়ার লিখিত অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। জনসাধারণের সামনে ‘সামরিক পুনর্গঠন’ হিসেবে তুলে ধরা হলেও পরিবর্তনকে একেবারে ‘সংবিধানপ্রণোদিত সামরিক একনায়কতন্ত্রের সূচনা’ বলছেন বিশ্লেষকেরা।
গত বৃহস্পতিবার আইনে পরিণত হওয়া সংবিধানের এই সংশোধনীর মাধ্যমে পাকিস্তানের সেনাপ্রধান ফিল্ড মার্শাল আসিম মুনিরকে সর্বময় সামরিক ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। গ্রেপ্তার ও বিচার থেকে আজীবন দায়মুক্তি পেয়েছেন তিনি। শুধু তাই নয়, গণতান্ত্রিকভাবে দুর্বল পাকিস্তানের জনগণের জন্য কিছুটা ভরসার জায়গা বিচার বিভাগকেও দুর্বল করে দেওয়া হয়েছে।
পারমাণবিক ক্ষমতাধর পাকিস্তানে রাজনীতিতে সেনাবাহিনীর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নতুন নয়। অভ্যুত্থানের মাধ্যমে ক্ষমতা দখল এবং পর্দার আড়ালে থেকে কলকাঠি নাড়ার নজির বহু আছে। জেনারেল পারভেজ মোশাররফ ও জেনারেল জিয়া-উল-হক তাঁর উদাহরণ। কিন্তু গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া অনুসরণ করে সামরিক ক্ষমতাকে গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানের ওপর স্থান দেওয়ার এই ঘটনা নজিরবিহীন ও সুদূরপ্রসারী।
১. সংবিধানের এই সংশোধীর ফলে সেনাপ্রধান আসিম মুনির প্রতিরক্ষা বাহিনীর প্রধান (সিডিএফ) হলেন। অর্থাৎ তিন বাহিনী, কৌশলগত কমান্ড, এমনকি পারমাণবিক বাহিনী তত্ত্বাবধানকারী কাঠামোর ওপরও তাঁর পূর্ণ কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হলো। এর ফলে কার্যত তিন বাহিনীর ভেতরের ভারসাম্য ভেঙে গেল। তিন বাহিনীর যৌথ নেতৃত্বের দীর্ঘ ৫ দশকের প্রাতিষ্ঠানিক ভূমিকা বাতিল হয়ে সেনাপ্রধানের একনায়ক হওয়ার পথ তৈরি হলো।
এই পরিবর্তনকে ‘আধুনিক যুদ্ধের প্রয়োজনে নেওয়া পদক্ষেপ’ বলে দাবি করছে পাকিস্তান সরকার। কিন্তু বাস্তবে এর মাধ্যমে সর্বময় ক্ষমতা পেয়েছেন সেনাপ্রধান— প্রতিরক্ষা বাহিনীর প্রধানের ভূমিকা, ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব অত্যন্ত উন্মুক্ত রাখা হয়েছে; তাঁর সিদ্ধান্তের ওপর পার্লামেন্টের কার্যত কোনো নিয়ন্ত্রণ রাখা হয়নি এবং এই পদের দায়িত্ব ও বাহিনীর কাঠামো ঠিক নির্ধারণের দায়িত্ব স্পষ্ট করা হয়নি। এই পরিবর্তন পাকিস্তানের ‘চেক অ্যান্ড ব্যালান্স’ ব্যবস্থা দুর্বল করে সামরিক কাঠামোকে আরও বেশি ব্যক্তিনির্ভর করে তুলেছে।
বিমানবাহিনীর সাবেক প্রধান এয়ার চিফ মার্শাল আব্বাস খট্টাক ডনকে বলেছেন, আধুনিক যুদ্ধের বাস্তবতা বলে, বিমান, নৌ ও স্থল বাহিনীর স্বাধীনতা ও সমন্বয়ই শক্তির উৎস। কিন্তু পাকিস্তান উল্টোপথে হাঁটছে। তিনি বলেন, ‘আমরা যদি বিশ্বমানের চর্চা থেকে সরে যাই, তাহলে এককেন্দ্রিক ক্ষমতা ভবিষ্যতে কৌশলগত ভুলের ঝুঁকি বাড়াবে।’
বিশেষ করে নতুন ন্যাশনাল স্ট্র্যাটেজিক কমান্ডের অধীনে তিন বাহিনীর পারমাণবিক ডেলিভারি সিস্টেম এক ছাতার নিচে আনা হলে বিমান ও নৌবাহিনীর কৌশলগত স্বাধীনতা আরও কমে যাওয়ার শঙ্কা দেখা দিয়েছে।
জর্জটাউন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক আকিল শাহ খোলাখুলি বলেছেন, ‘এটি মুনিরের ক্ষমতার দখলকে আরও পাকাপোক্ত করেছে। পার্লামেন্ট এমনভাবে একজন সামরিক প্রধানের আধিপত্যকে বৈধতা দিয়েছে, যা আমরা আগে কখনও দেখিনি।’ (দ্য গার্ডিয়ান) শাহের মতে, বিচার বিভাগ ও সংসদ উভয়কেই ঠেলে দেওয়া হয়েছে প্রান্তে—যা গণতন্ত্রের স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্য নয়।
২. পাকিস্তানের পারমাণবিক কাঠামো এখনো রাজনৈতিক নেতৃত্ব থাকলেও সংবিধান সংশোধনীর মাধ্যমে কর্তৃত্বের ভারসাম্য বদলে গেছে। ন্যাশনাল কমান্ড অথরিটি–এনসিএ কাঠামোগতভাবে এখনও বেসামরিক নেতৃত্বাধীন। কিন্তু ন্যাশনাল স্ট্র্যাটেজিক কমান্ডারের (সিএনএসসি) নিয়োগ, পুনঃনিয়োগ ও মেয়াদ বৃদ্ধির সিদ্ধান্ত এখন নির্ভর করবে কেবলমাত্র সিডিএফের সুপারিশের ওপর।
কেবল তাই নয়, কফিনে শেষ পেরেক ঠুকার মতো এই সিদ্ধান্তের ওপর বিচার বিভাগীয় পর্যালোচনা নিষিদ্ধ করা হয়েছে। সংশোধিত সংবিধানের ধারা ৮ই (২) অনুযায়ী, সিএনএসসির নিয়োগ বা মেয়াদ বৃদ্ধির বিষয়টি কোনো আদালতে চ্যালেঞ্জ করা যাবে না। আইন বিশেষজ্ঞরা বলছেন—এটা পাকিস্তানের সংবিধানের ৪, ৯ ও ১৯৯ অনুচ্ছেদের সঙ্গে সাংঘর্ষিক। কারণ, রাষ্ট্রের সকল নাগরিক আইনের সামনে সমান এবং প্রশাসনিক সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আইনি প্রতিকার সাংবিধানিক অধিকার।
পাকিস্তানের সাবেক সামরিক আইন কর্মকর্তা ইনাম-উর-রহিম বলেন, ‘সশস্ত্র বাহিনীর যেকোনো সিদ্ধান্ত, যদি তা অনিয়ম বা কর্তৃত্ববহির্ভূত হয়, তা উচ্চ আদালতে বিচারযোগ্য— এটাই সুপ্রতিষ্ঠিত নীতি।’
এটা পাকিস্তানের পারমাণবিক স্থাপত্যে সেনাবাহিনীর প্রভাবকে আরও স্থায়ী করে তুলছে, যা আইনের শাসনের জন্য বড় চ্যালেঞ্জ।
৩. সামরিক কাঠামোর এই পুনর্গঠনের অন্যতম ফল হলো ক্ষমতার চূড়ান্ত কেন্দ্রে একজন ব্যক্তির দীর্ঘায়িত মেয়াদ। প্রতিরক্ষা বাহিনী তথা সেনাবাহিনীর প্রধানের মেয়াদ ২০৩০ সাল পর্যন্ত বাড়ানো এবং নির্দিষ্ট পরিস্থিতিতে তা ২০৩৫ পর্যন্ত যাওয়ার সুযোগ তৈরি করা। অর্থাৎ পাকিস্তানের পুরো প্রতিরক্ষা কাঠামো প্রায় এক দশকজুড়ে এক ব্যক্তির সিদ্ধান্ত, দৃষ্টিভঙ্গি ও রাজনৈতিক অবস্থানের ওপর নির্ভরশীল হবে।
সেনাপ্রধান ফিল্ড মার্শাল আসিম মুনিরকে দীর্ঘায়িত ও সর্বময় ক্ষমতার পাশাপাশি কোনো অপরাধে গ্রেপ্তর ও বিচার থেকেও আজীবন দায়মুক্তি দেওয়া হয়েছে।
পাকিস্তানের সাবেক প্রতিরক্ষা সচিব লেফটেন্যান্ট জেনারেল (অব) আসিফ ইয়াসিন মালিক এই বিষয়ে কড়া মন্তব্য দিয়েছেন। তিনি বলেন, ‘মনে হচ্ছে এক ব্যক্তির জন্য আইন করা হলো, প্রাতিষ্ঠানিক কল্যাণের জন্য নয়।’ (ডন)
তাঁর মতে, তিন বাহিনীর প্রয়োজনে নয়, একজন ব্যক্তিকে সামনে রেখে এই আইন প্রণীত হলো। পাকিস্তানের সাবেক রাষ্ট্রদূত মালিহা লোধির মতে, ‘এই আইনি পুনর্গঠন শুধু সামরিক ক্ষমতা বাড়ায়নি, পাকিস্তানের বিচার কাঠামোকেও দুর্বল করে দিয়েছে।’
৪. নিজ বাহিনীর ভেতরে পদোন্নতি-বদলির বিষয়ে বিমান ও নৌবাহিনী প্রধানের ক্ষমতা খর্ব হলো। এখন এই বাহিনী প্রধানদের হাতে কেবল থ্রি স্টার অর্থাৎ লেফটেন্যান্ট জেনারেল ও নিচের পদমর্যাদার পদোন্নতি-বদলির ওপর ক্ষমতা থাকল। ফোর স্টার সব নিয়োগ ভবিষ্যতে প্রতিরক্ষা বাহিনীর প্রধানের সঙ্গে ‘আনুষ্ঠানিক বা অনানুষ্ঠানিক পরামর্শে’ হবে। অর্থাৎ বাকি দুই বাহিনী প্রধানদের ভূমিকা ও প্রভাব কমল।
বিশ্লেষকেরা বলছেন, পাকিস্তানের সামরিক বাহিনীর পুরনো কাঠামোতে সমস্যা থাকলেও নতুন কাঠামো কোনো সমাধান নয়। সিজেসিএসসি বহু বছর ধরেই আনুষ্ঠানিক পদ হিসেবে ছিল এবং তিন বাহিনী কার্যত সমান্তরাল আমলাতন্ত্রের মতো চলত। কিন্তু যেভাবে পাকিস্তানে সেনাপ্রধানকে সর্বোচ্চ ক্ষমতা দেওয়া হলো, সেই পথটি উল্টো। যুক্তরাষ্ট্র বা ভারতের মতো দেশও তিন বাহিনীতে যৌথতা এনেছে, তবে স্বাধীন যৌথ কমান্ড গড়ে তুলে।
বাস্তবে ফিল্ড মার্শাল আসিম মুনিরের অধীনে সামরিক কাঠামো এখন এমন এক অবস্থায় পৌঁছেছে যেখানে— বাহিনীসমূহের ভারসাম্য দুর্বল, বিচার বিভাগের ভূমিকা সংকুচিত, পারমাণবিক স্থাপত্যে সেনাবাহিনীর আধিপত্য সুসংহত, এবং প্রতিরক্ষা নীতি-পরিকল্পনা কার্যত একজন ব্যক্তির পছন্দ-অপছন্দের ওপর নির্ভরশীল।
এমন পরিবর্তনে উদ্বেগ তুলে ধরে পাকিস্তানের নিরাপত্তা বিশ্লেষক মজিদ নিজামী আল জাজিরাকে বলেন, সিডিএফের নতুন ভূমিকা অস্পষ্ট এবং তিন বাহিনীর কৌশলগত সমন্বয় বিপর্যস্ত হতে পারে। কাঠামোর অস্পষ্টতা ভবিষ্যতের সংঘাতে সিদ্ধান্ত বিভ্রান্তি ডেকে আনতে পারে বলে তিনি সতর্ক করেন।
সিদ্ধান্ত গ্রহণ, নিয়োগ–বদলি ও কৌশলগত বাহিনীর নিয়ন্ত্রণ এক ব্যক্তির হাতে কেন্দ্রীভূত হলে রাষ্ট্র প্রাতিষ্ঠানিক শক্তি হারাবে। সেই মুহূর্তে একনায়কতন্ত্র আর সম্ভাবনার পর্যায়ে থাকে না, তা বাস্তবে পরিণত হওয়ার ঝুঁকি তৈরি করে। পাকিস্তান সেই রূপান্তরের দুয়ারে দাঁড়িয়ে। কারণ, পার্লামেন্ট যে আইন পাস করেছে, তা শুধু প্রশাসনিক কাঠামো পাল্টায়নি, রাষ্ট্রকে কার্যত এক ব্যক্তিনির্ভর সামরিক সিদ্ধান্তপ্রক্রিয়ার দিকে ঠেলে দিয়েছে।
পাকিস্তানের বেসামরিক সরকার কি তার কার্যক্ষমতা ধরে রাখতে পারবে? সেনাবাহিনীর তিন শাখার মধ্যে ভারসাম্য কি বজায় থাকবে? বিচার বিভাগ ও সংসদ কি একনায়কতান্ত্রিক প্রবণতার বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়তে সক্ষম হবে? সময় জবাব দেবে এসব প্রশ্নের।

এত জোরে এবং এমন অভদ্র ভাষায় ভদ্রলোক ধমক দিলেন তাঁর স্ত্রীকে যে ঘরের নানান কোণের আলাপের গুঞ্জন সঙ্গে সঙ্গে হঠাৎ করেই থেমে গেল। অদ্ভুত এক স্তব্ধতা নেমে এল সারা ঘরে। আমরা হতবাক—নিজেদের কানকেই কেউ আমরা বিশ্বাস করতে পারছিলাম না।
০৬ নভেম্বর ২০২৪
অন্তর্বর্তী সরকারপ্রধান অধ্যাপক ইউনূসের জাতির উদ্দেশে ভাষণের পর ফেব্রুয়ারিতে নির্বাচনের একটি আবহ তৈরি হয়েছে। জামায়াতে ইসলামী আর এনসিপি জুলাই সনদের ব্যাপারে একটা ফয়সালা না হলে নির্বাচনে যাবে না, এ রকম যে অবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল, প্রধান উপদেষ্টার ভাষণের পর সে অবস্থার পরিবর্তন হয়েছে বলে মনে হচ্ছে।
৮ ঘণ্টা আগে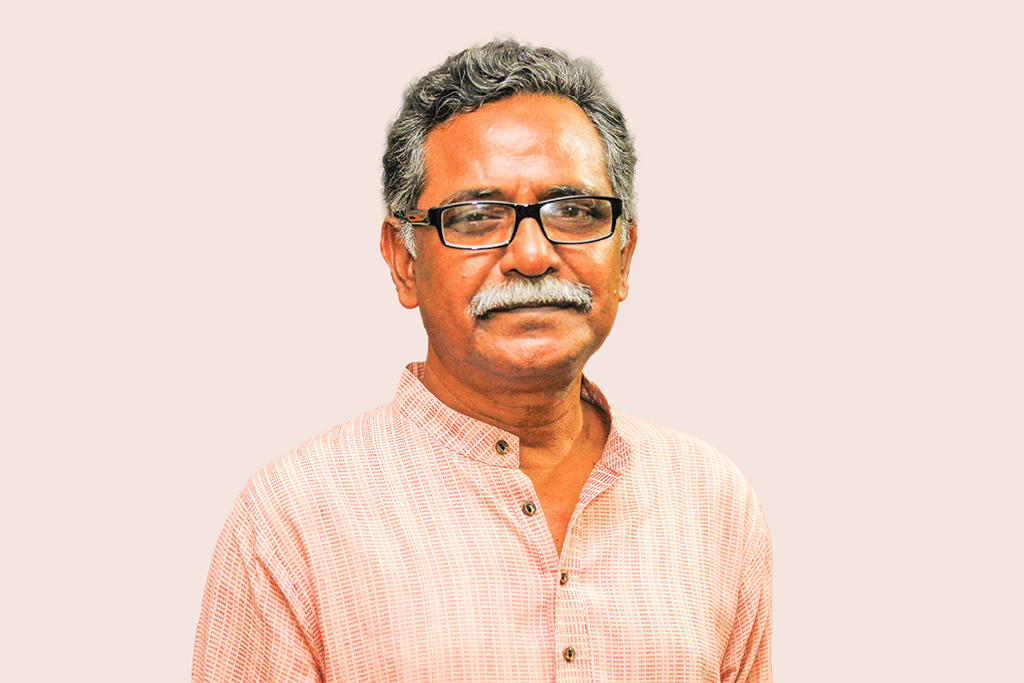
আনু মুহাম্মদ জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের সাবেক অধ্যাপক। তিনি ‘সর্বজনকথা’ পত্রিকার সম্পাদক। দীর্ঘদিন তেল-গ্যাস-খনিজ সম্পদ ও বিদ্যুৎ-বন্দর রক্ষা জাতীয় কমিটির সদস্যসচিব হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। বর্তমানে ‘গণতান্ত্রিক অধিকার কমিটি’র কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের দায়িত্ব পালন করছেন।
৮ ঘণ্টা আগে
একটা সময় মাছ মানেই ছিল রুই, কাতলা বা ইলিশ। কিন্তু এখন দেশের গ্রামীণ পুকুর থেকে শুরু করে শহরের হাটবাজার পর্যন্ত এক নতুন তারকার উত্থান—তেলাপিয়া। দ্রুত বৃদ্ধি, সহজ চাষপদ্ধতি এবং সাশ্রয়ী মূল্যের কারণে তেলাপিয়াকে বিশ্বের অনেক দেশেই বলা হয় ‘জলজ মুরগি’, কেউ বলে ‘গ্রামের রুপালি সম্পদ...
৮ ঘণ্টা আগে