জাহাঙ্গীর আলম, ঢাকা

গাছ লাগানো ভালো। প্রতিবছর ৫ জুন বিশ্ব পরিবেশ দিবস উপলক্ষে নানা দেশেই আজকাল গাছ রোপণের রেকর্ড হচ্ছে। কিন্তু এভাবে গাছ রোপণ কি আসলেই জলবায়ু পরিবর্তন ঠেকানোর জন্য যথেষ্ট? এতে কি গ্রীষ্মকালের প্রচণ্ড গরম সহনীয় পর্যায়ে আনা সম্ভব।
প্রকৃতপক্ষে রেকর্ডের উদ্দেশ্যে গাছ রোপণের কিছু নেতিবাচক দিক রয়েছে। ধরেই নেওয়া হয় এসব চারার মাত্র ৪০ শতাংশ শেষ পর্যন্ত টিকে যায়।
কিন্তু আসলেই কত শতাংশ টিকে থাকে, সে খবর তো আর নেওয়া হয় না। কারণ, চারা রোপণের পরবর্তী কয়েক মাস যে নিবিড় যত্নের প্রয়োজন হয়—সেটি করার মতো জনবল, অর্থবল ও ধৈর্য কোনোটাই সাধারণত দেখা যায় না। চারায় পানি দেওয়া, ছোট অবস্থায় গরু-ছাগলের মতো তৃণভোজী প্রাণীর হাত থেকে রক্ষা করা ইত্যাদি যত্নআত্তি সাধারণত হয় না। তা ছাড়া এসব রেকর্ডের বৃক্ষ রোপণে দেখা যায়, চারাগুলোর মাঝখানে যথেষ্ট দূরত্ব রাখা হয় না। ফলে এগুলো সঠিকভাবে বেড়ে উঠতে পারে না।
এই সময়ের সবচেয়ে বড় পরিবেশগত দুটি চ্যালেঞ্জ হলো, জলবায়ু পরিবর্তন এবং জীববৈচিত্র্যের ক্রম অবনতি। আয়োজন করে বৃক্ষরোপণ, কিন্তু এই ইস্যুতে খুব কমই কাজে আসে।
‘জলবায়ু পরিবর্তন’ বলতে মূলত একটি সামগ্রিক পরিস্থিতিকে বোঝানো হয়। যখন বায়ুমণ্ডলে এমন সব গ্যাসের ঘনত্ব বেড়ে যায়, যা মাত্রাতিরিক্ত তাপ ধরে রাখে। ফলে পরিবেশের তাপমাত্রা এবং আবহাওয়ায় অস্বাভাবিক পরিবর্তন আসতে শুরু করে। এটি ঘটে মূলত জীবাশ্ম জ্বালানি পোড়ানোর মাধ্যমে গ্রিন হাউস গ্যাস উৎপাদনের কারণে। এই প্রক্রিয়া বন্ধ করার সহজ সমাধান হলো পরিবেশ থেকে বিদ্যমান কার্বন ডাই-অক্সাইড কমানো। যৌক্তিক কারণেই মোক্ষম উপায় হিসেবে বেশি বেশি গাছ লাগানোর কথা বলা হয়। কারণ, গাছের খাদ্য উৎপাদনের প্রধান কাঁচামাল কার্বন ডাই-অক্সাইড। এই কার্বন ডাই-অক্সাইড প্রক্রিয়াজাত করে গাছ কাণ্ডে-শাখায় পুষ্ট হয়।
কিন্তু গাছ রোপণের ধারণায় যে বিষয়টি উপেক্ষা করা হয়, সেটি হলো যখন কোনো প্রাকৃতিক কারণেই একটি গাছের মৃত্যু ঘটে, ধীরে ধীরে সেই কার্বন দেহটি আবার বায়ুমণ্ডলেই ফিরে আসে। অথচ সেটি কোনো প্রাকৃতিক বনে জঙ্গলে ঘটলে মৃত গাছের ওপর অসংখ্য ক্ষুদ্র উদ্ভিদ ও প্রাণের সমাহার ঘটে, এরা কার্বন দেহটি হাইড্রো-কার্বন গ্যাস রূপে বায়ুমণ্ডলে ফিরে আসতে দেয় না। আটকা পড়ে যায়। তার মানে, গাছ যে বায়ুমণ্ডল থেকে কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্রহণ করছে, সেটি স্থায়ীভাবে ধরে রাখা সম্ভব শুধু প্রাকৃতিক বনেই।
বৃক্ষরোপণের আরেকটি বড় নেতিবাচক দিক হলো, এই পদক্ষেপ জীববৈচিত্র্য রক্ষায় কোনো কাজে আসে না, এমনকি কোনো কোনো ক্ষেত্রে জীববৈচিত্র্যের জন্য হুমকিও হতে পারে। এ ধরনের বৃক্ষরোপণের ক্ষেত্রে সাধারণত দ্রুত বর্ধনশীল, পাতা দ্রুত পচনশীল এবং চিরহরিৎ—এমন বৈশিষ্ট্যের গাছ পছন্দ করা হয়। ফলে সাধারণত স্থানীয় প্রজাতি উপেক্ষিত হয়। আমাদের দেশে ইউক্যালিপটাস, শিশু, রেইনট্রি, মেহগনি ইত্যাদি গাছ এভাবে জনপ্রিয় হয়েছে। এসব গাছ পাখিদের খাবার ও বাসস্থানের জন্য উপযোগী নয়। এসব গাছ প্রচুর পরিমাণে ভূগর্ভস্থ পানি শোষণ করে। জীববৈচিত্র্যের জন্যও কোনো উপকারে আসে না। বাতাসে প্রচুর রেণু ছড়িয়ে পড়ে। ফলে আশপাশে অ্যালার্জির সমস্যা বাড়ে।
এর মধ্যে কিছু গাছ আছে, অত্যন্ত দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে। এতে স্থানীয় বৃক্ষ প্রজাতি হুমকির মুখে পড়ে। এ কারণে আজকাল অবশ্য এসব বিদেশি গাছ রোপণ নিরুৎসাহিত করা হয়।
মজার বিষয় হলো, গ্রীষ্মকালে এসব গাছ তাপমাত্রা না কমিয়ে উল্টো বাড়িয়ে দিতে পারে। আবহাওয়া বিজ্ঞানে ‘ওয়েট বাল্ব টেম্পারেচার’ বলে একটি কথা আছে। বাতাসের আর্দ্রতা বেশি থাকলে, অর্থাৎ বাতাস যদি সম্পৃক্ত হয়; তাহলে বাষ্পীভবনের মাধ্যমে ঠান্ডা হওয়ার সুযোগ কমে যায়। এই কারণেই কিন্তু আর্দ্রতা বেশি থাকলে অস্বস্তি বাড়ে। শরীর ঘামলেও তাপমাত্রা কমে না। এতে হিট স্ট্রোকের ঝুঁকিও বাড়ে।
ওই সব বিদেশি গাছের প্রস্বেদনের হার স্থানীয় জাতের অনেক গাছের চেয়ে ঢের বেশি। ফলে এসব গাছ বেশি থাকলে সেই এলাকায় ওয়েট বাল্ব টেম্পারেচার পরিস্থিতি দেখা দিতে পারে।
সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, হাতে গোনা কয়েক প্রজাতির গাছ রোপণের মাধ্যমে বন তৈরি করা কখনো সম্ভব নয়। একটি বনের যে জটিল বাস্তুতন্ত্র থাকে, যার মাধ্যমে জীববৈচিত্র্য রক্ষিত হয়—সেটি এই তথাকথিত কৃত্রিম বনায়নের মাধ্যমে অসম্ভব।
একাধিক গবেষণায় প্রমাণিত, গাছ লাগানো প্রাকৃতিক বনের বিকল্প হতে পারে। ২০১৯ সালের দিকে ‘ফ্রন্টিয়ার ইন ফরেস্ট অ্যান্ড গ্লোবাল চেঞ্জ’ সাময়িকীতে প্রকাশিত একটি গবেষণায় দেখানো হয়, বিদ্যমান বনগুলোকে সেগুলোর পরিবেশগত সম্ভাবনা অক্ষত রেখে বাড়ানোর উদ্যোগ নেওয়াই বেশি কার্যকর উপায়। এটিকে বলে ‘প্রোফরেস্টেশন’। এই কৌশল বায়ুমণ্ডল থেকে গ্রিন হাউস গ্যাস অপসারণ এবং সংরক্ষণের জন্য বেশি কার্যকর। আর এতে ব্যয়ও কম।
জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত আন্তসরকারি প্যানেলের (আইপিসিসি) একটি প্রতিবেদনে সুন্দরবনের বর্তমান অবস্থার ওপর আলোকপাত করা হয়েছে। প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে, সুন্দরবনের ম্যানগ্রোভের বিশাল এলাকা গত দুই শতাব্দীতে ধানের খেত এবং সম্প্রতি চিংড়ির ঘেরে রূপান্তরিত হয়েছে। প্রতিবেদনে সতর্ক করা হয়েছে, ম্যানগ্রোভ বন ও জলাভূমি ধ্বংসের ফলে উপকূলীয় ভূমি ক্ষয় ত্বরান্বিত হতে পারে।
নেচার জার্নালে প্রকাশিত একটি সমীক্ষায় বলা হয়েছে, সংকুচিত হয়ে আসা বনের প্রাকৃতিক পুনর্জন্মের মাধ্যমে ক্যানোপি কভার (গাছের আচ্ছাদন) বৃদ্ধি করা, নতুন বৃক্ষরোপণের চেয়ে বেশি উপকারী হতে পারে। অন্তত এক শতাব্দীর মধ্যে জলবায়ু সুরক্ষায় উল্লেখযোগ্য সুফল এনে দিতে পারে।
এ কারণে প্রাকৃতিক বন পুনরুদ্ধারই এখন বিজ্ঞানী এবং নীতিনির্ধারকদের কাছে বেশি মনোযোগ পাচ্ছে। জার্মান সরকার এবং ইন্টারন্যাশনাল ইউনিয়ন ফর কনজারভেশন অব নেচার (আইইউসিএন) ২০৩০ সালের মধ্যে ৩৫ কোটি হেক্টর বন পুনরুদ্ধারের লক্ষ্য নির্ধারণ করেছে। এ ছাড়া গ্রীষ্মমণ্ডলীয় এবং উপক্রান্তীয় অঞ্চলের ৪৩টি দেশ বন পুনরুদ্ধারের অঙ্গীকার করেছে। উদাহরণস্বরূপ, ভিয়েতনাম ১ কোটি ৪৬ লাখ হেক্টর প্রাকৃতিক বন পুনরুদ্ধার করবে।
বাংলাদেশও এই প্রতিশ্রুতির বাইরে নেই। পরিসংখ্যান বলছে, দেশে গত ২০ বছরে ৪ দশমিক ১ শতাংশ প্রাথমিক বনাঞ্চল কমেছে। এর মধ্যে প্রায় সাড়ে ৩ শতাংশই কমেছে উত্তর-পূর্বাঞ্চলে। যদিও ব্যাপকভাবে বৃক্ষরোপণের মাধ্যমে ট্রি কভার (ক্যানোপি) বাড়ছে বলে দাবি করছে সরকার।
দুঃখের বিষয় হলো, বন রক্ষা এ দেশে সামাজিক আন্দোলনে রূপ নিতে পারেনি। প্রতিবছর গ্রীষ্মে যখন গরমে হাঁসফাঁস করতে থাকে মানুষ, তখনই বৃক্ষ নিধন নিয়ে বিলাপ, আর বেশি বেশি গাছ লাগানোর নছিহত চলতে থাকে।
এই ক্যাম্পেইন শহরে রীতিমতো ফ্যাশনে পরিণত হয়েছে। রাজধানীতে এক ইঞ্চি জায়গাও কেউ ছাড়তে চায় না। সেখানে বৃক্ষরোপণের আলাপ বিলাসিতা। যাঁদের বিলাসিতার সামর্থ্য আছে, তাঁরা তো বাড়ির সামনে গোছানো লন রাখেন। কিন্তু শহরের এই সুন্দর লনে তো প্রাণপ্রকৃতি রক্ষা পাবে না। অনেকেই এখন ছাদে বারান্দায় বাগান করছেন। কে জানে শৌখিন শহুরে মানুষের এই শখের ছাদবাগান থেকে উড়ে আসা এডিস মশার কামড়ে প্রতিবছর ডেঙ্গুতে হাজার হাজার মানুষের মৃত্যুতে হচ্ছে কি না!
গ্রীষ্মকালকে আবার সহনীয় করতে চাইলে আমাদের বরং উচিত, নির্বিচারে বন নিধনের পরও এখনো যতখানি টিকে আছে তার পুঙ্খানুপুঙ্খ পরিসংখ্যান ও মানচিত্র তৈরি করে সেগুলো সংরক্ষণ, পুনরুদ্ধার ও বর্ধনে জোর দেওয়া। বিভিন্ন এলাকায় এখনো পুরোনো ও বৃহৎ বৃক্ষ টিকে রয়েছে, সেগুলো সংরক্ষণে নজর দিতে হবে। বাড়াতে হবে জলাধার, উন্মুক্ত মাটি। সেই সঙ্গে পরিবেশবান্ধব ভবন নির্মাণে দায়বদ্ধতা। আরও দরকার ব্যক্তিগত পরিবহন কমিয়ে গণপরিবহন এবং হাঁটার উপযোগী ফুটপাত।
লেখক: আজকের পত্রিকার জ্যেষ্ঠ সহসম্পাদক

গাছ লাগানো ভালো। প্রতিবছর ৫ জুন বিশ্ব পরিবেশ দিবস উপলক্ষে নানা দেশেই আজকাল গাছ রোপণের রেকর্ড হচ্ছে। কিন্তু এভাবে গাছ রোপণ কি আসলেই জলবায়ু পরিবর্তন ঠেকানোর জন্য যথেষ্ট? এতে কি গ্রীষ্মকালের প্রচণ্ড গরম সহনীয় পর্যায়ে আনা সম্ভব।
প্রকৃতপক্ষে রেকর্ডের উদ্দেশ্যে গাছ রোপণের কিছু নেতিবাচক দিক রয়েছে। ধরেই নেওয়া হয় এসব চারার মাত্র ৪০ শতাংশ শেষ পর্যন্ত টিকে যায়।
কিন্তু আসলেই কত শতাংশ টিকে থাকে, সে খবর তো আর নেওয়া হয় না। কারণ, চারা রোপণের পরবর্তী কয়েক মাস যে নিবিড় যত্নের প্রয়োজন হয়—সেটি করার মতো জনবল, অর্থবল ও ধৈর্য কোনোটাই সাধারণত দেখা যায় না। চারায় পানি দেওয়া, ছোট অবস্থায় গরু-ছাগলের মতো তৃণভোজী প্রাণীর হাত থেকে রক্ষা করা ইত্যাদি যত্নআত্তি সাধারণত হয় না। তা ছাড়া এসব রেকর্ডের বৃক্ষ রোপণে দেখা যায়, চারাগুলোর মাঝখানে যথেষ্ট দূরত্ব রাখা হয় না। ফলে এগুলো সঠিকভাবে বেড়ে উঠতে পারে না।
এই সময়ের সবচেয়ে বড় পরিবেশগত দুটি চ্যালেঞ্জ হলো, জলবায়ু পরিবর্তন এবং জীববৈচিত্র্যের ক্রম অবনতি। আয়োজন করে বৃক্ষরোপণ, কিন্তু এই ইস্যুতে খুব কমই কাজে আসে।
‘জলবায়ু পরিবর্তন’ বলতে মূলত একটি সামগ্রিক পরিস্থিতিকে বোঝানো হয়। যখন বায়ুমণ্ডলে এমন সব গ্যাসের ঘনত্ব বেড়ে যায়, যা মাত্রাতিরিক্ত তাপ ধরে রাখে। ফলে পরিবেশের তাপমাত্রা এবং আবহাওয়ায় অস্বাভাবিক পরিবর্তন আসতে শুরু করে। এটি ঘটে মূলত জীবাশ্ম জ্বালানি পোড়ানোর মাধ্যমে গ্রিন হাউস গ্যাস উৎপাদনের কারণে। এই প্রক্রিয়া বন্ধ করার সহজ সমাধান হলো পরিবেশ থেকে বিদ্যমান কার্বন ডাই-অক্সাইড কমানো। যৌক্তিক কারণেই মোক্ষম উপায় হিসেবে বেশি বেশি গাছ লাগানোর কথা বলা হয়। কারণ, গাছের খাদ্য উৎপাদনের প্রধান কাঁচামাল কার্বন ডাই-অক্সাইড। এই কার্বন ডাই-অক্সাইড প্রক্রিয়াজাত করে গাছ কাণ্ডে-শাখায় পুষ্ট হয়।
কিন্তু গাছ রোপণের ধারণায় যে বিষয়টি উপেক্ষা করা হয়, সেটি হলো যখন কোনো প্রাকৃতিক কারণেই একটি গাছের মৃত্যু ঘটে, ধীরে ধীরে সেই কার্বন দেহটি আবার বায়ুমণ্ডলেই ফিরে আসে। অথচ সেটি কোনো প্রাকৃতিক বনে জঙ্গলে ঘটলে মৃত গাছের ওপর অসংখ্য ক্ষুদ্র উদ্ভিদ ও প্রাণের সমাহার ঘটে, এরা কার্বন দেহটি হাইড্রো-কার্বন গ্যাস রূপে বায়ুমণ্ডলে ফিরে আসতে দেয় না। আটকা পড়ে যায়। তার মানে, গাছ যে বায়ুমণ্ডল থেকে কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্রহণ করছে, সেটি স্থায়ীভাবে ধরে রাখা সম্ভব শুধু প্রাকৃতিক বনেই।
বৃক্ষরোপণের আরেকটি বড় নেতিবাচক দিক হলো, এই পদক্ষেপ জীববৈচিত্র্য রক্ষায় কোনো কাজে আসে না, এমনকি কোনো কোনো ক্ষেত্রে জীববৈচিত্র্যের জন্য হুমকিও হতে পারে। এ ধরনের বৃক্ষরোপণের ক্ষেত্রে সাধারণত দ্রুত বর্ধনশীল, পাতা দ্রুত পচনশীল এবং চিরহরিৎ—এমন বৈশিষ্ট্যের গাছ পছন্দ করা হয়। ফলে সাধারণত স্থানীয় প্রজাতি উপেক্ষিত হয়। আমাদের দেশে ইউক্যালিপটাস, শিশু, রেইনট্রি, মেহগনি ইত্যাদি গাছ এভাবে জনপ্রিয় হয়েছে। এসব গাছ পাখিদের খাবার ও বাসস্থানের জন্য উপযোগী নয়। এসব গাছ প্রচুর পরিমাণে ভূগর্ভস্থ পানি শোষণ করে। জীববৈচিত্র্যের জন্যও কোনো উপকারে আসে না। বাতাসে প্রচুর রেণু ছড়িয়ে পড়ে। ফলে আশপাশে অ্যালার্জির সমস্যা বাড়ে।
এর মধ্যে কিছু গাছ আছে, অত্যন্ত দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে। এতে স্থানীয় বৃক্ষ প্রজাতি হুমকির মুখে পড়ে। এ কারণে আজকাল অবশ্য এসব বিদেশি গাছ রোপণ নিরুৎসাহিত করা হয়।
মজার বিষয় হলো, গ্রীষ্মকালে এসব গাছ তাপমাত্রা না কমিয়ে উল্টো বাড়িয়ে দিতে পারে। আবহাওয়া বিজ্ঞানে ‘ওয়েট বাল্ব টেম্পারেচার’ বলে একটি কথা আছে। বাতাসের আর্দ্রতা বেশি থাকলে, অর্থাৎ বাতাস যদি সম্পৃক্ত হয়; তাহলে বাষ্পীভবনের মাধ্যমে ঠান্ডা হওয়ার সুযোগ কমে যায়। এই কারণেই কিন্তু আর্দ্রতা বেশি থাকলে অস্বস্তি বাড়ে। শরীর ঘামলেও তাপমাত্রা কমে না। এতে হিট স্ট্রোকের ঝুঁকিও বাড়ে।
ওই সব বিদেশি গাছের প্রস্বেদনের হার স্থানীয় জাতের অনেক গাছের চেয়ে ঢের বেশি। ফলে এসব গাছ বেশি থাকলে সেই এলাকায় ওয়েট বাল্ব টেম্পারেচার পরিস্থিতি দেখা দিতে পারে।
সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, হাতে গোনা কয়েক প্রজাতির গাছ রোপণের মাধ্যমে বন তৈরি করা কখনো সম্ভব নয়। একটি বনের যে জটিল বাস্তুতন্ত্র থাকে, যার মাধ্যমে জীববৈচিত্র্য রক্ষিত হয়—সেটি এই তথাকথিত কৃত্রিম বনায়নের মাধ্যমে অসম্ভব।
একাধিক গবেষণায় প্রমাণিত, গাছ লাগানো প্রাকৃতিক বনের বিকল্প হতে পারে। ২০১৯ সালের দিকে ‘ফ্রন্টিয়ার ইন ফরেস্ট অ্যান্ড গ্লোবাল চেঞ্জ’ সাময়িকীতে প্রকাশিত একটি গবেষণায় দেখানো হয়, বিদ্যমান বনগুলোকে সেগুলোর পরিবেশগত সম্ভাবনা অক্ষত রেখে বাড়ানোর উদ্যোগ নেওয়াই বেশি কার্যকর উপায়। এটিকে বলে ‘প্রোফরেস্টেশন’। এই কৌশল বায়ুমণ্ডল থেকে গ্রিন হাউস গ্যাস অপসারণ এবং সংরক্ষণের জন্য বেশি কার্যকর। আর এতে ব্যয়ও কম।
জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত আন্তসরকারি প্যানেলের (আইপিসিসি) একটি প্রতিবেদনে সুন্দরবনের বর্তমান অবস্থার ওপর আলোকপাত করা হয়েছে। প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে, সুন্দরবনের ম্যানগ্রোভের বিশাল এলাকা গত দুই শতাব্দীতে ধানের খেত এবং সম্প্রতি চিংড়ির ঘেরে রূপান্তরিত হয়েছে। প্রতিবেদনে সতর্ক করা হয়েছে, ম্যানগ্রোভ বন ও জলাভূমি ধ্বংসের ফলে উপকূলীয় ভূমি ক্ষয় ত্বরান্বিত হতে পারে।
নেচার জার্নালে প্রকাশিত একটি সমীক্ষায় বলা হয়েছে, সংকুচিত হয়ে আসা বনের প্রাকৃতিক পুনর্জন্মের মাধ্যমে ক্যানোপি কভার (গাছের আচ্ছাদন) বৃদ্ধি করা, নতুন বৃক্ষরোপণের চেয়ে বেশি উপকারী হতে পারে। অন্তত এক শতাব্দীর মধ্যে জলবায়ু সুরক্ষায় উল্লেখযোগ্য সুফল এনে দিতে পারে।
এ কারণে প্রাকৃতিক বন পুনরুদ্ধারই এখন বিজ্ঞানী এবং নীতিনির্ধারকদের কাছে বেশি মনোযোগ পাচ্ছে। জার্মান সরকার এবং ইন্টারন্যাশনাল ইউনিয়ন ফর কনজারভেশন অব নেচার (আইইউসিএন) ২০৩০ সালের মধ্যে ৩৫ কোটি হেক্টর বন পুনরুদ্ধারের লক্ষ্য নির্ধারণ করেছে। এ ছাড়া গ্রীষ্মমণ্ডলীয় এবং উপক্রান্তীয় অঞ্চলের ৪৩টি দেশ বন পুনরুদ্ধারের অঙ্গীকার করেছে। উদাহরণস্বরূপ, ভিয়েতনাম ১ কোটি ৪৬ লাখ হেক্টর প্রাকৃতিক বন পুনরুদ্ধার করবে।
বাংলাদেশও এই প্রতিশ্রুতির বাইরে নেই। পরিসংখ্যান বলছে, দেশে গত ২০ বছরে ৪ দশমিক ১ শতাংশ প্রাথমিক বনাঞ্চল কমেছে। এর মধ্যে প্রায় সাড়ে ৩ শতাংশই কমেছে উত্তর-পূর্বাঞ্চলে। যদিও ব্যাপকভাবে বৃক্ষরোপণের মাধ্যমে ট্রি কভার (ক্যানোপি) বাড়ছে বলে দাবি করছে সরকার।
দুঃখের বিষয় হলো, বন রক্ষা এ দেশে সামাজিক আন্দোলনে রূপ নিতে পারেনি। প্রতিবছর গ্রীষ্মে যখন গরমে হাঁসফাঁস করতে থাকে মানুষ, তখনই বৃক্ষ নিধন নিয়ে বিলাপ, আর বেশি বেশি গাছ লাগানোর নছিহত চলতে থাকে।
এই ক্যাম্পেইন শহরে রীতিমতো ফ্যাশনে পরিণত হয়েছে। রাজধানীতে এক ইঞ্চি জায়গাও কেউ ছাড়তে চায় না। সেখানে বৃক্ষরোপণের আলাপ বিলাসিতা। যাঁদের বিলাসিতার সামর্থ্য আছে, তাঁরা তো বাড়ির সামনে গোছানো লন রাখেন। কিন্তু শহরের এই সুন্দর লনে তো প্রাণপ্রকৃতি রক্ষা পাবে না। অনেকেই এখন ছাদে বারান্দায় বাগান করছেন। কে জানে শৌখিন শহুরে মানুষের এই শখের ছাদবাগান থেকে উড়ে আসা এডিস মশার কামড়ে প্রতিবছর ডেঙ্গুতে হাজার হাজার মানুষের মৃত্যুতে হচ্ছে কি না!
গ্রীষ্মকালকে আবার সহনীয় করতে চাইলে আমাদের বরং উচিত, নির্বিচারে বন নিধনের পরও এখনো যতখানি টিকে আছে তার পুঙ্খানুপুঙ্খ পরিসংখ্যান ও মানচিত্র তৈরি করে সেগুলো সংরক্ষণ, পুনরুদ্ধার ও বর্ধনে জোর দেওয়া। বিভিন্ন এলাকায় এখনো পুরোনো ও বৃহৎ বৃক্ষ টিকে রয়েছে, সেগুলো সংরক্ষণে নজর দিতে হবে। বাড়াতে হবে জলাধার, উন্মুক্ত মাটি। সেই সঙ্গে পরিবেশবান্ধব ভবন নির্মাণে দায়বদ্ধতা। আরও দরকার ব্যক্তিগত পরিবহন কমিয়ে গণপরিবহন এবং হাঁটার উপযোগী ফুটপাত।
লেখক: আজকের পত্রিকার জ্যেষ্ঠ সহসম্পাদক
জাহাঙ্গীর আলম, ঢাকা

গাছ লাগানো ভালো। প্রতিবছর ৫ জুন বিশ্ব পরিবেশ দিবস উপলক্ষে নানা দেশেই আজকাল গাছ রোপণের রেকর্ড হচ্ছে। কিন্তু এভাবে গাছ রোপণ কি আসলেই জলবায়ু পরিবর্তন ঠেকানোর জন্য যথেষ্ট? এতে কি গ্রীষ্মকালের প্রচণ্ড গরম সহনীয় পর্যায়ে আনা সম্ভব।
প্রকৃতপক্ষে রেকর্ডের উদ্দেশ্যে গাছ রোপণের কিছু নেতিবাচক দিক রয়েছে। ধরেই নেওয়া হয় এসব চারার মাত্র ৪০ শতাংশ শেষ পর্যন্ত টিকে যায়।
কিন্তু আসলেই কত শতাংশ টিকে থাকে, সে খবর তো আর নেওয়া হয় না। কারণ, চারা রোপণের পরবর্তী কয়েক মাস যে নিবিড় যত্নের প্রয়োজন হয়—সেটি করার মতো জনবল, অর্থবল ও ধৈর্য কোনোটাই সাধারণত দেখা যায় না। চারায় পানি দেওয়া, ছোট অবস্থায় গরু-ছাগলের মতো তৃণভোজী প্রাণীর হাত থেকে রক্ষা করা ইত্যাদি যত্নআত্তি সাধারণত হয় না। তা ছাড়া এসব রেকর্ডের বৃক্ষ রোপণে দেখা যায়, চারাগুলোর মাঝখানে যথেষ্ট দূরত্ব রাখা হয় না। ফলে এগুলো সঠিকভাবে বেড়ে উঠতে পারে না।
এই সময়ের সবচেয়ে বড় পরিবেশগত দুটি চ্যালেঞ্জ হলো, জলবায়ু পরিবর্তন এবং জীববৈচিত্র্যের ক্রম অবনতি। আয়োজন করে বৃক্ষরোপণ, কিন্তু এই ইস্যুতে খুব কমই কাজে আসে।
‘জলবায়ু পরিবর্তন’ বলতে মূলত একটি সামগ্রিক পরিস্থিতিকে বোঝানো হয়। যখন বায়ুমণ্ডলে এমন সব গ্যাসের ঘনত্ব বেড়ে যায়, যা মাত্রাতিরিক্ত তাপ ধরে রাখে। ফলে পরিবেশের তাপমাত্রা এবং আবহাওয়ায় অস্বাভাবিক পরিবর্তন আসতে শুরু করে। এটি ঘটে মূলত জীবাশ্ম জ্বালানি পোড়ানোর মাধ্যমে গ্রিন হাউস গ্যাস উৎপাদনের কারণে। এই প্রক্রিয়া বন্ধ করার সহজ সমাধান হলো পরিবেশ থেকে বিদ্যমান কার্বন ডাই-অক্সাইড কমানো। যৌক্তিক কারণেই মোক্ষম উপায় হিসেবে বেশি বেশি গাছ লাগানোর কথা বলা হয়। কারণ, গাছের খাদ্য উৎপাদনের প্রধান কাঁচামাল কার্বন ডাই-অক্সাইড। এই কার্বন ডাই-অক্সাইড প্রক্রিয়াজাত করে গাছ কাণ্ডে-শাখায় পুষ্ট হয়।
কিন্তু গাছ রোপণের ধারণায় যে বিষয়টি উপেক্ষা করা হয়, সেটি হলো যখন কোনো প্রাকৃতিক কারণেই একটি গাছের মৃত্যু ঘটে, ধীরে ধীরে সেই কার্বন দেহটি আবার বায়ুমণ্ডলেই ফিরে আসে। অথচ সেটি কোনো প্রাকৃতিক বনে জঙ্গলে ঘটলে মৃত গাছের ওপর অসংখ্য ক্ষুদ্র উদ্ভিদ ও প্রাণের সমাহার ঘটে, এরা কার্বন দেহটি হাইড্রো-কার্বন গ্যাস রূপে বায়ুমণ্ডলে ফিরে আসতে দেয় না। আটকা পড়ে যায়। তার মানে, গাছ যে বায়ুমণ্ডল থেকে কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্রহণ করছে, সেটি স্থায়ীভাবে ধরে রাখা সম্ভব শুধু প্রাকৃতিক বনেই।
বৃক্ষরোপণের আরেকটি বড় নেতিবাচক দিক হলো, এই পদক্ষেপ জীববৈচিত্র্য রক্ষায় কোনো কাজে আসে না, এমনকি কোনো কোনো ক্ষেত্রে জীববৈচিত্র্যের জন্য হুমকিও হতে পারে। এ ধরনের বৃক্ষরোপণের ক্ষেত্রে সাধারণত দ্রুত বর্ধনশীল, পাতা দ্রুত পচনশীল এবং চিরহরিৎ—এমন বৈশিষ্ট্যের গাছ পছন্দ করা হয়। ফলে সাধারণত স্থানীয় প্রজাতি উপেক্ষিত হয়। আমাদের দেশে ইউক্যালিপটাস, শিশু, রেইনট্রি, মেহগনি ইত্যাদি গাছ এভাবে জনপ্রিয় হয়েছে। এসব গাছ পাখিদের খাবার ও বাসস্থানের জন্য উপযোগী নয়। এসব গাছ প্রচুর পরিমাণে ভূগর্ভস্থ পানি শোষণ করে। জীববৈচিত্র্যের জন্যও কোনো উপকারে আসে না। বাতাসে প্রচুর রেণু ছড়িয়ে পড়ে। ফলে আশপাশে অ্যালার্জির সমস্যা বাড়ে।
এর মধ্যে কিছু গাছ আছে, অত্যন্ত দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে। এতে স্থানীয় বৃক্ষ প্রজাতি হুমকির মুখে পড়ে। এ কারণে আজকাল অবশ্য এসব বিদেশি গাছ রোপণ নিরুৎসাহিত করা হয়।
মজার বিষয় হলো, গ্রীষ্মকালে এসব গাছ তাপমাত্রা না কমিয়ে উল্টো বাড়িয়ে দিতে পারে। আবহাওয়া বিজ্ঞানে ‘ওয়েট বাল্ব টেম্পারেচার’ বলে একটি কথা আছে। বাতাসের আর্দ্রতা বেশি থাকলে, অর্থাৎ বাতাস যদি সম্পৃক্ত হয়; তাহলে বাষ্পীভবনের মাধ্যমে ঠান্ডা হওয়ার সুযোগ কমে যায়। এই কারণেই কিন্তু আর্দ্রতা বেশি থাকলে অস্বস্তি বাড়ে। শরীর ঘামলেও তাপমাত্রা কমে না। এতে হিট স্ট্রোকের ঝুঁকিও বাড়ে।
ওই সব বিদেশি গাছের প্রস্বেদনের হার স্থানীয় জাতের অনেক গাছের চেয়ে ঢের বেশি। ফলে এসব গাছ বেশি থাকলে সেই এলাকায় ওয়েট বাল্ব টেম্পারেচার পরিস্থিতি দেখা দিতে পারে।
সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, হাতে গোনা কয়েক প্রজাতির গাছ রোপণের মাধ্যমে বন তৈরি করা কখনো সম্ভব নয়। একটি বনের যে জটিল বাস্তুতন্ত্র থাকে, যার মাধ্যমে জীববৈচিত্র্য রক্ষিত হয়—সেটি এই তথাকথিত কৃত্রিম বনায়নের মাধ্যমে অসম্ভব।
একাধিক গবেষণায় প্রমাণিত, গাছ লাগানো প্রাকৃতিক বনের বিকল্প হতে পারে। ২০১৯ সালের দিকে ‘ফ্রন্টিয়ার ইন ফরেস্ট অ্যান্ড গ্লোবাল চেঞ্জ’ সাময়িকীতে প্রকাশিত একটি গবেষণায় দেখানো হয়, বিদ্যমান বনগুলোকে সেগুলোর পরিবেশগত সম্ভাবনা অক্ষত রেখে বাড়ানোর উদ্যোগ নেওয়াই বেশি কার্যকর উপায়। এটিকে বলে ‘প্রোফরেস্টেশন’। এই কৌশল বায়ুমণ্ডল থেকে গ্রিন হাউস গ্যাস অপসারণ এবং সংরক্ষণের জন্য বেশি কার্যকর। আর এতে ব্যয়ও কম।
জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত আন্তসরকারি প্যানেলের (আইপিসিসি) একটি প্রতিবেদনে সুন্দরবনের বর্তমান অবস্থার ওপর আলোকপাত করা হয়েছে। প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে, সুন্দরবনের ম্যানগ্রোভের বিশাল এলাকা গত দুই শতাব্দীতে ধানের খেত এবং সম্প্রতি চিংড়ির ঘেরে রূপান্তরিত হয়েছে। প্রতিবেদনে সতর্ক করা হয়েছে, ম্যানগ্রোভ বন ও জলাভূমি ধ্বংসের ফলে উপকূলীয় ভূমি ক্ষয় ত্বরান্বিত হতে পারে।
নেচার জার্নালে প্রকাশিত একটি সমীক্ষায় বলা হয়েছে, সংকুচিত হয়ে আসা বনের প্রাকৃতিক পুনর্জন্মের মাধ্যমে ক্যানোপি কভার (গাছের আচ্ছাদন) বৃদ্ধি করা, নতুন বৃক্ষরোপণের চেয়ে বেশি উপকারী হতে পারে। অন্তত এক শতাব্দীর মধ্যে জলবায়ু সুরক্ষায় উল্লেখযোগ্য সুফল এনে দিতে পারে।
এ কারণে প্রাকৃতিক বন পুনরুদ্ধারই এখন বিজ্ঞানী এবং নীতিনির্ধারকদের কাছে বেশি মনোযোগ পাচ্ছে। জার্মান সরকার এবং ইন্টারন্যাশনাল ইউনিয়ন ফর কনজারভেশন অব নেচার (আইইউসিএন) ২০৩০ সালের মধ্যে ৩৫ কোটি হেক্টর বন পুনরুদ্ধারের লক্ষ্য নির্ধারণ করেছে। এ ছাড়া গ্রীষ্মমণ্ডলীয় এবং উপক্রান্তীয় অঞ্চলের ৪৩টি দেশ বন পুনরুদ্ধারের অঙ্গীকার করেছে। উদাহরণস্বরূপ, ভিয়েতনাম ১ কোটি ৪৬ লাখ হেক্টর প্রাকৃতিক বন পুনরুদ্ধার করবে।
বাংলাদেশও এই প্রতিশ্রুতির বাইরে নেই। পরিসংখ্যান বলছে, দেশে গত ২০ বছরে ৪ দশমিক ১ শতাংশ প্রাথমিক বনাঞ্চল কমেছে। এর মধ্যে প্রায় সাড়ে ৩ শতাংশই কমেছে উত্তর-পূর্বাঞ্চলে। যদিও ব্যাপকভাবে বৃক্ষরোপণের মাধ্যমে ট্রি কভার (ক্যানোপি) বাড়ছে বলে দাবি করছে সরকার।
দুঃখের বিষয় হলো, বন রক্ষা এ দেশে সামাজিক আন্দোলনে রূপ নিতে পারেনি। প্রতিবছর গ্রীষ্মে যখন গরমে হাঁসফাঁস করতে থাকে মানুষ, তখনই বৃক্ষ নিধন নিয়ে বিলাপ, আর বেশি বেশি গাছ লাগানোর নছিহত চলতে থাকে।
এই ক্যাম্পেইন শহরে রীতিমতো ফ্যাশনে পরিণত হয়েছে। রাজধানীতে এক ইঞ্চি জায়গাও কেউ ছাড়তে চায় না। সেখানে বৃক্ষরোপণের আলাপ বিলাসিতা। যাঁদের বিলাসিতার সামর্থ্য আছে, তাঁরা তো বাড়ির সামনে গোছানো লন রাখেন। কিন্তু শহরের এই সুন্দর লনে তো প্রাণপ্রকৃতি রক্ষা পাবে না। অনেকেই এখন ছাদে বারান্দায় বাগান করছেন। কে জানে শৌখিন শহুরে মানুষের এই শখের ছাদবাগান থেকে উড়ে আসা এডিস মশার কামড়ে প্রতিবছর ডেঙ্গুতে হাজার হাজার মানুষের মৃত্যুতে হচ্ছে কি না!
গ্রীষ্মকালকে আবার সহনীয় করতে চাইলে আমাদের বরং উচিত, নির্বিচারে বন নিধনের পরও এখনো যতখানি টিকে আছে তার পুঙ্খানুপুঙ্খ পরিসংখ্যান ও মানচিত্র তৈরি করে সেগুলো সংরক্ষণ, পুনরুদ্ধার ও বর্ধনে জোর দেওয়া। বিভিন্ন এলাকায় এখনো পুরোনো ও বৃহৎ বৃক্ষ টিকে রয়েছে, সেগুলো সংরক্ষণে নজর দিতে হবে। বাড়াতে হবে জলাধার, উন্মুক্ত মাটি। সেই সঙ্গে পরিবেশবান্ধব ভবন নির্মাণে দায়বদ্ধতা। আরও দরকার ব্যক্তিগত পরিবহন কমিয়ে গণপরিবহন এবং হাঁটার উপযোগী ফুটপাত।
লেখক: আজকের পত্রিকার জ্যেষ্ঠ সহসম্পাদক

গাছ লাগানো ভালো। প্রতিবছর ৫ জুন বিশ্ব পরিবেশ দিবস উপলক্ষে নানা দেশেই আজকাল গাছ রোপণের রেকর্ড হচ্ছে। কিন্তু এভাবে গাছ রোপণ কি আসলেই জলবায়ু পরিবর্তন ঠেকানোর জন্য যথেষ্ট? এতে কি গ্রীষ্মকালের প্রচণ্ড গরম সহনীয় পর্যায়ে আনা সম্ভব।
প্রকৃতপক্ষে রেকর্ডের উদ্দেশ্যে গাছ রোপণের কিছু নেতিবাচক দিক রয়েছে। ধরেই নেওয়া হয় এসব চারার মাত্র ৪০ শতাংশ শেষ পর্যন্ত টিকে যায়।
কিন্তু আসলেই কত শতাংশ টিকে থাকে, সে খবর তো আর নেওয়া হয় না। কারণ, চারা রোপণের পরবর্তী কয়েক মাস যে নিবিড় যত্নের প্রয়োজন হয়—সেটি করার মতো জনবল, অর্থবল ও ধৈর্য কোনোটাই সাধারণত দেখা যায় না। চারায় পানি দেওয়া, ছোট অবস্থায় গরু-ছাগলের মতো তৃণভোজী প্রাণীর হাত থেকে রক্ষা করা ইত্যাদি যত্নআত্তি সাধারণত হয় না। তা ছাড়া এসব রেকর্ডের বৃক্ষ রোপণে দেখা যায়, চারাগুলোর মাঝখানে যথেষ্ট দূরত্ব রাখা হয় না। ফলে এগুলো সঠিকভাবে বেড়ে উঠতে পারে না।
এই সময়ের সবচেয়ে বড় পরিবেশগত দুটি চ্যালেঞ্জ হলো, জলবায়ু পরিবর্তন এবং জীববৈচিত্র্যের ক্রম অবনতি। আয়োজন করে বৃক্ষরোপণ, কিন্তু এই ইস্যুতে খুব কমই কাজে আসে।
‘জলবায়ু পরিবর্তন’ বলতে মূলত একটি সামগ্রিক পরিস্থিতিকে বোঝানো হয়। যখন বায়ুমণ্ডলে এমন সব গ্যাসের ঘনত্ব বেড়ে যায়, যা মাত্রাতিরিক্ত তাপ ধরে রাখে। ফলে পরিবেশের তাপমাত্রা এবং আবহাওয়ায় অস্বাভাবিক পরিবর্তন আসতে শুরু করে। এটি ঘটে মূলত জীবাশ্ম জ্বালানি পোড়ানোর মাধ্যমে গ্রিন হাউস গ্যাস উৎপাদনের কারণে। এই প্রক্রিয়া বন্ধ করার সহজ সমাধান হলো পরিবেশ থেকে বিদ্যমান কার্বন ডাই-অক্সাইড কমানো। যৌক্তিক কারণেই মোক্ষম উপায় হিসেবে বেশি বেশি গাছ লাগানোর কথা বলা হয়। কারণ, গাছের খাদ্য উৎপাদনের প্রধান কাঁচামাল কার্বন ডাই-অক্সাইড। এই কার্বন ডাই-অক্সাইড প্রক্রিয়াজাত করে গাছ কাণ্ডে-শাখায় পুষ্ট হয়।
কিন্তু গাছ রোপণের ধারণায় যে বিষয়টি উপেক্ষা করা হয়, সেটি হলো যখন কোনো প্রাকৃতিক কারণেই একটি গাছের মৃত্যু ঘটে, ধীরে ধীরে সেই কার্বন দেহটি আবার বায়ুমণ্ডলেই ফিরে আসে। অথচ সেটি কোনো প্রাকৃতিক বনে জঙ্গলে ঘটলে মৃত গাছের ওপর অসংখ্য ক্ষুদ্র উদ্ভিদ ও প্রাণের সমাহার ঘটে, এরা কার্বন দেহটি হাইড্রো-কার্বন গ্যাস রূপে বায়ুমণ্ডলে ফিরে আসতে দেয় না। আটকা পড়ে যায়। তার মানে, গাছ যে বায়ুমণ্ডল থেকে কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্রহণ করছে, সেটি স্থায়ীভাবে ধরে রাখা সম্ভব শুধু প্রাকৃতিক বনেই।
বৃক্ষরোপণের আরেকটি বড় নেতিবাচক দিক হলো, এই পদক্ষেপ জীববৈচিত্র্য রক্ষায় কোনো কাজে আসে না, এমনকি কোনো কোনো ক্ষেত্রে জীববৈচিত্র্যের জন্য হুমকিও হতে পারে। এ ধরনের বৃক্ষরোপণের ক্ষেত্রে সাধারণত দ্রুত বর্ধনশীল, পাতা দ্রুত পচনশীল এবং চিরহরিৎ—এমন বৈশিষ্ট্যের গাছ পছন্দ করা হয়। ফলে সাধারণত স্থানীয় প্রজাতি উপেক্ষিত হয়। আমাদের দেশে ইউক্যালিপটাস, শিশু, রেইনট্রি, মেহগনি ইত্যাদি গাছ এভাবে জনপ্রিয় হয়েছে। এসব গাছ পাখিদের খাবার ও বাসস্থানের জন্য উপযোগী নয়। এসব গাছ প্রচুর পরিমাণে ভূগর্ভস্থ পানি শোষণ করে। জীববৈচিত্র্যের জন্যও কোনো উপকারে আসে না। বাতাসে প্রচুর রেণু ছড়িয়ে পড়ে। ফলে আশপাশে অ্যালার্জির সমস্যা বাড়ে।
এর মধ্যে কিছু গাছ আছে, অত্যন্ত দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে। এতে স্থানীয় বৃক্ষ প্রজাতি হুমকির মুখে পড়ে। এ কারণে আজকাল অবশ্য এসব বিদেশি গাছ রোপণ নিরুৎসাহিত করা হয়।
মজার বিষয় হলো, গ্রীষ্মকালে এসব গাছ তাপমাত্রা না কমিয়ে উল্টো বাড়িয়ে দিতে পারে। আবহাওয়া বিজ্ঞানে ‘ওয়েট বাল্ব টেম্পারেচার’ বলে একটি কথা আছে। বাতাসের আর্দ্রতা বেশি থাকলে, অর্থাৎ বাতাস যদি সম্পৃক্ত হয়; তাহলে বাষ্পীভবনের মাধ্যমে ঠান্ডা হওয়ার সুযোগ কমে যায়। এই কারণেই কিন্তু আর্দ্রতা বেশি থাকলে অস্বস্তি বাড়ে। শরীর ঘামলেও তাপমাত্রা কমে না। এতে হিট স্ট্রোকের ঝুঁকিও বাড়ে।
ওই সব বিদেশি গাছের প্রস্বেদনের হার স্থানীয় জাতের অনেক গাছের চেয়ে ঢের বেশি। ফলে এসব গাছ বেশি থাকলে সেই এলাকায় ওয়েট বাল্ব টেম্পারেচার পরিস্থিতি দেখা দিতে পারে।
সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, হাতে গোনা কয়েক প্রজাতির গাছ রোপণের মাধ্যমে বন তৈরি করা কখনো সম্ভব নয়। একটি বনের যে জটিল বাস্তুতন্ত্র থাকে, যার মাধ্যমে জীববৈচিত্র্য রক্ষিত হয়—সেটি এই তথাকথিত কৃত্রিম বনায়নের মাধ্যমে অসম্ভব।
একাধিক গবেষণায় প্রমাণিত, গাছ লাগানো প্রাকৃতিক বনের বিকল্প হতে পারে। ২০১৯ সালের দিকে ‘ফ্রন্টিয়ার ইন ফরেস্ট অ্যান্ড গ্লোবাল চেঞ্জ’ সাময়িকীতে প্রকাশিত একটি গবেষণায় দেখানো হয়, বিদ্যমান বনগুলোকে সেগুলোর পরিবেশগত সম্ভাবনা অক্ষত রেখে বাড়ানোর উদ্যোগ নেওয়াই বেশি কার্যকর উপায়। এটিকে বলে ‘প্রোফরেস্টেশন’। এই কৌশল বায়ুমণ্ডল থেকে গ্রিন হাউস গ্যাস অপসারণ এবং সংরক্ষণের জন্য বেশি কার্যকর। আর এতে ব্যয়ও কম।
জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত আন্তসরকারি প্যানেলের (আইপিসিসি) একটি প্রতিবেদনে সুন্দরবনের বর্তমান অবস্থার ওপর আলোকপাত করা হয়েছে। প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে, সুন্দরবনের ম্যানগ্রোভের বিশাল এলাকা গত দুই শতাব্দীতে ধানের খেত এবং সম্প্রতি চিংড়ির ঘেরে রূপান্তরিত হয়েছে। প্রতিবেদনে সতর্ক করা হয়েছে, ম্যানগ্রোভ বন ও জলাভূমি ধ্বংসের ফলে উপকূলীয় ভূমি ক্ষয় ত্বরান্বিত হতে পারে।
নেচার জার্নালে প্রকাশিত একটি সমীক্ষায় বলা হয়েছে, সংকুচিত হয়ে আসা বনের প্রাকৃতিক পুনর্জন্মের মাধ্যমে ক্যানোপি কভার (গাছের আচ্ছাদন) বৃদ্ধি করা, নতুন বৃক্ষরোপণের চেয়ে বেশি উপকারী হতে পারে। অন্তত এক শতাব্দীর মধ্যে জলবায়ু সুরক্ষায় উল্লেখযোগ্য সুফল এনে দিতে পারে।
এ কারণে প্রাকৃতিক বন পুনরুদ্ধারই এখন বিজ্ঞানী এবং নীতিনির্ধারকদের কাছে বেশি মনোযোগ পাচ্ছে। জার্মান সরকার এবং ইন্টারন্যাশনাল ইউনিয়ন ফর কনজারভেশন অব নেচার (আইইউসিএন) ২০৩০ সালের মধ্যে ৩৫ কোটি হেক্টর বন পুনরুদ্ধারের লক্ষ্য নির্ধারণ করেছে। এ ছাড়া গ্রীষ্মমণ্ডলীয় এবং উপক্রান্তীয় অঞ্চলের ৪৩টি দেশ বন পুনরুদ্ধারের অঙ্গীকার করেছে। উদাহরণস্বরূপ, ভিয়েতনাম ১ কোটি ৪৬ লাখ হেক্টর প্রাকৃতিক বন পুনরুদ্ধার করবে।
বাংলাদেশও এই প্রতিশ্রুতির বাইরে নেই। পরিসংখ্যান বলছে, দেশে গত ২০ বছরে ৪ দশমিক ১ শতাংশ প্রাথমিক বনাঞ্চল কমেছে। এর মধ্যে প্রায় সাড়ে ৩ শতাংশই কমেছে উত্তর-পূর্বাঞ্চলে। যদিও ব্যাপকভাবে বৃক্ষরোপণের মাধ্যমে ট্রি কভার (ক্যানোপি) বাড়ছে বলে দাবি করছে সরকার।
দুঃখের বিষয় হলো, বন রক্ষা এ দেশে সামাজিক আন্দোলনে রূপ নিতে পারেনি। প্রতিবছর গ্রীষ্মে যখন গরমে হাঁসফাঁস করতে থাকে মানুষ, তখনই বৃক্ষ নিধন নিয়ে বিলাপ, আর বেশি বেশি গাছ লাগানোর নছিহত চলতে থাকে।
এই ক্যাম্পেইন শহরে রীতিমতো ফ্যাশনে পরিণত হয়েছে। রাজধানীতে এক ইঞ্চি জায়গাও কেউ ছাড়তে চায় না। সেখানে বৃক্ষরোপণের আলাপ বিলাসিতা। যাঁদের বিলাসিতার সামর্থ্য আছে, তাঁরা তো বাড়ির সামনে গোছানো লন রাখেন। কিন্তু শহরের এই সুন্দর লনে তো প্রাণপ্রকৃতি রক্ষা পাবে না। অনেকেই এখন ছাদে বারান্দায় বাগান করছেন। কে জানে শৌখিন শহুরে মানুষের এই শখের ছাদবাগান থেকে উড়ে আসা এডিস মশার কামড়ে প্রতিবছর ডেঙ্গুতে হাজার হাজার মানুষের মৃত্যুতে হচ্ছে কি না!
গ্রীষ্মকালকে আবার সহনীয় করতে চাইলে আমাদের বরং উচিত, নির্বিচারে বন নিধনের পরও এখনো যতখানি টিকে আছে তার পুঙ্খানুপুঙ্খ পরিসংখ্যান ও মানচিত্র তৈরি করে সেগুলো সংরক্ষণ, পুনরুদ্ধার ও বর্ধনে জোর দেওয়া। বিভিন্ন এলাকায় এখনো পুরোনো ও বৃহৎ বৃক্ষ টিকে রয়েছে, সেগুলো সংরক্ষণে নজর দিতে হবে। বাড়াতে হবে জলাধার, উন্মুক্ত মাটি। সেই সঙ্গে পরিবেশবান্ধব ভবন নির্মাণে দায়বদ্ধতা। আরও দরকার ব্যক্তিগত পরিবহন কমিয়ে গণপরিবহন এবং হাঁটার উপযোগী ফুটপাত।
লেখক: আজকের পত্রিকার জ্যেষ্ঠ সহসম্পাদক
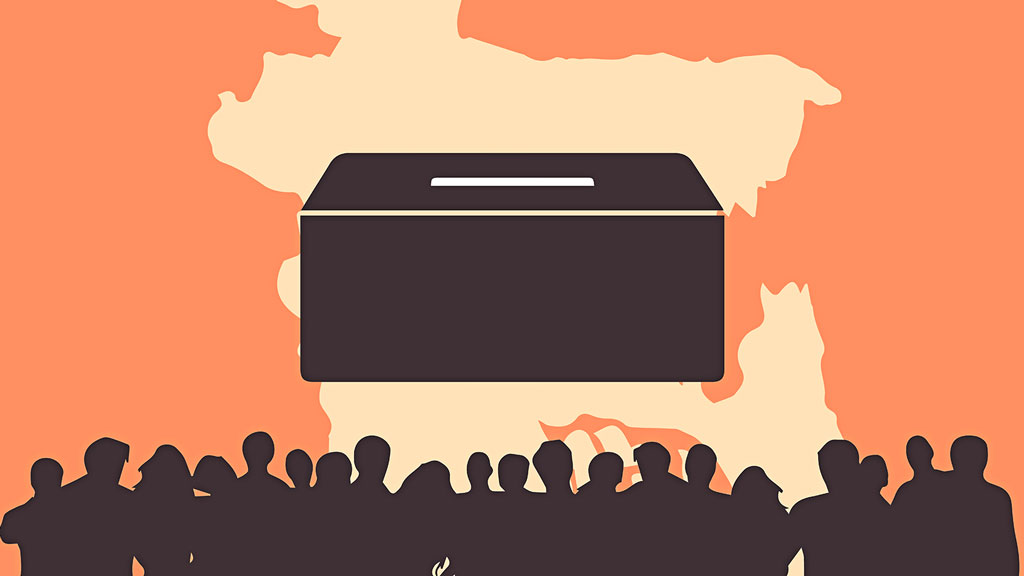
বাংলাদেশ আবারও একটি সংবেদনশীল সময় অতিক্রম করছে। সামনে জাতীয় নির্বাচন—যা শুধু ক্ষমতা পরিবর্তনের আনুষ্ঠানিক প্রক্রিয়া নয়; বরং রাষ্ট্রের গণতান্ত্রিক যাত্রার একটি গুরুত্বপূর্ণ বাঁক। এই নির্বাচন ঘিরে জনগণের প্রত্যাশা যেমন আছে, তেমনি রয়েছে গভীর উদ্বেগও।
১১ ঘণ্টা আগে
শুরুটা ছিল বেশ আশাজাগানিয়া। বিধি অনুযায়ী আমাদের দেশে মন্ত্রিসভার সদস্যদের কী বেতন বা সম্মানী এবং ভাতা ও সুবিধাদি এক্ষণে জানা নেই। যুগের সঙ্গে তাল মিলিয়েই নিশ্চয় তা নির্ধারণ করা হয়েছে। মন্ত্রী ছাড়া যাঁরা সংসদ সদস্য, তাঁদের বেলায়ও একই কথা; মোটা অঙ্কের বেতন-ভাতা এবং বলতে গেলে অবাধ সুযোগ-সুবিধা আছে বলেই
১১ ঘণ্টা আগে
বিজয়ের মাস চলছে। বাঙালি জাতির হাজার বছরের শৌর্যবীর্য ও বীরত্বের এক অবিস্মরণীয় গৌরবময় দিনটি ছিল গতকাল। ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর সঙ্গে দীর্ঘ ৯ মাসের রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ শেষে বাঙালি জাতির শ্রেষ্ঠতম অর্জন ‘বিজয়’। এদিন বাঙালির আত্মপরিচয় লাভের দিন।
১১ ঘণ্টা আগে
দেশের মানুষ যখন উৎসবমুখর পরিবেশে ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ভোট দিতে উন্মুখ হয়ে আছে, তখন কিছু অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনায় নির্বাচনে বিশৃঙ্খল পরিবেশ তৈরি হওয়ার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। এ নিয়ে আজকের পত্রিকায় ১৫ ডিসেম্বর একটা উদ্বেগজনক ‘ভোটের আগে আতঙ্ক জনমনে’ শিরোনামে সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে।
১১ ঘণ্টা আগেএই কঠিন সময়েও বিজয় দিবস আমাদের আশার কথা শোনায়। ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়, বাংলাদেশ সংকট থেকে ঘুরে দাঁড়াতে জানে। কিন্তু সেই সক্ষমতা কাজে লাগাতে হলে আমাদের সচেতন সিদ্ধান্ত নিতে হবে— আমরা কি সহিংসতার পুরোনো বৃত্তেই ঘুরপাক খাব, নাকি দায়িত্বশীল রাজনীতি ও সহনশীলতার পথে এগিয়ে যাব। এ সিদ্ধান্ত নেওয়ার সময় এখনই।
কামরুল হাসান
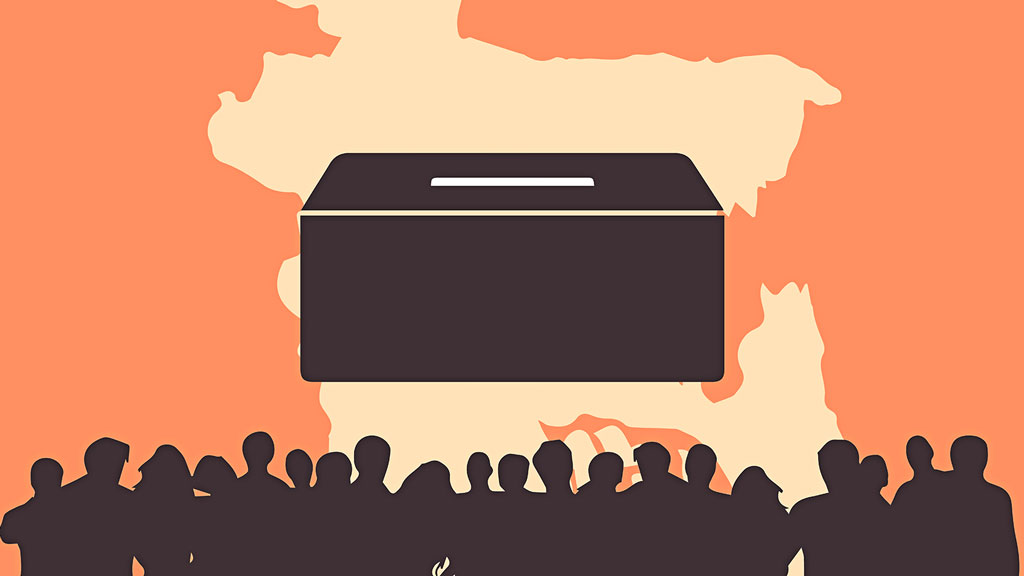
বাংলাদেশ আবারও একটি সংবেদনশীল সময় অতিক্রম করছে। সামনে জাতীয় নির্বাচন—যা শুধু ক্ষমতা পরিবর্তনের আনুষ্ঠানিক প্রক্রিয়া নয়; বরং রাষ্ট্রের গণতান্ত্রিক যাত্রার একটি গুরুত্বপূর্ণ বাঁক। এই নির্বাচন ঘিরে জনগণের প্রত্যাশা যেমন আছে, তেমনি রয়েছে গভীর উদ্বেগও। রাজনৈতিক অঙ্গন উত্তপ্ত, সামাজিক পরিসরে উৎকণ্ঠা, আর সাধারণ মানুষের মনে ভবিষ্যৎ নিয়ে অনিশ্চয়তার দোলাচল স্পষ্টভাবে দৃশ্যমান।
এই শঙ্কা ও উদ্বেগজনক পরিস্থিতির মধ্যেই নির্বাচনের সম্ভাব্য এক প্রার্থীর ওপর নৃশংস হামলার ঘটনা দেশকে নতুন করে নাড়া দিয়েছে। এমন ঘটনা শুধু একজন ব্যক্তির ওপর আঘাত নয়; এটি দেশের রাজনৈতিক সংস্কৃতি, নির্বাচনকালীন নিরাপত্তাব্যবস্থা এবং রাষ্ট্রের সামগ্রিক সক্ষমতার ওপর একটি গুরুতর প্রশ্নচিহ্ন এঁকে দেয়। একটি গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় নির্বাচনে অংশ নেওয়া প্রার্থীর নিরাপত্তা নিশ্চিত করা না গেলে সাধারণ ভোটারের নিরাপত্তা এবং আস্থার জায়গাটি কতটা সুদৃঢ় অবস্থায় দাঁড়িয়ে আছে, সেই প্রশ্ন এড়ানোর সুযোগ নেই।
এমনিতেই বেশ কিছুদিন ধরে যানবাহনে অগ্নিসংযোগ ও ককটেল হামলার মতো ঘটনা ঘটছে। এসব ঘটনা স্পষ্ট ইঙ্গিত দিচ্ছে, একটি পরিকল্পিত আতঙ্ক সৃষ্টির চেষ্টা চলছে। সেই ধারাবাহিকতায় সম্ভাব্য প্রার্থী শরিফ ওসমান হাদির ওপর হামলার ঘটনা নির্বাচন ঘিরে সামগ্রিক নিরাপত্তাব্যবস্থার দুর্বলতাকে নতুন করে সামনে এনেছে। এটি কোনো বিচ্ছিন্ন অপরাধ নয়; বরং নির্বাচনপ্রক্রিয়াকে বাধাগ্রস্ত করার একটি সুপরিকল্পিত অপচেষ্টা বলেই প্রতীয়মান হচ্ছে।
রাজনৈতিক অঙ্গনের অনেকে মনে করছেন, ওসমান হাদির ওপর হামলার লক্ষ্য ছিল শুধু একজন ব্যক্তিকে ভয় দেখানো নয়; বরং নির্বাচনকেই অনিশ্চয়তায় ফেলা। আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারাও স্বীকার করছেন, দীর্ঘদিন ধরে একটি চক্র নির্বাচন বানচালের হুমকি দিয়ে আসছে। সহিংসতার এই ধারাবাহিকতা সেই হুমকিকে বাস্তবে রূপ দেওয়ার ইঙ্গিত বহন করে।
তবে অন্তর্বর্তী সরকার ঘটনাটিকে নির্বাচনবিরোধী ষড়যন্ত্র হিসেবে দেখছে। প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ইউনূসের বক্তব্যে বিষয়টি স্পষ্ট করা হয়েছে যে নির্বাচন বাধাগ্রস্ত করার উদ্দেশ্যে কোনো ধরনের সহিংসতা বরদাশত করা হবে না। জনগণের নিরাপত্তা দেওয়া এবং প্রার্থীদের অবাধ চলাচল নিশ্চিত করা রাষ্ট্রের মৌলিক দায়িত্ব—এই অবস্থান জোরালোভাবে পুনর্ব্যক্ত করা হয়েছে।
কিন্তু বক্তব্যের দৃঢ়তা বাস্তব পদক্ষেপে প্রতিফলিত না হলে জনমনে আস্থা ফিরবে না। নির্বাচন কমিশন ও অন্তর্বর্তী সরকারের এখন প্রধান কর্তব্য হলো, কঠোর নিরাপত্তাব্যবস্থা গ্রহণ, দলমত-নির্বিশেষে দোষীদের দ্রুত শনাক্ত ও বিচারের আওতায় আনা এবং নির্বাচনী পরিবেশের ওপর আস্থা নিশ্চিত করা। গণতন্ত্রের পথ কখনোই ভয় আর সহিংসতার ওপর দাঁড়াতে পারে না।
এ মুহূর্তে সরকারের কঠোর ও নিরপেক্ষ অবস্থানই পারে নির্বাচনকে সুরক্ষিত রাখতে এবং জনগণের আস্থা পুনঃপ্রতিষ্ঠা করতে।
আজকের এই সময়ে দাঁড়িয়ে সবাই স্বীকার করবেন, বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক ইতিহাসে সংকট নতুন কিছু নয়। রাজনৈতিক প্রতিহিংসা, সহিংস আন্দোলন, অবিশ্বাসের চর্চা—এসব উপাদান বহুবার নির্বাচনপ্রক্রিয়াকে বিতর্কিত করেছে। কোনো কোনো সময় নির্বাচন হয়ে উঠেছে জনগণের উৎসব, আবার কোনো কোনো সময় তা রূপ নিয়েছে আতঙ্ক ও শঙ্কার আভাসে। ফলে প্রতিবার ভোটের আগে মানুষের মনে একটি স্বাভাবিক সংশয় সৃষ্টি হয়, সেটি হলো—এই নির্বাচন শান্তিপূর্ণ হবে তো? নাকি আবারও সহিংসতার ছায়া পড়বে?
গণতন্ত্রের মৌলিক বৈশিষ্ট্যই হলো মতভিন্নতা। প্রতিযোগিতা থাকবে, মতের সংঘাত হবে—এটিই স্বাভাবিক। কিন্তু সেই প্রতিযোগিতা যখন অস্ত্র, হামলা কিংবা ভয়ভীতির হয়, তখন তা গণতন্ত্রকে শক্তিশালী করে না; বরং তাকে দুর্বল করে দেয়। রাজনীতির শক্তি হওয়া উচিত যুক্তি, কর্মসূচি ও জনসমর্থন। সহিংসতা কখনোই রাজনৈতিক সমাধান নয়। ইতিহাস বারবার প্রমাণ করেছে, সহিংসতার পথ বেছে নিলে শেষ পর্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত হয় রাষ্ট্র, সমাজ এবং সাধারণ মানুষ।
এই বাস্তবতায় নির্বাচন কমিশন ও আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। নির্বাচন কমিশনের ওপর জনগণের আস্থা অনেকাংশে নির্ভর করে তাদের নিরপেক্ষতা এবং দৃঢ়তার ওপর। একইভাবে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর পেশাদার ও পক্ষপাতহীন ভূমিকা ছাড়া নির্বাচনকালীন সহিংসতা প্রতিরোধ করা সম্ভব নয়। কোনো ধরনের শিথিলতা কিংবা পক্ষপাত পরিস্থিতিকে আরও জটিল করে তুলতে পারে। আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী এখনো যে ধরনের নাজুক অবস্থায় রয়েছে, তাতে তাদের পুরো মনোবল ফিরিয়ে আনতে না পারলে রাষ্ট্র হয়তো বিপদে পড়ে যাবে।
দায়িত্ব অবশ্য শুধু রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলোর ওপরই বর্তায় না; সরকার ও বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলোর ভূমিকাও সমান গুরুত্বপূর্ণ। ক্ষমতায় থাকা কিংবা ক্ষমতার বাইরে থাকা—উভয় অবস্থানেই দায়িত্বশীল আচরণ গণতন্ত্রের পূর্বশর্ত। উসকানিমূলক বক্তব্য, গুজব ছড়ানো কিংবা সহিংস কর্মসূচির মাধ্যমে রাজনৈতিক ফায়দার চেষ্টা শেষ পর্যন্ত জাতির জন্য ক্ষতিকর হয়। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে যা খুশি তা লেখা যায় বলে গুজব ছড়ানো সহজ। অনেকে কোনো প্রমাণ ছাড়াই এমন সব ভুয়া তথ্য ছড়িয়ে থাকেন, যা আদতে পরস্পরের প্রতি সন্দেহ-অবিশ্বাস এমনকি সংঘাতের জন্ম দেয়।
এমনই অস্থির এক সময়ে জাতীয় জীবনে ফিরে এল মহান বিজয় দিবস—১৬ ডিসেম্বর। স্বাধীনতার এদিনটি আমাদের মনে করিয়ে দিল, বাংলাদেশ জন্ম নিয়েছিল রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম এবং অপরিসীম আত্মত্যাগের মধ্য দিয়ে। ১৯৭১ সালে একটি জাতি প্রমাণ করেছিল, তারা অন্যায়ের কাছে মাথানত করতে জানে না। যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশ থেকে আজকের বাংলাদেশ—এই দীর্ঘ পথচলায় রয়েছে রক্ত, বেদনা ও গৌরবের ইতিহাস।
বিজয় দিবস তাই শুধু উৎসবের দিন নয়; এটি আত্মজিজ্ঞাসার সময়ও। স্বাধীনতার এত বছর পর এসে আমাদের নিজেদের প্রশ্ন করা জরুরি—আমরা কি সেই মুক্তিযুদ্ধের চেতনার প্রতি যথাযথ সম্মান দেখাতে পেরেছি? একটি সহনশীল, নিরাপদ ও ন্যায়ভিত্তিক রাষ্ট্র কি গড়ে তুলতে পেরেছি? রাজনৈতিক মতভিন্নতা কি আমরা শান্তিপূর্ণভাবে মেনে নিতে শিখেছি?
দুঃখজনক হলেও সত্য, এসব প্রশ্নের উত্তর এখনো পুরোপুরি ইতিবাচক নয়। রাজনৈতিক অসহিষ্ণুতা, ক্ষমতার অপব্যবহার এবং দায়িত্বহীন আচরণ আমাদের গণতান্ত্রিক অগ্রযাত্রা বারবার বাধাগ্রস্ত করেছে। নির্বাচনের সময় এসব প্রবণতা আরও তীব্র হয়ে ওঠে। অথচ নির্বাচন হওয়া উচিত জনগণের ক্ষমতা প্রয়োগের সবচেয়ে বড় উৎসব; ভয়ের উপলক্ষ নয়।
এই প্রেক্ষাপটে সবচেয়ে জরুরি বিষয় হলো সংযম। রাজনৈতিক দলগুলোর সংযম, প্রশাসনের সংযম এবং রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলোর দায়িত্বশীলতা। একটি অবাধ, সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণ নির্বাচন কোনো একক পক্ষে নিশ্চিত করা সম্ভব নয়। সরকার, বিরোধী দল, নির্বাচন কমিশন, আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী, গণমাধ্যম ও নাগরিক সমাজ—সবার সম্মিলিত উদ্যোগ ছাড়া এই লক্ষ্য অর্জন করা যাবে না। পাশাপাশি এটিও আমাদের ভাবতে হবে, অন্তর্ভুক্তিমূলক নির্বাচন বলতে আমরা কী বুঝব। কোনো রাজনৈতিক দল কিংবা তার সমর্থকদের নির্বাচনের বাইরে রাখা হলে তা কি অন্তর্ভুক্তিমূলক নির্বাচন হতে পারে?
সবার জন্য লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড তৈরি করতে পারলে জনগণের পক্ষে তাদের রায় দেওয়া সহজ হয়। যদি কারও আচরণে জনগণ অতিষ্ঠ হয়ে ওঠে, তাহলে ব্যালটের মাধ্যমে তা সহজে জানিয়ে দিতে পারবে। ওপর থেকে চাপিয়ে না দিয়ে জনগণকেই এ বিষয়ে বোঝাপড়ার দায়িত্ব দেওয়া উচিত।
গণমাধ্যমের ভূমিকাও এখানে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। দায়িত্বশীল সাংবাদিকতা জনগণের সঠিক তথ্য জানার অধিকার নিশ্চিত করে এবং গুজব ও অপপ্রচার রোধে ভূমিকা রাখে। একইভাবে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে দায়িত্বশীল আচরণ এখন সময়ের দাবি। যাচাইহীন তথ্য, উসকানিমূলক বক্তব্য বা বিভ্রান্তিকর প্রচার পরিস্থিতিকে আরও অস্থিতিশীল করে তুলতে পারে। এবারের নির্বাচন নানা কারণেই গুরুত্বপূর্ণ। এ সময় গণমাধ্যমের উচিত নৈর্ব্যক্তিকভাবে পর্যালোচনা করে সংবাদ পরিবেশন করা। কোনো কারণেই পক্ষপাতমূলক সংবাদ পরিবেশন করা উচিত নয়। সেই অঙ্গীকার পালন করা হচ্ছে কি না, সেদিকে জনগণও নজর রাখবে।
এই কঠিন সময়েও বিজয় দিবস আমাদের আশার কথা শোনায়। বাংলাদেশ সংকট থেকে ঘুরে দাঁড়াতে জানে।
কিন্তু সেই সক্ষমতা কাজে লাগাতে হলে আমাদের সচেতন সিদ্ধান্ত নিতে হবে—আমরা কি সহিংসতার পুরোনো বৃত্তে ঘুরপাক খাব, নাকি দায়িত্বশীল রাজনীতি ও সহনশীলতার পথে এগিয়ে যাব, এ সিদ্ধান্ত নেওয়ার সময় এখনই।
জাতির আকাঙ্ক্ষা খুব সহজ, কিন্তু গভীর—ভালো থাকুক বাংলাদেশ। রক্তপাত নয়, ব্যালটের মাধ্যমে হোক ক্ষমতার পরিবর্তন। আতঙ্ক নয়, আস্থার মধ্য দিয়ে গড়ে উঠুক আগামী দিনের পথচলা। স্বাধীনতার চেতনার প্রতি প্রকৃত শ্রদ্ধা দেখাতে হলে আমাদের এ পথই কিন্তু বেছে নিতে হবে।
লেখক: ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক আজকের পত্রিকা
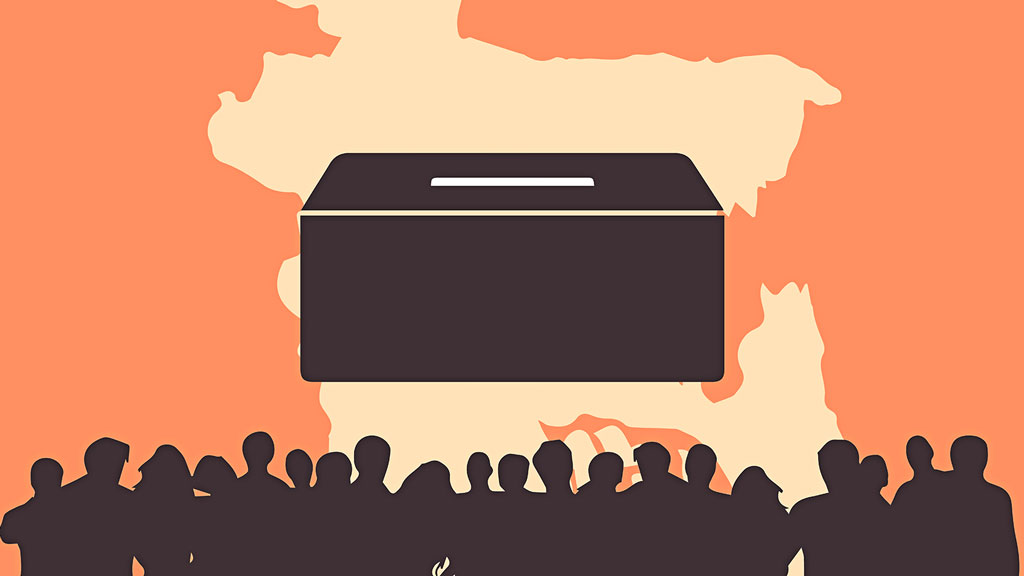
বাংলাদেশ আবারও একটি সংবেদনশীল সময় অতিক্রম করছে। সামনে জাতীয় নির্বাচন—যা শুধু ক্ষমতা পরিবর্তনের আনুষ্ঠানিক প্রক্রিয়া নয়; বরং রাষ্ট্রের গণতান্ত্রিক যাত্রার একটি গুরুত্বপূর্ণ বাঁক। এই নির্বাচন ঘিরে জনগণের প্রত্যাশা যেমন আছে, তেমনি রয়েছে গভীর উদ্বেগও। রাজনৈতিক অঙ্গন উত্তপ্ত, সামাজিক পরিসরে উৎকণ্ঠা, আর সাধারণ মানুষের মনে ভবিষ্যৎ নিয়ে অনিশ্চয়তার দোলাচল স্পষ্টভাবে দৃশ্যমান।
এই শঙ্কা ও উদ্বেগজনক পরিস্থিতির মধ্যেই নির্বাচনের সম্ভাব্য এক প্রার্থীর ওপর নৃশংস হামলার ঘটনা দেশকে নতুন করে নাড়া দিয়েছে। এমন ঘটনা শুধু একজন ব্যক্তির ওপর আঘাত নয়; এটি দেশের রাজনৈতিক সংস্কৃতি, নির্বাচনকালীন নিরাপত্তাব্যবস্থা এবং রাষ্ট্রের সামগ্রিক সক্ষমতার ওপর একটি গুরুতর প্রশ্নচিহ্ন এঁকে দেয়। একটি গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় নির্বাচনে অংশ নেওয়া প্রার্থীর নিরাপত্তা নিশ্চিত করা না গেলে সাধারণ ভোটারের নিরাপত্তা এবং আস্থার জায়গাটি কতটা সুদৃঢ় অবস্থায় দাঁড়িয়ে আছে, সেই প্রশ্ন এড়ানোর সুযোগ নেই।
এমনিতেই বেশ কিছুদিন ধরে যানবাহনে অগ্নিসংযোগ ও ককটেল হামলার মতো ঘটনা ঘটছে। এসব ঘটনা স্পষ্ট ইঙ্গিত দিচ্ছে, একটি পরিকল্পিত আতঙ্ক সৃষ্টির চেষ্টা চলছে। সেই ধারাবাহিকতায় সম্ভাব্য প্রার্থী শরিফ ওসমান হাদির ওপর হামলার ঘটনা নির্বাচন ঘিরে সামগ্রিক নিরাপত্তাব্যবস্থার দুর্বলতাকে নতুন করে সামনে এনেছে। এটি কোনো বিচ্ছিন্ন অপরাধ নয়; বরং নির্বাচনপ্রক্রিয়াকে বাধাগ্রস্ত করার একটি সুপরিকল্পিত অপচেষ্টা বলেই প্রতীয়মান হচ্ছে।
রাজনৈতিক অঙ্গনের অনেকে মনে করছেন, ওসমান হাদির ওপর হামলার লক্ষ্য ছিল শুধু একজন ব্যক্তিকে ভয় দেখানো নয়; বরং নির্বাচনকেই অনিশ্চয়তায় ফেলা। আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারাও স্বীকার করছেন, দীর্ঘদিন ধরে একটি চক্র নির্বাচন বানচালের হুমকি দিয়ে আসছে। সহিংসতার এই ধারাবাহিকতা সেই হুমকিকে বাস্তবে রূপ দেওয়ার ইঙ্গিত বহন করে।
তবে অন্তর্বর্তী সরকার ঘটনাটিকে নির্বাচনবিরোধী ষড়যন্ত্র হিসেবে দেখছে। প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ইউনূসের বক্তব্যে বিষয়টি স্পষ্ট করা হয়েছে যে নির্বাচন বাধাগ্রস্ত করার উদ্দেশ্যে কোনো ধরনের সহিংসতা বরদাশত করা হবে না। জনগণের নিরাপত্তা দেওয়া এবং প্রার্থীদের অবাধ চলাচল নিশ্চিত করা রাষ্ট্রের মৌলিক দায়িত্ব—এই অবস্থান জোরালোভাবে পুনর্ব্যক্ত করা হয়েছে।
কিন্তু বক্তব্যের দৃঢ়তা বাস্তব পদক্ষেপে প্রতিফলিত না হলে জনমনে আস্থা ফিরবে না। নির্বাচন কমিশন ও অন্তর্বর্তী সরকারের এখন প্রধান কর্তব্য হলো, কঠোর নিরাপত্তাব্যবস্থা গ্রহণ, দলমত-নির্বিশেষে দোষীদের দ্রুত শনাক্ত ও বিচারের আওতায় আনা এবং নির্বাচনী পরিবেশের ওপর আস্থা নিশ্চিত করা। গণতন্ত্রের পথ কখনোই ভয় আর সহিংসতার ওপর দাঁড়াতে পারে না।
এ মুহূর্তে সরকারের কঠোর ও নিরপেক্ষ অবস্থানই পারে নির্বাচনকে সুরক্ষিত রাখতে এবং জনগণের আস্থা পুনঃপ্রতিষ্ঠা করতে।
আজকের এই সময়ে দাঁড়িয়ে সবাই স্বীকার করবেন, বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক ইতিহাসে সংকট নতুন কিছু নয়। রাজনৈতিক প্রতিহিংসা, সহিংস আন্দোলন, অবিশ্বাসের চর্চা—এসব উপাদান বহুবার নির্বাচনপ্রক্রিয়াকে বিতর্কিত করেছে। কোনো কোনো সময় নির্বাচন হয়ে উঠেছে জনগণের উৎসব, আবার কোনো কোনো সময় তা রূপ নিয়েছে আতঙ্ক ও শঙ্কার আভাসে। ফলে প্রতিবার ভোটের আগে মানুষের মনে একটি স্বাভাবিক সংশয় সৃষ্টি হয়, সেটি হলো—এই নির্বাচন শান্তিপূর্ণ হবে তো? নাকি আবারও সহিংসতার ছায়া পড়বে?
গণতন্ত্রের মৌলিক বৈশিষ্ট্যই হলো মতভিন্নতা। প্রতিযোগিতা থাকবে, মতের সংঘাত হবে—এটিই স্বাভাবিক। কিন্তু সেই প্রতিযোগিতা যখন অস্ত্র, হামলা কিংবা ভয়ভীতির হয়, তখন তা গণতন্ত্রকে শক্তিশালী করে না; বরং তাকে দুর্বল করে দেয়। রাজনীতির শক্তি হওয়া উচিত যুক্তি, কর্মসূচি ও জনসমর্থন। সহিংসতা কখনোই রাজনৈতিক সমাধান নয়। ইতিহাস বারবার প্রমাণ করেছে, সহিংসতার পথ বেছে নিলে শেষ পর্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত হয় রাষ্ট্র, সমাজ এবং সাধারণ মানুষ।
এই বাস্তবতায় নির্বাচন কমিশন ও আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। নির্বাচন কমিশনের ওপর জনগণের আস্থা অনেকাংশে নির্ভর করে তাদের নিরপেক্ষতা এবং দৃঢ়তার ওপর। একইভাবে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর পেশাদার ও পক্ষপাতহীন ভূমিকা ছাড়া নির্বাচনকালীন সহিংসতা প্রতিরোধ করা সম্ভব নয়। কোনো ধরনের শিথিলতা কিংবা পক্ষপাত পরিস্থিতিকে আরও জটিল করে তুলতে পারে। আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী এখনো যে ধরনের নাজুক অবস্থায় রয়েছে, তাতে তাদের পুরো মনোবল ফিরিয়ে আনতে না পারলে রাষ্ট্র হয়তো বিপদে পড়ে যাবে।
দায়িত্ব অবশ্য শুধু রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলোর ওপরই বর্তায় না; সরকার ও বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলোর ভূমিকাও সমান গুরুত্বপূর্ণ। ক্ষমতায় থাকা কিংবা ক্ষমতার বাইরে থাকা—উভয় অবস্থানেই দায়িত্বশীল আচরণ গণতন্ত্রের পূর্বশর্ত। উসকানিমূলক বক্তব্য, গুজব ছড়ানো কিংবা সহিংস কর্মসূচির মাধ্যমে রাজনৈতিক ফায়দার চেষ্টা শেষ পর্যন্ত জাতির জন্য ক্ষতিকর হয়। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে যা খুশি তা লেখা যায় বলে গুজব ছড়ানো সহজ। অনেকে কোনো প্রমাণ ছাড়াই এমন সব ভুয়া তথ্য ছড়িয়ে থাকেন, যা আদতে পরস্পরের প্রতি সন্দেহ-অবিশ্বাস এমনকি সংঘাতের জন্ম দেয়।
এমনই অস্থির এক সময়ে জাতীয় জীবনে ফিরে এল মহান বিজয় দিবস—১৬ ডিসেম্বর। স্বাধীনতার এদিনটি আমাদের মনে করিয়ে দিল, বাংলাদেশ জন্ম নিয়েছিল রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম এবং অপরিসীম আত্মত্যাগের মধ্য দিয়ে। ১৯৭১ সালে একটি জাতি প্রমাণ করেছিল, তারা অন্যায়ের কাছে মাথানত করতে জানে না। যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশ থেকে আজকের বাংলাদেশ—এই দীর্ঘ পথচলায় রয়েছে রক্ত, বেদনা ও গৌরবের ইতিহাস।
বিজয় দিবস তাই শুধু উৎসবের দিন নয়; এটি আত্মজিজ্ঞাসার সময়ও। স্বাধীনতার এত বছর পর এসে আমাদের নিজেদের প্রশ্ন করা জরুরি—আমরা কি সেই মুক্তিযুদ্ধের চেতনার প্রতি যথাযথ সম্মান দেখাতে পেরেছি? একটি সহনশীল, নিরাপদ ও ন্যায়ভিত্তিক রাষ্ট্র কি গড়ে তুলতে পেরেছি? রাজনৈতিক মতভিন্নতা কি আমরা শান্তিপূর্ণভাবে মেনে নিতে শিখেছি?
দুঃখজনক হলেও সত্য, এসব প্রশ্নের উত্তর এখনো পুরোপুরি ইতিবাচক নয়। রাজনৈতিক অসহিষ্ণুতা, ক্ষমতার অপব্যবহার এবং দায়িত্বহীন আচরণ আমাদের গণতান্ত্রিক অগ্রযাত্রা বারবার বাধাগ্রস্ত করেছে। নির্বাচনের সময় এসব প্রবণতা আরও তীব্র হয়ে ওঠে। অথচ নির্বাচন হওয়া উচিত জনগণের ক্ষমতা প্রয়োগের সবচেয়ে বড় উৎসব; ভয়ের উপলক্ষ নয়।
এই প্রেক্ষাপটে সবচেয়ে জরুরি বিষয় হলো সংযম। রাজনৈতিক দলগুলোর সংযম, প্রশাসনের সংযম এবং রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলোর দায়িত্বশীলতা। একটি অবাধ, সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণ নির্বাচন কোনো একক পক্ষে নিশ্চিত করা সম্ভব নয়। সরকার, বিরোধী দল, নির্বাচন কমিশন, আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী, গণমাধ্যম ও নাগরিক সমাজ—সবার সম্মিলিত উদ্যোগ ছাড়া এই লক্ষ্য অর্জন করা যাবে না। পাশাপাশি এটিও আমাদের ভাবতে হবে, অন্তর্ভুক্তিমূলক নির্বাচন বলতে আমরা কী বুঝব। কোনো রাজনৈতিক দল কিংবা তার সমর্থকদের নির্বাচনের বাইরে রাখা হলে তা কি অন্তর্ভুক্তিমূলক নির্বাচন হতে পারে?
সবার জন্য লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড তৈরি করতে পারলে জনগণের পক্ষে তাদের রায় দেওয়া সহজ হয়। যদি কারও আচরণে জনগণ অতিষ্ঠ হয়ে ওঠে, তাহলে ব্যালটের মাধ্যমে তা সহজে জানিয়ে দিতে পারবে। ওপর থেকে চাপিয়ে না দিয়ে জনগণকেই এ বিষয়ে বোঝাপড়ার দায়িত্ব দেওয়া উচিত।
গণমাধ্যমের ভূমিকাও এখানে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। দায়িত্বশীল সাংবাদিকতা জনগণের সঠিক তথ্য জানার অধিকার নিশ্চিত করে এবং গুজব ও অপপ্রচার রোধে ভূমিকা রাখে। একইভাবে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে দায়িত্বশীল আচরণ এখন সময়ের দাবি। যাচাইহীন তথ্য, উসকানিমূলক বক্তব্য বা বিভ্রান্তিকর প্রচার পরিস্থিতিকে আরও অস্থিতিশীল করে তুলতে পারে। এবারের নির্বাচন নানা কারণেই গুরুত্বপূর্ণ। এ সময় গণমাধ্যমের উচিত নৈর্ব্যক্তিকভাবে পর্যালোচনা করে সংবাদ পরিবেশন করা। কোনো কারণেই পক্ষপাতমূলক সংবাদ পরিবেশন করা উচিত নয়। সেই অঙ্গীকার পালন করা হচ্ছে কি না, সেদিকে জনগণও নজর রাখবে।
এই কঠিন সময়েও বিজয় দিবস আমাদের আশার কথা শোনায়। বাংলাদেশ সংকট থেকে ঘুরে দাঁড়াতে জানে।
কিন্তু সেই সক্ষমতা কাজে লাগাতে হলে আমাদের সচেতন সিদ্ধান্ত নিতে হবে—আমরা কি সহিংসতার পুরোনো বৃত্তে ঘুরপাক খাব, নাকি দায়িত্বশীল রাজনীতি ও সহনশীলতার পথে এগিয়ে যাব, এ সিদ্ধান্ত নেওয়ার সময় এখনই।
জাতির আকাঙ্ক্ষা খুব সহজ, কিন্তু গভীর—ভালো থাকুক বাংলাদেশ। রক্তপাত নয়, ব্যালটের মাধ্যমে হোক ক্ষমতার পরিবর্তন। আতঙ্ক নয়, আস্থার মধ্য দিয়ে গড়ে উঠুক আগামী দিনের পথচলা। স্বাধীনতার চেতনার প্রতি প্রকৃত শ্রদ্ধা দেখাতে হলে আমাদের এ পথই কিন্তু বেছে নিতে হবে।
লেখক: ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক আজকের পত্রিকা

গাছ লাগানো ভালো। প্রতিবছর ৫ জুন বিশ্ব পরিবেশ দিবস উপলক্ষে নানা দেশেই আজকাল গাছ রোপণের রেকর্ড হচ্ছে। কিন্তু এভাবে গাছ রোপণ কি আসলেই জলবায়ু পরিবর্তন ঠেকানোর জন্য যথেষ্ট? এতে কি গ্রীষ্মকালের প্রচণ্ড গরম সহনীয় পর্যায়ে আনা সম্ভব।
২১ এপ্রিল ২০২৪
শুরুটা ছিল বেশ আশাজাগানিয়া। বিধি অনুযায়ী আমাদের দেশে মন্ত্রিসভার সদস্যদের কী বেতন বা সম্মানী এবং ভাতা ও সুবিধাদি এক্ষণে জানা নেই। যুগের সঙ্গে তাল মিলিয়েই নিশ্চয় তা নির্ধারণ করা হয়েছে। মন্ত্রী ছাড়া যাঁরা সংসদ সদস্য, তাঁদের বেলায়ও একই কথা; মোটা অঙ্কের বেতন-ভাতা এবং বলতে গেলে অবাধ সুযোগ-সুবিধা আছে বলেই
১১ ঘণ্টা আগে
বিজয়ের মাস চলছে। বাঙালি জাতির হাজার বছরের শৌর্যবীর্য ও বীরত্বের এক অবিস্মরণীয় গৌরবময় দিনটি ছিল গতকাল। ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর সঙ্গে দীর্ঘ ৯ মাসের রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ শেষে বাঙালি জাতির শ্রেষ্ঠতম অর্জন ‘বিজয়’। এদিন বাঙালির আত্মপরিচয় লাভের দিন।
১১ ঘণ্টা আগে
দেশের মানুষ যখন উৎসবমুখর পরিবেশে ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ভোট দিতে উন্মুখ হয়ে আছে, তখন কিছু অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনায় নির্বাচনে বিশৃঙ্খল পরিবেশ তৈরি হওয়ার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। এ নিয়ে আজকের পত্রিকায় ১৫ ডিসেম্বর একটা উদ্বেগজনক ‘ভোটের আগে আতঙ্ক জনমনে’ শিরোনামে সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে।
১১ ঘণ্টা আগেমুক্তিযুদ্ধকালে গঠিত মুজিবনগর বা প্রবাসী সরকারের প্রধানমন্ত্রীসহ অন্যান্য মন্ত্রী এবং নির্বাচিত সংসদ সদস্যগণ প্রত্যেককে কিছু সম্মানী দেওয়া হতো। প্রধানমন্ত্রী ও মন্ত্রীদের জন্য কিছু বেশি; তবে সংসদ সদস্যদের জন্য ৪০০ টাকা করে বেতন-ভাতা নির্ধারিত ছিল।
বিমল সরকার

শুরুটা ছিল বেশ আশাজাগানিয়া। বিধি অনুযায়ী আমাদের দেশে মন্ত্রিসভার সদস্যদের কী বেতন বা সম্মানী এবং ভাতা ও সুবিধাদি এক্ষণে জানা নেই। যুগের সঙ্গে তাল মিলিয়েই নিশ্চয় তা নির্ধারণ করা হয়েছে। মন্ত্রী ছাড়া যাঁরা সংসদ সদস্য, তাঁদের বেলায়ও একই কথা; মোটা অঙ্কের বেতন-ভাতা এবং বলতে গেলে অবাধ সুযোগ-সুবিধা আছে বলেই মন্ত্রী ও সংসদ সদস্য হওয়ার জন্য একেকজনের কী আগ্রহ, তোড়জোড় ও প্রাণান্ত চেষ্টা-তদবির; তা নির্বাচনের আগমুহূর্তে বেশি টের পাওয়া যায়!
পাকিস্তান আমলে আমাদের দেশে প্রথমে ছিল গভর্নর জেনারেল ও পরে রাষ্ট্রপতিশাসিত (প্রেসিডেনশিয়াল) পদ্ধতির সরকার। পঞ্চাশ ও ষাটের দশকে আইয়ুব খান, ইয়াহিয়া খান ছিলেন পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট (১৯৭১ সাল পর্যন্ত)। প্রদেশে ছিলেন গভর্নর। স্বাধীনতার পর ব্যবস্থা পরিবর্তন করে দেশে সংসদীয় পদ্ধতির সরকার প্রবর্তন করা হয়।
পাকিস্তানের কারাগার থেকে মুক্তি পেয়ে দেশে ফিরে সদ্য স্বাধীন দেশের শাসনদণ্ডভার কাঁধে তুলে নেন শেখ মুজিবুর রহমান। সংসদীয় পদ্ধতিতে ১৯৭২ সালের ১২ জানুয়ারি শেখ মুজিবের প্রথম মন্ত্রিসভা গঠিত হয়। যুদ্ধবিধ্বস্ত ও কপর্দকশূন্য একটি দেশের কান্ডারি হলেন তিনি। স্বাধীন-সার্বভৌম নবীন রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশের যাত্রা হলো শুরু। সরকারের দায়িত্বভার গ্রহণ করে তিনি প্রথমেই নাগরিক জীবনে কৃচ্ছ্রসাধনের ওপর গুরুত্ব দেন। তিনি নবগঠিত মন্ত্রিসভার সদস্যদের বেতন নির্ধারণ করেন পাকিস্তান আমলের তুলনায় অন্তত এক-তৃতীয়াংশ কম। ১৫ ফেব্রুয়ারি ১৯৭২-এ তাঁর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত মন্ত্রিসভার বৈঠকে একজন মন্ত্রীর মাসিক বেতন নির্ধারণ করা হয় ১ হাজার ৫০০ টাকা। এ ছাড়া আপ্যায়ন ভাতা হিসেবে রাখা হয় আরও ৫০০ টাকা। উল্লেখ্য, পাকিস্তান আমলে আইয়ুব খান বা ইয়াহিয়া খানের মন্ত্রিসভার সদস্যরা ২ হাজার ২০০ টাকা করে বেতন এবং প্রত্যেকে মাসিক আপ্যায়ন ভাতা হিসেবে পেতেন আরও ১ হাজার টাকা। অর্থাৎ পাকিস্তান আমলে একজন মন্ত্রী যেখানে ৩ হাজার ২০০ টাকা (বেতন ২২০০ + আপ্যায়ন ভাতা ১০০০) বেতন-ভাতা পেয়েছেন, সেখানে স্বাধীনতার পর বাংলাদেশের একজন মন্ত্রীর জন্য বেতন-ভাতা নির্ধারণ করা হয় সাকল্যে ২ হাজার (বেতন ১৫০০ + ভাতা ৫০০) টাকা।
কিন্তু মন্ত্রীদের জন্য এই বেতন-ভাতা নির্ধারণের পর মাস তো দূরের কথা, সপ্তাহটি কোনোরকমে কেটেছে। পাকিস্তানিদের ৯ মাসব্যাপী তাণ্ডব চালানোর পর একদম শূন্য থেকে বাংলাদেশের পথচলা শুরু। সাহায্য হিসেবে অর্থ, খাদ্যসামগ্রীসহ নানা কিছু আসছে বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে। এমতাবস্থায় মন্ত্রীদের এত
বেশি বেতন নেওয়া ঠিক হবে না। এ ব্যাপারে ঘনিষ্ঠ দু-চারজন সহকর্মী-মন্ত্রীর সঙ্গে কথাও বলেন শেখ মুজিবুর রহমান। ফলে
২৪ ফেব্রুয়ারি ১৯৭২ সালে নতুন করে আবারও সরকারি নির্দেশনা জারি করা হলো। নতুন নির্দেশনা অনুযায়ী মন্ত্রীদের বেতনের পরিমাণ আরও কমিয়ে ১ হাজার ৫০০ টাকার স্থলে ঠিক ১ হাজার টাকা পুনর্নির্ধারণ করা হয়। আপ্যায়ন ভাতা আগের ৫০০ টাকাতেই স্থির থাকে।
১৯৫৪ সালে পূর্ববঙ্গে অনুষ্ঠিত নির্বাচনের আগে মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী, শেরেবাংলা এ কে ফজলুল হক প্রমুখের নেতৃত্বে যুক্তফ্রন্ট গঠিত হয়। ক্ষমতাসীন মুসলিম লীগ সরকারের দুঃশাসনের বিপরীতে যুক্তফ্রন্ট তাদের ২১ দফা নির্বাচনী অঙ্গীকারনামা (মেনিফেস্টো) ঘোষণা করে। ওই অঙ্গীকারনামাকে শাসন-শোষণ আর বৈষম্যের শিকার হতভাগ্য পূর্ববঙ্গবাসী তাদের ‘মুক্তির সনদ’ হিসেবে গ্রহণ এবং নৌকা প্রতীকে ভোট দিয়ে যুক্তফ্রন্টকে বিজয়ী করে। যুক্তফ্রন্টের ২১ দফার অন্তর্ভুক্ত প্রশাসনিক এবং রাজনৈতিক অনেক অঙ্গীকারের মধ্যে ছিল:
১. শাসনব্যয় হ্রাস এবং যুক্তফ্রন্ট সরকারের কোনো মন্ত্রীর ১ হাজার টাকার বেশি বেতন গ্রহণ না করা (১২ নম্বর দফা)।
২. দুর্নীতি-স্বজনপ্রীতি ও ঘুষ-রিসওয়াত বন্ধ করার কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ (১৩ নম্বর দফা)।
৩. বর্ধমান হাউসের পরিবর্তে কম বিলাসের বাড়িতে যুক্তফ্রন্ট সরকারের মুখ্যমন্ত্রীর অবস্থান করা এবং বর্ধমান হাউসকে প্রথমে ছাত্রাবাস ও পরে বাংলা ভাষার গবেষণাগারে পরিণত করা (১৪ নম্বর দফা)। বাঙালির দুর্ভাগ্য যে শেরেবাংলার নেতৃত্বে সরকার গঠন করে মন্ত্রিসভার কার্যক্রম শুরু করতে না করতেই কেন্দ্রীয় সরকার নানা ছুতায় মাত্র ৫৬ দিনের মাথায় প্রাদেশিক যুক্তফ্রন্ট সরকারকে বরখাস্ত করে।
উল্লেখ্য, মুক্তিযুদ্ধকালে গঠিত মুজিবনগর বা প্রবাসী সরকারের প্রধানমন্ত্রীসহ অন্যান্য মন্ত্রী এবং নির্বাচিত সংসদ সদস্যগণকে কিছু সম্মানী দেওয়া হতো। প্রধানমন্ত্রী ও মন্ত্রীদের জন্য কিছু বেশি; তবে সংসদ সদস্যদের জন্য ৪০০ টাকা করে বেতন-ভাতা নির্ধারিত ছিল (যা ১৯৭৫ সাল পর্যন্ত একই হারে বহাল থাকে)। অর্থাৎ বলতে গেলে সত্তরের দশকজুড়ে টিএ-ডিএসহ সামান্য সুবিধা ও সম্মানী হিসেবে ৪০০ টাকা ভাতা পান একজন সংসদ সদস্য।
মন্ত্রী এবং সংসদ সদস্যদের সম্মানী এবং বেতন-ভাতাদি নিয়ে মানুষের বেশ কৌতূহল। বিভিন্ন মহলে এ নিয়ে রয়েছে আলোচনা-সমালোচনা। আবারও নিজের সীমাবদ্ধতাকে স্বীকার করি; আমার জানা নেই ৫০ বছরের বেশি সময়ের ব্যবধানে বর্তমান ব্যবস্থা অনুযায়ী সরকারের একজন মন্ত্রী এবং সংসদ সদস্যের সম্মানী কিংবা বেতন-ভাতার পরিমাণ কী। ১৯৫৪ সালে নির্বাচনের আগেই রাজনীতিকেরা বেতন-ভাতার ব্যাপারে সুস্পষ্টভাবে অঙ্গীকার করেছিলেন। ১৯৭২ সালে সরকার গঠনের অব্যবহিত পর ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করে দফায় দফায় তাঁদের বেতন-ভাতা কমানো হয়। ত্রয়োদশ নির্বাচনের প্রাক্কালে রাজনৈতিক দলগুলোর কাছে প্রত্যাশা, নিজ নিজ ঘোষিতব্য মেনিফেস্টোতে বেতন-ভাতার বিষয়টিও স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হোক।
লেখক: অবসরপ্রাপ্ত কলেজশিক্ষক

শুরুটা ছিল বেশ আশাজাগানিয়া। বিধি অনুযায়ী আমাদের দেশে মন্ত্রিসভার সদস্যদের কী বেতন বা সম্মানী এবং ভাতা ও সুবিধাদি এক্ষণে জানা নেই। যুগের সঙ্গে তাল মিলিয়েই নিশ্চয় তা নির্ধারণ করা হয়েছে। মন্ত্রী ছাড়া যাঁরা সংসদ সদস্য, তাঁদের বেলায়ও একই কথা; মোটা অঙ্কের বেতন-ভাতা এবং বলতে গেলে অবাধ সুযোগ-সুবিধা আছে বলেই মন্ত্রী ও সংসদ সদস্য হওয়ার জন্য একেকজনের কী আগ্রহ, তোড়জোড় ও প্রাণান্ত চেষ্টা-তদবির; তা নির্বাচনের আগমুহূর্তে বেশি টের পাওয়া যায়!
পাকিস্তান আমলে আমাদের দেশে প্রথমে ছিল গভর্নর জেনারেল ও পরে রাষ্ট্রপতিশাসিত (প্রেসিডেনশিয়াল) পদ্ধতির সরকার। পঞ্চাশ ও ষাটের দশকে আইয়ুব খান, ইয়াহিয়া খান ছিলেন পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট (১৯৭১ সাল পর্যন্ত)। প্রদেশে ছিলেন গভর্নর। স্বাধীনতার পর ব্যবস্থা পরিবর্তন করে দেশে সংসদীয় পদ্ধতির সরকার প্রবর্তন করা হয়।
পাকিস্তানের কারাগার থেকে মুক্তি পেয়ে দেশে ফিরে সদ্য স্বাধীন দেশের শাসনদণ্ডভার কাঁধে তুলে নেন শেখ মুজিবুর রহমান। সংসদীয় পদ্ধতিতে ১৯৭২ সালের ১২ জানুয়ারি শেখ মুজিবের প্রথম মন্ত্রিসভা গঠিত হয়। যুদ্ধবিধ্বস্ত ও কপর্দকশূন্য একটি দেশের কান্ডারি হলেন তিনি। স্বাধীন-সার্বভৌম নবীন রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশের যাত্রা হলো শুরু। সরকারের দায়িত্বভার গ্রহণ করে তিনি প্রথমেই নাগরিক জীবনে কৃচ্ছ্রসাধনের ওপর গুরুত্ব দেন। তিনি নবগঠিত মন্ত্রিসভার সদস্যদের বেতন নির্ধারণ করেন পাকিস্তান আমলের তুলনায় অন্তত এক-তৃতীয়াংশ কম। ১৫ ফেব্রুয়ারি ১৯৭২-এ তাঁর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত মন্ত্রিসভার বৈঠকে একজন মন্ত্রীর মাসিক বেতন নির্ধারণ করা হয় ১ হাজার ৫০০ টাকা। এ ছাড়া আপ্যায়ন ভাতা হিসেবে রাখা হয় আরও ৫০০ টাকা। উল্লেখ্য, পাকিস্তান আমলে আইয়ুব খান বা ইয়াহিয়া খানের মন্ত্রিসভার সদস্যরা ২ হাজার ২০০ টাকা করে বেতন এবং প্রত্যেকে মাসিক আপ্যায়ন ভাতা হিসেবে পেতেন আরও ১ হাজার টাকা। অর্থাৎ পাকিস্তান আমলে একজন মন্ত্রী যেখানে ৩ হাজার ২০০ টাকা (বেতন ২২০০ + আপ্যায়ন ভাতা ১০০০) বেতন-ভাতা পেয়েছেন, সেখানে স্বাধীনতার পর বাংলাদেশের একজন মন্ত্রীর জন্য বেতন-ভাতা নির্ধারণ করা হয় সাকল্যে ২ হাজার (বেতন ১৫০০ + ভাতা ৫০০) টাকা।
কিন্তু মন্ত্রীদের জন্য এই বেতন-ভাতা নির্ধারণের পর মাস তো দূরের কথা, সপ্তাহটি কোনোরকমে কেটেছে। পাকিস্তানিদের ৯ মাসব্যাপী তাণ্ডব চালানোর পর একদম শূন্য থেকে বাংলাদেশের পথচলা শুরু। সাহায্য হিসেবে অর্থ, খাদ্যসামগ্রীসহ নানা কিছু আসছে বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে। এমতাবস্থায় মন্ত্রীদের এত
বেশি বেতন নেওয়া ঠিক হবে না। এ ব্যাপারে ঘনিষ্ঠ দু-চারজন সহকর্মী-মন্ত্রীর সঙ্গে কথাও বলেন শেখ মুজিবুর রহমান। ফলে
২৪ ফেব্রুয়ারি ১৯৭২ সালে নতুন করে আবারও সরকারি নির্দেশনা জারি করা হলো। নতুন নির্দেশনা অনুযায়ী মন্ত্রীদের বেতনের পরিমাণ আরও কমিয়ে ১ হাজার ৫০০ টাকার স্থলে ঠিক ১ হাজার টাকা পুনর্নির্ধারণ করা হয়। আপ্যায়ন ভাতা আগের ৫০০ টাকাতেই স্থির থাকে।
১৯৫৪ সালে পূর্ববঙ্গে অনুষ্ঠিত নির্বাচনের আগে মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী, শেরেবাংলা এ কে ফজলুল হক প্রমুখের নেতৃত্বে যুক্তফ্রন্ট গঠিত হয়। ক্ষমতাসীন মুসলিম লীগ সরকারের দুঃশাসনের বিপরীতে যুক্তফ্রন্ট তাদের ২১ দফা নির্বাচনী অঙ্গীকারনামা (মেনিফেস্টো) ঘোষণা করে। ওই অঙ্গীকারনামাকে শাসন-শোষণ আর বৈষম্যের শিকার হতভাগ্য পূর্ববঙ্গবাসী তাদের ‘মুক্তির সনদ’ হিসেবে গ্রহণ এবং নৌকা প্রতীকে ভোট দিয়ে যুক্তফ্রন্টকে বিজয়ী করে। যুক্তফ্রন্টের ২১ দফার অন্তর্ভুক্ত প্রশাসনিক এবং রাজনৈতিক অনেক অঙ্গীকারের মধ্যে ছিল:
১. শাসনব্যয় হ্রাস এবং যুক্তফ্রন্ট সরকারের কোনো মন্ত্রীর ১ হাজার টাকার বেশি বেতন গ্রহণ না করা (১২ নম্বর দফা)।
২. দুর্নীতি-স্বজনপ্রীতি ও ঘুষ-রিসওয়াত বন্ধ করার কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ (১৩ নম্বর দফা)।
৩. বর্ধমান হাউসের পরিবর্তে কম বিলাসের বাড়িতে যুক্তফ্রন্ট সরকারের মুখ্যমন্ত্রীর অবস্থান করা এবং বর্ধমান হাউসকে প্রথমে ছাত্রাবাস ও পরে বাংলা ভাষার গবেষণাগারে পরিণত করা (১৪ নম্বর দফা)। বাঙালির দুর্ভাগ্য যে শেরেবাংলার নেতৃত্বে সরকার গঠন করে মন্ত্রিসভার কার্যক্রম শুরু করতে না করতেই কেন্দ্রীয় সরকার নানা ছুতায় মাত্র ৫৬ দিনের মাথায় প্রাদেশিক যুক্তফ্রন্ট সরকারকে বরখাস্ত করে।
উল্লেখ্য, মুক্তিযুদ্ধকালে গঠিত মুজিবনগর বা প্রবাসী সরকারের প্রধানমন্ত্রীসহ অন্যান্য মন্ত্রী এবং নির্বাচিত সংসদ সদস্যগণকে কিছু সম্মানী দেওয়া হতো। প্রধানমন্ত্রী ও মন্ত্রীদের জন্য কিছু বেশি; তবে সংসদ সদস্যদের জন্য ৪০০ টাকা করে বেতন-ভাতা নির্ধারিত ছিল (যা ১৯৭৫ সাল পর্যন্ত একই হারে বহাল থাকে)। অর্থাৎ বলতে গেলে সত্তরের দশকজুড়ে টিএ-ডিএসহ সামান্য সুবিধা ও সম্মানী হিসেবে ৪০০ টাকা ভাতা পান একজন সংসদ সদস্য।
মন্ত্রী এবং সংসদ সদস্যদের সম্মানী এবং বেতন-ভাতাদি নিয়ে মানুষের বেশ কৌতূহল। বিভিন্ন মহলে এ নিয়ে রয়েছে আলোচনা-সমালোচনা। আবারও নিজের সীমাবদ্ধতাকে স্বীকার করি; আমার জানা নেই ৫০ বছরের বেশি সময়ের ব্যবধানে বর্তমান ব্যবস্থা অনুযায়ী সরকারের একজন মন্ত্রী এবং সংসদ সদস্যের সম্মানী কিংবা বেতন-ভাতার পরিমাণ কী। ১৯৫৪ সালে নির্বাচনের আগেই রাজনীতিকেরা বেতন-ভাতার ব্যাপারে সুস্পষ্টভাবে অঙ্গীকার করেছিলেন। ১৯৭২ সালে সরকার গঠনের অব্যবহিত পর ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করে দফায় দফায় তাঁদের বেতন-ভাতা কমানো হয়। ত্রয়োদশ নির্বাচনের প্রাক্কালে রাজনৈতিক দলগুলোর কাছে প্রত্যাশা, নিজ নিজ ঘোষিতব্য মেনিফেস্টোতে বেতন-ভাতার বিষয়টিও স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হোক।
লেখক: অবসরপ্রাপ্ত কলেজশিক্ষক

গাছ লাগানো ভালো। প্রতিবছর ৫ জুন বিশ্ব পরিবেশ দিবস উপলক্ষে নানা দেশেই আজকাল গাছ রোপণের রেকর্ড হচ্ছে। কিন্তু এভাবে গাছ রোপণ কি আসলেই জলবায়ু পরিবর্তন ঠেকানোর জন্য যথেষ্ট? এতে কি গ্রীষ্মকালের প্রচণ্ড গরম সহনীয় পর্যায়ে আনা সম্ভব।
২১ এপ্রিল ২০২৪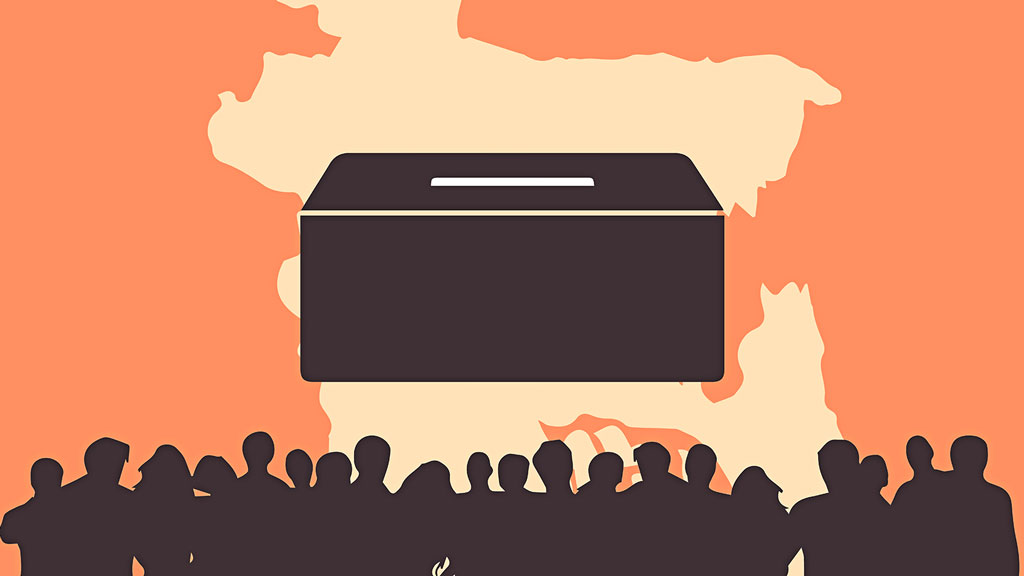
বাংলাদেশ আবারও একটি সংবেদনশীল সময় অতিক্রম করছে। সামনে জাতীয় নির্বাচন—যা শুধু ক্ষমতা পরিবর্তনের আনুষ্ঠানিক প্রক্রিয়া নয়; বরং রাষ্ট্রের গণতান্ত্রিক যাত্রার একটি গুরুত্বপূর্ণ বাঁক। এই নির্বাচন ঘিরে জনগণের প্রত্যাশা যেমন আছে, তেমনি রয়েছে গভীর উদ্বেগও।
১১ ঘণ্টা আগে
বিজয়ের মাস চলছে। বাঙালি জাতির হাজার বছরের শৌর্যবীর্য ও বীরত্বের এক অবিস্মরণীয় গৌরবময় দিনটি ছিল গতকাল। ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর সঙ্গে দীর্ঘ ৯ মাসের রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ শেষে বাঙালি জাতির শ্রেষ্ঠতম অর্জন ‘বিজয়’। এদিন বাঙালির আত্মপরিচয় লাভের দিন।
১১ ঘণ্টা আগে
দেশের মানুষ যখন উৎসবমুখর পরিবেশে ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ভোট দিতে উন্মুখ হয়ে আছে, তখন কিছু অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনায় নির্বাচনে বিশৃঙ্খল পরিবেশ তৈরি হওয়ার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। এ নিয়ে আজকের পত্রিকায় ১৫ ডিসেম্বর একটা উদ্বেগজনক ‘ভোটের আগে আতঙ্ক জনমনে’ শিরোনামে সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে।
১১ ঘণ্টা আগেডা. মুহাম্মাদ মাহতাব হোসাইন মাজেদ

বিজয়ের মাস চলছে। বাঙালি জাতির হাজার বছরের শৌর্যবীর্য ও বীরত্বের এক অবিস্মরণীয় গৌরবময় দিনটি ছিল গতকাল। ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর সঙ্গে দীর্ঘ ৯ মাসের রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ শেষে বাঙালি জাতির শ্রেষ্ঠতম অর্জন ‘বিজয়’। এদিন বাঙালির আত্মপরিচয় লাভের দিন।
ডিসেম্বর এলেই বাংলাদেশের জাতীয় জীবনে এক ভিন্ন আবহ তৈরি হয়। শীতের সকালের কুয়াশার ভেতর দিয়ে উড়তে থাকা লাল-সবুজ পতাকা আমাদের মনে করিয়ে দেয় এক রক্তাক্ত কিন্তু গৌরবময় ইতিহাসের কথা। আজ বিজয় দিবসে দাঁড়িয়ে আমরা গর্বের সঙ্গে সেই ইতিহাস স্মরণ করি, একই সঙ্গে নিজেদের দায়িত্বের দিকে ফিরে তাকাই।
এই বিজয় কোনো আকস্মিক ঘটনা ছিল না। পাকিস্তানি শাসনামলের দীর্ঘ বৈষম্য, রাজনৈতিক বঞ্চনা এবং সাংস্কৃতিক দমন-পীড়নের বিরুদ্ধে বাঙালির প্রতিবাদ ধীরে ধীরে এক অনিবার্য সংগ্রামে রূপ নেয়। ভাষা আন্দোলন থেকে ছয় দফা, গণ-অভ্যুত্থান থেকে অসহযোগ—এই ধারাবাহিক লড়াইই মুক্তিযুদ্ধের ভিত্তি তৈরি করেছিল। ২৫ মার্চের কালরাতে নির্বিচার গণহত্যা সেই সংগ্রামকে চূড়ান্ত রূপ দেয়। অস্তিত্ব রক্ষার তাগিদেই বাঙালি জাতি অস্ত্র হাতে নিতে বাধ্য হয়।
মুক্তিযুদ্ধের সবচেয়ে বড় শক্তি ছিল সাধারণ মানুষ। এটি কোনো পেশাদার বাহিনীর একক যুদ্ধ ছিল না; বরং গ্রাম ও শহরের মানুষ মিলেই গড়ে তুলেছিল প্রতিরোধ। কৃষক যেমন লড়েছেন, তেমনি লড়েছেন শ্রমিক, ছাত্র, শিক্ষক, শিল্পী ও বুদ্ধিজীবীরা। নারীরা শুধু সহযোদ্ধাই নন, অনেক ক্ষেত্রে সম্মুখযোদ্ধার ভূমিকাও পালন করেছেন। এই সর্বস্তরের মানুষের অংশগ্রহণই মুক্তিযুদ্ধকে একটি সর্বজনীন জাতীয় সংগ্রামে পরিণত করে।
এই বিজয়ের মূল্য ছিল ভয়াবহ। ৩০ লাখ শহীদের আত্মত্যাগ, অসংখ্য মা-বোনের সম্ভ্রমহানি, লাখো মানুষের বাস্তুচ্যুতি—সব মিলিয়ে স্বাধীনতার মূল্য পরিশোধ করতে হয়েছে। এই ইতিহাস আমাদের গৌরবের, কিন্তু একই সঙ্গে বেদনারও। বিজয় দিবস তাই শুধু উৎসবের নয়, নীরব শ্রদ্ধা ও আত্মসমালোচনারও দিন।
৫৪ বছর পর বাংলাদেশের দিকে তাকালে অগ্রগতির চিত্র অস্বীকার করা যায় না। যুদ্ধবিধ্বস্ত একটি দেশ আজ উন্নয়নশীল রাষ্ট্র হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছে। খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা, বিদ্যুৎ উৎপাদনে অগ্রগতি, সড়ক-সেতু ও যোগাযোগ অবকাঠামোর বিস্তার দেশের অর্থনৈতিক সক্ষমতা বাড়িয়েছে। শিক্ষা ও স্বাস্থ্য সূচকে উন্নতি, নারীশিক্ষা ও নারী অংশগ্রহণ বৃদ্ধি সমাজে ইতিবাচক পরিবর্তন এনেছে।
আন্তর্জাতিক পরিসরেও বাংলাদেশের অবস্থান এখন দৃশ্যমান। জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে বাংলাদেশের ভূমিকা, জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকি মোকাবিলায় সোচ্চার অবস্থান এবং মানবিক সহায়তায় অংশগ্রহণ দেশটির ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করেছে। একসময় যে দেশটিকে অবহেলার চোখে দেখা হতো, আজ সেই দেশ সম্ভাবনার নাম।
তবু বিজয়ের এই সাফল্যের আড়ালে কিছু বাস্তবতা আমাদের বিব্রত করে। সমাজে বৈষম্য এখনো বড় সমস্যা। ধনী ও দরিদ্রের ব্যবধান কমার বদলে অনেক ক্ষেত্রে বেড়েছে। শহরের সুযোগ-সুবিধা গ্রাম পর্যন্ত সমানভাবে পৌঁছায়নি। শিক্ষা, স্বাস্থ্যসেবা ও কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে সমতার প্রশ্ন আজও জোরালোভাবে উপস্থিত।
একটি স্বাধীন রাষ্ট্রের মূল ভিত্তি আইনের শাসন ও ন্যায়বিচার। এই জায়গায় ঘাটতি থাকলে মানুষের রাষ্ট্রের ওপর আস্থা দুর্বল হয়ে পড়ে। বিচারহীনতার সংস্কৃতি যেকোনো সমাজকে ভেতর থেকে ক্ষয় করে দেয়। বিজয়ের চেতনা তখনই অর্থবহ হয়, যখন সাধারণ মানুষ নিরাপদ বোধ করে এবং ন্যায়বিচার পাওয়ার আশা রাখতে পারে।
গণতন্ত্র ও মতপ্রকাশের স্বাধীনতাও মুক্তিযুদ্ধের আদর্শের সঙ্গে ওতপ্রোত জড়িত। ভিন্নমতকে শত্রুতা হিসেবে দেখার প্রবণতা সমাজে বিভাজন সৃষ্টি করে। একটি পরিণত রাষ্ট্রে মতভিন্নতা থাকবে, কিন্তু সেটিকে সহনশীলতার মধ্য দিয়ে মোকাবিলা করতে হবে। যুক্তি ও আলোচনার সংস্কৃতি শক্তিশালী না হলে বিজয়ের চেতনা দুর্বল হয়ে পড়ে।
দুর্নীতি আজ আমাদের জাতীয় জীবনের অন্যতম বড় চ্যালেঞ্জ। এটি কেবল অর্থনৈতিক ক্ষতির বিষয় নয়; বরং নৈতিক অবক্ষয়ের প্রতীক। দুর্নীতির সঙ্গে আপস করা মানেই মুক্তিযুদ্ধের আদর্শের সঙ্গে আপস করা। সুশাসন ও জবাবদিহি নিশ্চিত করা ছাড়া উন্নয়ন কখনোই টেকসই হতে পারে না।
মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসচর্চার ক্ষেত্রেও দায়িত্বশীলতা জরুরি। ইতিহাস বিকৃতি বা রাজনৈতিক সুবিধার হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার বিজয়ের চেতনাকে ক্ষতিগ্রস্ত করে। এই ইতিহাস কোনো ব্যক্তি বা দলের সম্পত্তি নয়; এটি পুরো জাতির। সত্য ও বস্তুনিষ্ঠ ইতিহাসচর্চাই ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে সঠিক পথ দেখাতে পারে।
আজকের তরুণ প্রজন্মের কাছে মুক্তিযুদ্ধ অনেক সময় বইয়ের পাতায় সীমাবদ্ধ একটি অধ্যায় হয়ে দাঁড়ায়। অথচ মুক্তিযুদ্ধ ছিল একটি মূল্যবোধের সংগ্রাম—ন্যায়, সমতা ও মানবিকতার জন্য লড়াই। এই মূল্যবোধ তরুণদের মাঝে ছড়িয়ে দিতে না পারলে উন্নয়নের অর্জনও একসময় অর্থহীন হয়ে পড়বে।
উন্নয়ন মানে শুধু বড় প্রকল্প নয়। মানুষের জীবনমানের উন্নয়নই রাষ্ট্রের সাফল্যের আসল মাপকাঠি। গ্রামবাংলা ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠী উন্নয়নের সুফল থেকে বঞ্চিত থাকলে স্বাধীনতার স্বপ্ন অপূর্ণ থেকে যায়। কৃষক ন্যায্য দাম না পেলে, শ্রমিক নিরাপত্তাহীন থাকলে বিজয়ের অর্থ প্রশ্নের মুখে পড়ে।
নারী ও শিশুর নিরাপত্তা ও মর্যাদা নিশ্চিত করা স্বাধীন রাষ্ট্রের নৈতিক দায়িত্ব। মুক্তিযুদ্ধের সময় নারীরা যে ভয়াবহ নির্যাতনের শিকার হয়েছেন, তার ঐতিহাসিক বাস্তবতা আমাদের এই দায়িত্ব আরও গভীরভাবে স্মরণ করিয়ে দেয়।
বিজয় দিবস আমাদের শেখায়, স্বাধীনতা কোনো স্থির অর্জন নয়। এটি প্রতিদিন রক্ষা করার বিষয়। দেশপ্রেম মানে কেবল স্লোগান দেওয়া নয়; আইন মেনে চলা, অন্যায়ের প্রতিবাদ করা আর মানবিক আচরণ করাই দেশপ্রেমের প্রকৃত রূপ।

বিজয়ের মাস চলছে। বাঙালি জাতির হাজার বছরের শৌর্যবীর্য ও বীরত্বের এক অবিস্মরণীয় গৌরবময় দিনটি ছিল গতকাল। ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর সঙ্গে দীর্ঘ ৯ মাসের রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ শেষে বাঙালি জাতির শ্রেষ্ঠতম অর্জন ‘বিজয়’। এদিন বাঙালির আত্মপরিচয় লাভের দিন।
ডিসেম্বর এলেই বাংলাদেশের জাতীয় জীবনে এক ভিন্ন আবহ তৈরি হয়। শীতের সকালের কুয়াশার ভেতর দিয়ে উড়তে থাকা লাল-সবুজ পতাকা আমাদের মনে করিয়ে দেয় এক রক্তাক্ত কিন্তু গৌরবময় ইতিহাসের কথা। আজ বিজয় দিবসে দাঁড়িয়ে আমরা গর্বের সঙ্গে সেই ইতিহাস স্মরণ করি, একই সঙ্গে নিজেদের দায়িত্বের দিকে ফিরে তাকাই।
এই বিজয় কোনো আকস্মিক ঘটনা ছিল না। পাকিস্তানি শাসনামলের দীর্ঘ বৈষম্য, রাজনৈতিক বঞ্চনা এবং সাংস্কৃতিক দমন-পীড়নের বিরুদ্ধে বাঙালির প্রতিবাদ ধীরে ধীরে এক অনিবার্য সংগ্রামে রূপ নেয়। ভাষা আন্দোলন থেকে ছয় দফা, গণ-অভ্যুত্থান থেকে অসহযোগ—এই ধারাবাহিক লড়াইই মুক্তিযুদ্ধের ভিত্তি তৈরি করেছিল। ২৫ মার্চের কালরাতে নির্বিচার গণহত্যা সেই সংগ্রামকে চূড়ান্ত রূপ দেয়। অস্তিত্ব রক্ষার তাগিদেই বাঙালি জাতি অস্ত্র হাতে নিতে বাধ্য হয়।
মুক্তিযুদ্ধের সবচেয়ে বড় শক্তি ছিল সাধারণ মানুষ। এটি কোনো পেশাদার বাহিনীর একক যুদ্ধ ছিল না; বরং গ্রাম ও শহরের মানুষ মিলেই গড়ে তুলেছিল প্রতিরোধ। কৃষক যেমন লড়েছেন, তেমনি লড়েছেন শ্রমিক, ছাত্র, শিক্ষক, শিল্পী ও বুদ্ধিজীবীরা। নারীরা শুধু সহযোদ্ধাই নন, অনেক ক্ষেত্রে সম্মুখযোদ্ধার ভূমিকাও পালন করেছেন। এই সর্বস্তরের মানুষের অংশগ্রহণই মুক্তিযুদ্ধকে একটি সর্বজনীন জাতীয় সংগ্রামে পরিণত করে।
এই বিজয়ের মূল্য ছিল ভয়াবহ। ৩০ লাখ শহীদের আত্মত্যাগ, অসংখ্য মা-বোনের সম্ভ্রমহানি, লাখো মানুষের বাস্তুচ্যুতি—সব মিলিয়ে স্বাধীনতার মূল্য পরিশোধ করতে হয়েছে। এই ইতিহাস আমাদের গৌরবের, কিন্তু একই সঙ্গে বেদনারও। বিজয় দিবস তাই শুধু উৎসবের নয়, নীরব শ্রদ্ধা ও আত্মসমালোচনারও দিন।
৫৪ বছর পর বাংলাদেশের দিকে তাকালে অগ্রগতির চিত্র অস্বীকার করা যায় না। যুদ্ধবিধ্বস্ত একটি দেশ আজ উন্নয়নশীল রাষ্ট্র হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছে। খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা, বিদ্যুৎ উৎপাদনে অগ্রগতি, সড়ক-সেতু ও যোগাযোগ অবকাঠামোর বিস্তার দেশের অর্থনৈতিক সক্ষমতা বাড়িয়েছে। শিক্ষা ও স্বাস্থ্য সূচকে উন্নতি, নারীশিক্ষা ও নারী অংশগ্রহণ বৃদ্ধি সমাজে ইতিবাচক পরিবর্তন এনেছে।
আন্তর্জাতিক পরিসরেও বাংলাদেশের অবস্থান এখন দৃশ্যমান। জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে বাংলাদেশের ভূমিকা, জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকি মোকাবিলায় সোচ্চার অবস্থান এবং মানবিক সহায়তায় অংশগ্রহণ দেশটির ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করেছে। একসময় যে দেশটিকে অবহেলার চোখে দেখা হতো, আজ সেই দেশ সম্ভাবনার নাম।
তবু বিজয়ের এই সাফল্যের আড়ালে কিছু বাস্তবতা আমাদের বিব্রত করে। সমাজে বৈষম্য এখনো বড় সমস্যা। ধনী ও দরিদ্রের ব্যবধান কমার বদলে অনেক ক্ষেত্রে বেড়েছে। শহরের সুযোগ-সুবিধা গ্রাম পর্যন্ত সমানভাবে পৌঁছায়নি। শিক্ষা, স্বাস্থ্যসেবা ও কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে সমতার প্রশ্ন আজও জোরালোভাবে উপস্থিত।
একটি স্বাধীন রাষ্ট্রের মূল ভিত্তি আইনের শাসন ও ন্যায়বিচার। এই জায়গায় ঘাটতি থাকলে মানুষের রাষ্ট্রের ওপর আস্থা দুর্বল হয়ে পড়ে। বিচারহীনতার সংস্কৃতি যেকোনো সমাজকে ভেতর থেকে ক্ষয় করে দেয়। বিজয়ের চেতনা তখনই অর্থবহ হয়, যখন সাধারণ মানুষ নিরাপদ বোধ করে এবং ন্যায়বিচার পাওয়ার আশা রাখতে পারে।
গণতন্ত্র ও মতপ্রকাশের স্বাধীনতাও মুক্তিযুদ্ধের আদর্শের সঙ্গে ওতপ্রোত জড়িত। ভিন্নমতকে শত্রুতা হিসেবে দেখার প্রবণতা সমাজে বিভাজন সৃষ্টি করে। একটি পরিণত রাষ্ট্রে মতভিন্নতা থাকবে, কিন্তু সেটিকে সহনশীলতার মধ্য দিয়ে মোকাবিলা করতে হবে। যুক্তি ও আলোচনার সংস্কৃতি শক্তিশালী না হলে বিজয়ের চেতনা দুর্বল হয়ে পড়ে।
দুর্নীতি আজ আমাদের জাতীয় জীবনের অন্যতম বড় চ্যালেঞ্জ। এটি কেবল অর্থনৈতিক ক্ষতির বিষয় নয়; বরং নৈতিক অবক্ষয়ের প্রতীক। দুর্নীতির সঙ্গে আপস করা মানেই মুক্তিযুদ্ধের আদর্শের সঙ্গে আপস করা। সুশাসন ও জবাবদিহি নিশ্চিত করা ছাড়া উন্নয়ন কখনোই টেকসই হতে পারে না।
মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসচর্চার ক্ষেত্রেও দায়িত্বশীলতা জরুরি। ইতিহাস বিকৃতি বা রাজনৈতিক সুবিধার হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার বিজয়ের চেতনাকে ক্ষতিগ্রস্ত করে। এই ইতিহাস কোনো ব্যক্তি বা দলের সম্পত্তি নয়; এটি পুরো জাতির। সত্য ও বস্তুনিষ্ঠ ইতিহাসচর্চাই ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে সঠিক পথ দেখাতে পারে।
আজকের তরুণ প্রজন্মের কাছে মুক্তিযুদ্ধ অনেক সময় বইয়ের পাতায় সীমাবদ্ধ একটি অধ্যায় হয়ে দাঁড়ায়। অথচ মুক্তিযুদ্ধ ছিল একটি মূল্যবোধের সংগ্রাম—ন্যায়, সমতা ও মানবিকতার জন্য লড়াই। এই মূল্যবোধ তরুণদের মাঝে ছড়িয়ে দিতে না পারলে উন্নয়নের অর্জনও একসময় অর্থহীন হয়ে পড়বে।
উন্নয়ন মানে শুধু বড় প্রকল্প নয়। মানুষের জীবনমানের উন্নয়নই রাষ্ট্রের সাফল্যের আসল মাপকাঠি। গ্রামবাংলা ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠী উন্নয়নের সুফল থেকে বঞ্চিত থাকলে স্বাধীনতার স্বপ্ন অপূর্ণ থেকে যায়। কৃষক ন্যায্য দাম না পেলে, শ্রমিক নিরাপত্তাহীন থাকলে বিজয়ের অর্থ প্রশ্নের মুখে পড়ে।
নারী ও শিশুর নিরাপত্তা ও মর্যাদা নিশ্চিত করা স্বাধীন রাষ্ট্রের নৈতিক দায়িত্ব। মুক্তিযুদ্ধের সময় নারীরা যে ভয়াবহ নির্যাতনের শিকার হয়েছেন, তার ঐতিহাসিক বাস্তবতা আমাদের এই দায়িত্ব আরও গভীরভাবে স্মরণ করিয়ে দেয়।
বিজয় দিবস আমাদের শেখায়, স্বাধীনতা কোনো স্থির অর্জন নয়। এটি প্রতিদিন রক্ষা করার বিষয়। দেশপ্রেম মানে কেবল স্লোগান দেওয়া নয়; আইন মেনে চলা, অন্যায়ের প্রতিবাদ করা আর মানবিক আচরণ করাই দেশপ্রেমের প্রকৃত রূপ।

গাছ লাগানো ভালো। প্রতিবছর ৫ জুন বিশ্ব পরিবেশ দিবস উপলক্ষে নানা দেশেই আজকাল গাছ রোপণের রেকর্ড হচ্ছে। কিন্তু এভাবে গাছ রোপণ কি আসলেই জলবায়ু পরিবর্তন ঠেকানোর জন্য যথেষ্ট? এতে কি গ্রীষ্মকালের প্রচণ্ড গরম সহনীয় পর্যায়ে আনা সম্ভব।
২১ এপ্রিল ২০২৪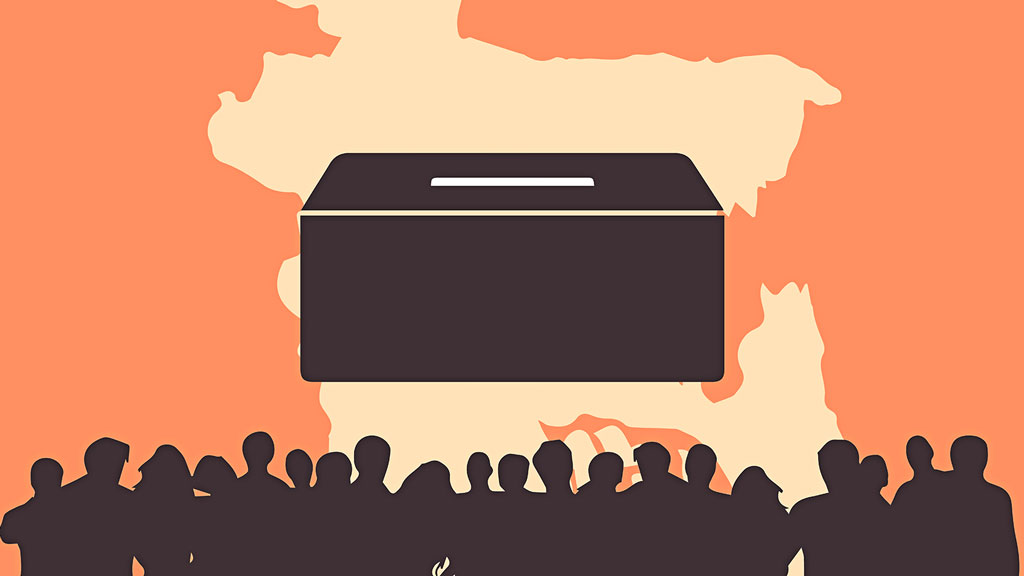
বাংলাদেশ আবারও একটি সংবেদনশীল সময় অতিক্রম করছে। সামনে জাতীয় নির্বাচন—যা শুধু ক্ষমতা পরিবর্তনের আনুষ্ঠানিক প্রক্রিয়া নয়; বরং রাষ্ট্রের গণতান্ত্রিক যাত্রার একটি গুরুত্বপূর্ণ বাঁক। এই নির্বাচন ঘিরে জনগণের প্রত্যাশা যেমন আছে, তেমনি রয়েছে গভীর উদ্বেগও।
১১ ঘণ্টা আগে
শুরুটা ছিল বেশ আশাজাগানিয়া। বিধি অনুযায়ী আমাদের দেশে মন্ত্রিসভার সদস্যদের কী বেতন বা সম্মানী এবং ভাতা ও সুবিধাদি এক্ষণে জানা নেই। যুগের সঙ্গে তাল মিলিয়েই নিশ্চয় তা নির্ধারণ করা হয়েছে। মন্ত্রী ছাড়া যাঁরা সংসদ সদস্য, তাঁদের বেলায়ও একই কথা; মোটা অঙ্কের বেতন-ভাতা এবং বলতে গেলে অবাধ সুযোগ-সুবিধা আছে বলেই
১১ ঘণ্টা আগে
দেশের মানুষ যখন উৎসবমুখর পরিবেশে ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ভোট দিতে উন্মুখ হয়ে আছে, তখন কিছু অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনায় নির্বাচনে বিশৃঙ্খল পরিবেশ তৈরি হওয়ার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। এ নিয়ে আজকের পত্রিকায় ১৫ ডিসেম্বর একটা উদ্বেগজনক ‘ভোটের আগে আতঙ্ক জনমনে’ শিরোনামে সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে।
১১ ঘণ্টা আগেসম্পাদকীয়

দেশের মানুষ যখন উৎসবমুখর পরিবেশে ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ভোট দিতে উন্মুখ হয়ে আছে, তখন কিছু অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনায় নির্বাচনে বিশৃঙ্খল পরিবেশ তৈরি হওয়ার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। এ নিয়ে আজকের পত্রিকায় ১৫ ডিসেম্বর একটা উদ্বেগজনক ‘ভোটের আগে আতঙ্ক জনমনে’ শিরোনামে সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে।
মূলত তফসিল ঘোষণার পরের দিন ইনকিলাব মঞ্চের নেতা শরিফ ওসমান হাদিকে হত্যার উদ্দেশ্যে গুলি করার ঘটনা সেই আশঙ্কাকে জোরালো করেছে। ফলে ওই ঘটনা সম্ভাব্য প্রার্থীসহ সাধারণ মানুষের মধ্যে নির্বাচন নিয়ে উৎসাহের বদলে আতঙ্ক তৈরি করেছে। নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছেন রাজনৈতিক নেতারাসহ জুলাই যোদ্ধারা। সরকার নিরাপত্তা দেওয়ার আশ্বাস দিলেও এই পরিস্থিতিতে নির্বাচনী প্রচার নিয়ে আশঙ্কা করছেন সম্ভাব্য প্রার্থীরা।
প্রকাশ্যে এই হামলা প্রমাণ করেছে, দেশের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির হাল অত্যন্ত নাজুক। নিরাপত্তা বিশ্লেষকদের অভিমত অনুযায়ী, সময়মতো কার্যকর উদ্যোগের অভাবই এই অবস্থার জন্য দায়ী। নির্বাচনপ্রক্রিয়া শুরু হওয়ার পরও যদি সম্ভাব্য প্রার্থীরা জীবন নিয়ে শঙ্কায় থাকেন, তবে তা একটি অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের পরিবেশের জন্য মারাত্মক হুমকি হতে পারে।
এই ঘটনা শুধু যে একটি বিচ্ছিন্ন হামলা নয়; এটি পুরো নির্বাচনের প্রক্রিয়াকে বাধাগ্রস্ত করার সুপরিকল্পিত ষড়যন্ত্র হিসেবে দেখছেন রাজনৈতিক বিশ্লেষকেরা। প্রশ্ন হলো, ২০২৪ সালের রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের পর আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি কখনো স্বাভাবিক ছিল না। একের পর এক মবের ঘটনা ঘটার পরেও এসব নিয়ন্ত্রণে সরকার এবং আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছে। এরপর জুলাই আন্দোলনের পর দেশের অনেক থানার অস্ত্র লুট হয়েছিল। সে সময় অধিকাংশ অস্ত্র উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি। সবচেয়ে ভয়াবহ ব্যাপার হলো, ৫ আগস্টের পর একে একে অনেক চিহ্নিত সন্ত্রাসী এবং জঙ্গিদের ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল। যে পরিস্থিতি আজ দাঁড়িয়েছে, তার সবটাই আগের ঘটনার ধারাবাহিকতা।
কিন্তু সরকার প্রথম থেকে বিশেষ করে পুলিশ বাহিনীকে সক্রিয় করতে ব্যর্থ হয়েছে। সংস্কার নিয়ে বিভিন্ন ধরনের কথাবার্তার আড়ালে জনগণের নিরাপত্তার বিষয়টি সব সময় এড়িয়ে যাওয়া হয়েছে।
এখন নির্বাচনের আগে প্রায় দেড় বছরের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির সংকট কীভাবে কাটানো সম্ভব? একটি ঘটনা ঘটার পর আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে নিয়োজিত ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা নানা কথার ফুলঝুরি শোনান, কিন্তু কিছুদিন পর পরিস্থিতি পরিবর্তনের কোনো লক্ষণ দেখা যায় না।
নির্বাচন যেন কোনোভাবেই বাধাগ্রস্ত না হয়, সেটি নিশ্চিত করতে অন্তর্বর্তী সরকার এবং নির্বাচন কমিশনকে শুধু আশ্বাস নয়, বরং কঠোর ও দৃশ্যমান পদক্ষেপ দেখাতে হবে। এখন দরকার দ্রুত বিচার এবং দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি। এই হামলার তদন্ত এবং অপরাধীদের দ্রুত গ্রেপ্তার নিশ্চিত করে জনগণের মধ্যে আস্থা ফিরিয়ে আনাটাই এখন সরকারের জন্য প্রধান চ্যালেঞ্জ। নির্বাচন কমিশনের দায়িত্ব হলো, একটি শঙ্কামুক্ত পরিবেশ তৈরি করে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়াকে এগিয়ে নেওয়া। এই পরিস্থিতিতে নিরাপত্তাই এখন নির্বাচনের প্রধান পূর্বশর্ত।

দেশের মানুষ যখন উৎসবমুখর পরিবেশে ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ভোট দিতে উন্মুখ হয়ে আছে, তখন কিছু অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনায় নির্বাচনে বিশৃঙ্খল পরিবেশ তৈরি হওয়ার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। এ নিয়ে আজকের পত্রিকায় ১৫ ডিসেম্বর একটা উদ্বেগজনক ‘ভোটের আগে আতঙ্ক জনমনে’ শিরোনামে সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে।
মূলত তফসিল ঘোষণার পরের দিন ইনকিলাব মঞ্চের নেতা শরিফ ওসমান হাদিকে হত্যার উদ্দেশ্যে গুলি করার ঘটনা সেই আশঙ্কাকে জোরালো করেছে। ফলে ওই ঘটনা সম্ভাব্য প্রার্থীসহ সাধারণ মানুষের মধ্যে নির্বাচন নিয়ে উৎসাহের বদলে আতঙ্ক তৈরি করেছে। নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছেন রাজনৈতিক নেতারাসহ জুলাই যোদ্ধারা। সরকার নিরাপত্তা দেওয়ার আশ্বাস দিলেও এই পরিস্থিতিতে নির্বাচনী প্রচার নিয়ে আশঙ্কা করছেন সম্ভাব্য প্রার্থীরা।
প্রকাশ্যে এই হামলা প্রমাণ করেছে, দেশের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির হাল অত্যন্ত নাজুক। নিরাপত্তা বিশ্লেষকদের অভিমত অনুযায়ী, সময়মতো কার্যকর উদ্যোগের অভাবই এই অবস্থার জন্য দায়ী। নির্বাচনপ্রক্রিয়া শুরু হওয়ার পরও যদি সম্ভাব্য প্রার্থীরা জীবন নিয়ে শঙ্কায় থাকেন, তবে তা একটি অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের পরিবেশের জন্য মারাত্মক হুমকি হতে পারে।
এই ঘটনা শুধু যে একটি বিচ্ছিন্ন হামলা নয়; এটি পুরো নির্বাচনের প্রক্রিয়াকে বাধাগ্রস্ত করার সুপরিকল্পিত ষড়যন্ত্র হিসেবে দেখছেন রাজনৈতিক বিশ্লেষকেরা। প্রশ্ন হলো, ২০২৪ সালের রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের পর আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি কখনো স্বাভাবিক ছিল না। একের পর এক মবের ঘটনা ঘটার পরেও এসব নিয়ন্ত্রণে সরকার এবং আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছে। এরপর জুলাই আন্দোলনের পর দেশের অনেক থানার অস্ত্র লুট হয়েছিল। সে সময় অধিকাংশ অস্ত্র উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি। সবচেয়ে ভয়াবহ ব্যাপার হলো, ৫ আগস্টের পর একে একে অনেক চিহ্নিত সন্ত্রাসী এবং জঙ্গিদের ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল। যে পরিস্থিতি আজ দাঁড়িয়েছে, তার সবটাই আগের ঘটনার ধারাবাহিকতা।
কিন্তু সরকার প্রথম থেকে বিশেষ করে পুলিশ বাহিনীকে সক্রিয় করতে ব্যর্থ হয়েছে। সংস্কার নিয়ে বিভিন্ন ধরনের কথাবার্তার আড়ালে জনগণের নিরাপত্তার বিষয়টি সব সময় এড়িয়ে যাওয়া হয়েছে।
এখন নির্বাচনের আগে প্রায় দেড় বছরের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির সংকট কীভাবে কাটানো সম্ভব? একটি ঘটনা ঘটার পর আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে নিয়োজিত ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা নানা কথার ফুলঝুরি শোনান, কিন্তু কিছুদিন পর পরিস্থিতি পরিবর্তনের কোনো লক্ষণ দেখা যায় না।
নির্বাচন যেন কোনোভাবেই বাধাগ্রস্ত না হয়, সেটি নিশ্চিত করতে অন্তর্বর্তী সরকার এবং নির্বাচন কমিশনকে শুধু আশ্বাস নয়, বরং কঠোর ও দৃশ্যমান পদক্ষেপ দেখাতে হবে। এখন দরকার দ্রুত বিচার এবং দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি। এই হামলার তদন্ত এবং অপরাধীদের দ্রুত গ্রেপ্তার নিশ্চিত করে জনগণের মধ্যে আস্থা ফিরিয়ে আনাটাই এখন সরকারের জন্য প্রধান চ্যালেঞ্জ। নির্বাচন কমিশনের দায়িত্ব হলো, একটি শঙ্কামুক্ত পরিবেশ তৈরি করে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়াকে এগিয়ে নেওয়া। এই পরিস্থিতিতে নিরাপত্তাই এখন নির্বাচনের প্রধান পূর্বশর্ত।

গাছ লাগানো ভালো। প্রতিবছর ৫ জুন বিশ্ব পরিবেশ দিবস উপলক্ষে নানা দেশেই আজকাল গাছ রোপণের রেকর্ড হচ্ছে। কিন্তু এভাবে গাছ রোপণ কি আসলেই জলবায়ু পরিবর্তন ঠেকানোর জন্য যথেষ্ট? এতে কি গ্রীষ্মকালের প্রচণ্ড গরম সহনীয় পর্যায়ে আনা সম্ভব।
২১ এপ্রিল ২০২৪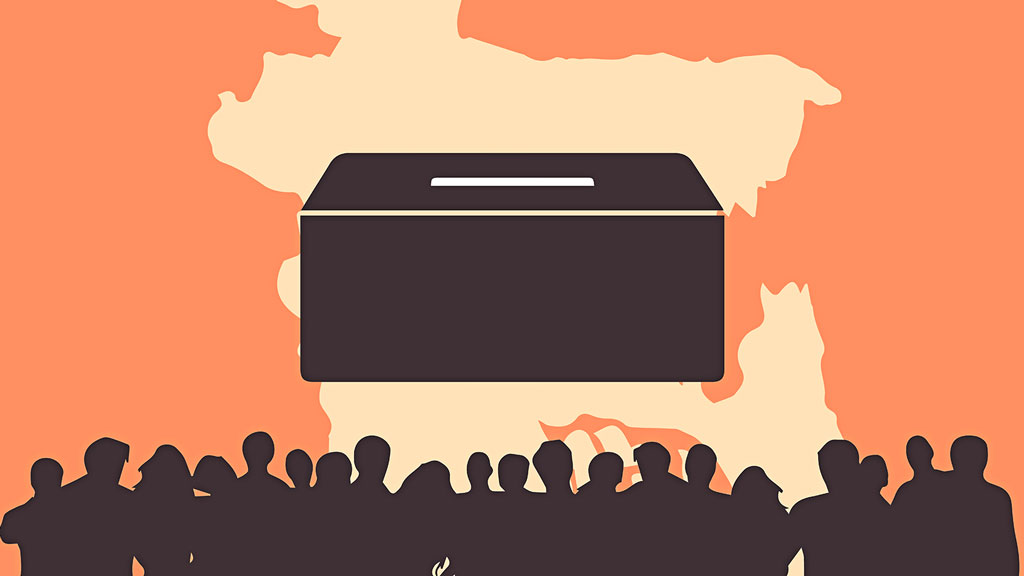
বাংলাদেশ আবারও একটি সংবেদনশীল সময় অতিক্রম করছে। সামনে জাতীয় নির্বাচন—যা শুধু ক্ষমতা পরিবর্তনের আনুষ্ঠানিক প্রক্রিয়া নয়; বরং রাষ্ট্রের গণতান্ত্রিক যাত্রার একটি গুরুত্বপূর্ণ বাঁক। এই নির্বাচন ঘিরে জনগণের প্রত্যাশা যেমন আছে, তেমনি রয়েছে গভীর উদ্বেগও।
১১ ঘণ্টা আগে
শুরুটা ছিল বেশ আশাজাগানিয়া। বিধি অনুযায়ী আমাদের দেশে মন্ত্রিসভার সদস্যদের কী বেতন বা সম্মানী এবং ভাতা ও সুবিধাদি এক্ষণে জানা নেই। যুগের সঙ্গে তাল মিলিয়েই নিশ্চয় তা নির্ধারণ করা হয়েছে। মন্ত্রী ছাড়া যাঁরা সংসদ সদস্য, তাঁদের বেলায়ও একই কথা; মোটা অঙ্কের বেতন-ভাতা এবং বলতে গেলে অবাধ সুযোগ-সুবিধা আছে বলেই
১১ ঘণ্টা আগে
বিজয়ের মাস চলছে। বাঙালি জাতির হাজার বছরের শৌর্যবীর্য ও বীরত্বের এক অবিস্মরণীয় গৌরবময় দিনটি ছিল গতকাল। ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর সঙ্গে দীর্ঘ ৯ মাসের রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ শেষে বাঙালি জাতির শ্রেষ্ঠতম অর্জন ‘বিজয়’। এদিন বাঙালির আত্মপরিচয় লাভের দিন।
১১ ঘণ্টা আগে