উন্নয়ন সংস্থার কর্মীদের অধিকার নিয়ে কে ভাবে?
উন্নয়ন সংস্থার কর্মীদের অধিকার নিয়ে কে ভাবে?
তাপস বড়ুয়া

অধিকার-কর্মীদের অধিকার নিয়ে সাধারণত কেউ কথা বলেন না। বিভিন্ন ক্ষেত্রের মানুষের অধিকার নিয়ে যারা সভা-সেমিনার, মানববন্ধন করে বেড়ান, তাঁরাও তাঁদের সহকর্মীদের অধিকার নিয়ে কথা বলেন না। এ বিষয়ে কোনো সভা-সেমিনার হয় না। লাখ লাখ মানুষ যে সেক্টরে কাজ করেন, তাঁদের ভালোমন্দের ইস্যু নিয়ে কথা হয় না কেন? কারণ, সে কথা বলতে গেলে দায়টা সভা-সেমিনার যারা করে বেড়ান, এই খাতের সেই সব হেভিওয়েটদের নিজের কাঁধেও এসে পড়ে।
বলছি দেশি-বিদেশি ও আন্তর্জাতিক উন্নয়ন প্রতিষ্ঠানের কর্মীদের কথা। করোনার দুটো বছর তাঁদের কেমন গেল? তাঁদের নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ তাঁদের পাশে কতটা দাঁড়িয়েছে—এসব কথা ভাববার দরকার আছে। ভাবার দরকার আছে, সুশীল সমাজ কেন এই খাতে কর্মরত মানুষের অধিকার নিয়ে মোটামুটি নীরব। কারণ সম্ভবত এই যে, এসব প্রতিষ্ঠানের সাথে সুশীল সমাজের বড় মানুষদের নিবিড় যোগাযোগ রয়েছে। এদের আয়োজিত সভা-সেমিনারেই সুশীল সমাজের লোকজন কথাবার্তা বলেন।
পঞ্চাশ বছর ধরে একটা খাত বিকশিত হয়েছে। লাখ লাখ মানুষ কাজ করছেন সেখানে। এই খাতের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান কত কত মানুষের ভালো-মন্দ নিয়ে গবেষণা করে। অথচ এই খাতে কাজ করা মানুষেরা কেমন আছেন—এটা নিয়ে কোনো ভালো গবেষণা চোখে পড়ে না।
কর্মীর সুযোগ-সুবিধাকে গুরুত্ব না দেওয়ার সম্ভাব্য কারণ
একসময় এনজিওগুলো নিজেরা পরিস্থিতি বা সমস্যা বিশ্লেষণ করত। এই বিশ্লেষণের ভিত্তিতে প্রকল্প প্রস্তাব তৈরি করত। তারপর সেই প্রস্তাবে কোন দাতা সংস্থা বা সহনীয় ভাষায় উন্নয়ন সহযোগী অর্থায়ন করতে চায়, সেটা খুঁজে বের করত। তার মানে সমস্যা চিহ্নিতকরণ ও তার ভিত্তিতে স্থানীয়ভাবে মানানসই কর্মসূচি এখানেই ডিজাইন করা হতো। সেটার সাথে যিনি একমত হতেন, তিনি অর্থায়ন করতেন।
এখন ঘটনা উল্টো। অধিকাংশ ক্ষেত্রে দাতা সংস্থা তাদের অগ্রাধিকারের ওপর ভিত্তি করে নিজেরাই নিজেদের উদ্যোগে প্রকল্প তৈরি করে। তারপর সাধারণত সেই দেশি কোন কনসালট্যান্সি ফার্ম সেটি বাস্তবায়নের ঠিকাদারি নেয় অনেকটা মধ্যস্বত্বভোগীর মতো। তারা নিজেদের বিভিন্ন নামে অভিহিত করে। তার মধ্যে ফান্ড ম্যানেজার, ফ্যাসিলিটি ম্যানেজার ইত্যাদি আছে। যা হোক, তারা তখন আগে থেকে কাজের গণ্ডি নির্দিষ্ট করে তার মধ্যে কিছু কাজ করার জন্য সাব-কন্ট্রাক্ট দেয়। এনজিওগুলো প্রতিযোগিতামূলক কর্মপরিকল্পনা ও বাজেট দাখিল করে প্রতিযোগিতার ভিত্তিতে কাজটি পায়। অধিকাংশ ক্ষেত্রে এখন এটাই নিয়ম হয়ে গেছে।
এখানেই প্রশ্নটা ওঠে। এই যে প্রতিযোগিতার মাধ্যমে কাজ পাওয়ার প্রক্রিয়া, সেখানে প্রতিযোগিতামূলক দর দিতে গিয়ে এনজিওগুলো কি তাদের কর্মীদের বেতন-ভাতা ও অন্য সুবিধাদির জায়গাটাতে ছাড় দিচ্ছে। এই অভিযোগ আমরা তৈরি পোশাক খাতের শিল্প উদ্যোক্তাদের বিরুদ্ধে শুনি। তারা প্রতিযোগিতামূলক দামে বিশ্ববাজারে পণ্য সরবরাহ করতে গিয়ে যে জায়গাটাতে খরচ কমায়, সেটা হচ্ছে শ্রমিকের বেতন ও অন্যান্য সুবিধাদি।
এনজিও খাত মানুষের অধিকার নিয়ে কাজ করে। তাদের কর্মীরাও যে মানুষ, এটা তারা মনে রাখলে এই কাজটি তাদের করার কথা না। উন্নয়ন সহযোগীদেরও কাজ দেওয়ার সময় প্রকল্পের বা প্রতিষ্ঠানের কর্মীরা, যারা কাজটি করবেন, তাদের অধিকার নিশ্চিত করেই কাজটি দেওয়া উচিত। এর বাইরে, সামন্তবাদী মনোভাব এবং কর্মীকে যত কম দিয়ে যত খাটিয়ে নেওয়া যায়, সেই চেষ্টা অনেক এনজিও প্রধানের মধ্যে ব্যাপকভাবে দেখা যায়।
খাত অলাভজনক হলেও কর্মীরা স্বেচ্ছাসেবী নয়
প্রয়োজনের তুলনায় কমসংখ্যক কর্মী দিয়ে বেশি পরিমাণ কাজ তুলে নিতে গিয়ে এনজিওকর্মীদের কর্মঘণ্টার ঠিকঠিকানা থাকে না। সপ্তাহে সাড়ে ৩৭ ঘণ্টার কাজ কখনো-কখনো ৫৫ বা ৬০ ঘণ্টায় গিয়ে দাঁড়ায়, যা নিশ্চিতভাবে শ্রমবিষয়ক জাতীয় ও আন্তর্জাতিক আইন ও নীতিমালাসমূহের ব্যত্যয়।
খাতটি অলাভজনক। তাই বলে কর্মীরা স্বেচ্ছাসেবী তা তো নয়। এসব প্রতিষ্ঠানে কাজ করা তো পেশা। মানুষ অন্য প্রতিষ্ঠানে যেমন বেতনের বিনিময়ে কাজ করে, এখানেও তাই। এত বড় একটা খাত দাঁড়িয়ে গেল। কিন্তু এই খাতে এমপ্লয়মেন্টের কোন সুনির্দিষ্ট নীতিমালা দাঁড়াল না কেন, সেটা দেখতে হবে। বছরের পর বছর চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ এখন এই খাতের নতুন ট্রেন্ড। এথিক্যাল ট্রেড নিয়ে যারা কাজ করে, তারা কমার্শিয়াল খাতেই এটার ঘোরবিরোধী। কারণ, এর মাধ্যমে কর্মীকে বিভিন্ন বেনিফিট থেকে ঠকানো হয়। অথচ উন্নয়ন নিয়ে কাজ করা প্রতিষ্ঠানে এই আনএথিক্যাল চর্চাই নিয়ম হয়ে দাঁড়িয়ে গেছে।
সমস্যা হলো, আমরা অ্যাক্টিভিজম ও প্রফেশনালিজমকে গুলিয়ে ফেলি। সেটা নিয়োগদাতাও; নিয়োগকৃত কর্মীও। আপনি বেতনের বিনিময়ে কাজ করেন এটা আপনার পেশা। কাজটা ভালো করে করবেন সেটা কাজের প্রতি সততা। অ্যাকটিভিস্ট না হয়েও সেটা করা যায়। কিন্তু একজন অ্যাকটিভিস্ট এই কর্মদায়িত্বের বাইরে গিয়েও সমাজের জন্য কাজ করেন। সমাজ পরিবর্তনে অবদান রাখেন। একজন ব্যক্তি একসঙ্গে পেশাদার এনজিও কর্মী ও অ্যাকটিভিস্ট হতে পারেন। কিন্তু হতেই হবে তেমন কোনো কথা নেই। একজন ব্যক্তি এর যেকোনো একটিও হতে পারেন। এবং দুটোর মাঝখানের সূক্ষ্ম রেখাটা যদি নিয়োগদাতা এবং কর্মী—দুজনই খেয়াল রাখেন, তাহলে সেটা সবার জন্য ভালো। বিশেষত নিয়োগকারী দিক থেকে স্বেচ্ছাশ্রম দাবির ঘটনা কম ঘটবে। খাত স্বেচ্ছাসেবী হলেও যে লোকটি কাজ করছে, সে পেশা হিসেবে এটাকে নিয়েছে। আর তাঁর নিয়োগটি হয়েছে চুক্তির অধীনে।
মানুষকে নিয়মিত কর্মী হিসেবে নিয়োগ না দিয়ে বারবার চুক্তি ভিত্তিতে নিয়োগ দেওয়া আইন ও নীতিবিরোধী। অথচ দেশীয় এনজিও তো বটেই জাতিসংঘের কোনো কোনো প্রতিষ্ঠানও এই চর্চা চালিয়ে যাচ্ছে বছরের পর বছর। সেখানে বার্ষিক চুক্তিতে নিয়োগ হয়। বছরের পর বছর চাকরির একই গ্রেড ও বেতনের একই ধাপে এই চুক্তি নবায়ন করা হয়।
করোনার সময় দেশি-বিদেশি নির্বিশেষে অধিকার নিয়ে সোচ্চার প্রতিষ্ঠানগুলো নিজেদের কর্মীদের অধিকার ভায়োলেট করে গেছে। পাঁচ বছরের প্রকল্প দুই বছর পর টাকা দেওয়া বন্ধ করেছে বড় দাতা সংস্থা এবং বিভিন্ন এনজিওকর্মীরা চাকরি হারিয়ে মানবেতর জীবনযাপন করছেন এমন উদাহরণ রয়েছে। মানবাধিকার নিশ্চিতের জন্য বিভিন্ন ক্ষেত্রে যারা আইন বদলের জন্য অ্যাডভোকেসি করে, তারা চুক্তির আইনগত ফাঁকফোকর ব্যবহার করে নিজের কর্মীকে কতটা কম দেওয়া যায় সেই সুযোগটা নিয়েছে।
করোনার ধাক্কা: একটি বাস্তব উদাহরণ
একটি নামডাকওয়ালা বিদেশি প্রতিষ্ঠানের একটি বাস্তব উদাহরণ দেওয়া যাক। একজন কর্মী সেখানে একটি উন্নয়ন প্রকল্পের কাজে যোগ দেন ২০১৬ সালে। প্রতিষ্ঠানের নিয়ম অনুযায়ী তিনি প্রভিডেন্ট ফান্ড, গ্র্যাচুইটি ইত্যাদি সুবিধা পেতেন। দুই বছর পর অফিস তাঁকে জানায়, আপনার কন্ট্রাক্টের ধরনটা বদলানোর সিদ্ধান্ত হয়েছে। আপনার পদ ও কর্মদায়িত্ব একই থাকবে। টাকাপয়সা, সুযোগ-সুবিধা, যা পাচ্ছেন তার সবই পাবেন। কিন্তু স্টাফ কন্ট্রাক্ট থেকে আপনাকে কনসালটেন্সি কন্ট্রাক্টে নেওয়া হবে। বার্ষিক মোট প্রাপ্য একই থাকলেও সেটাকে দিন হিসেবে ভাঙা হবে এবং প্রতি মাসে যত দিন কাজ করবেন, তত দিনের টাকা পাবেন।
সেই প্রকল্পেই একজন সরকারি কর্মকর্তা লিয়েন নিয়ে কাজ করছিলেন। তাঁর ক্ষেত্রে আবার এটা করা হলো না। কারণ, তাহলে পদ ও কর্মদায়িত্ব একই রেখে কন্ট্রাক্টের ধরন পরিবর্তনের যৌক্তিকতা নিয়ে সরকারি কর্তৃপক্ষ প্রশ্ন তুলতে পারেন, যার আসলেই কোনো জবাব নেই।
তারপর এল করোনা। স্টাফ কন্ট্রাক্ট থাকলে কর্মীটির আয় আগের মতোই থাকত। কিন্তু নতুন চুক্তিতে যেহেতু দিন হিসেবে পেমেন্ট করার সুযোগ আছে, তাকে বলা হলো এখন আপনি অর্ধেকসংখ্যক দিন কাজ করেন। ফলে তার মাসিক আয় গেল অর্ধেক হয়ে। হঠাৎ আয় অর্ধেক হয়ে যাওয়া মানুষের কষ্ট এই প্রতিষ্ঠানগুলো বুঝতে চায় না।
বলে রাখা ভালো, ওই কর্মীটি যে প্রকল্পে কাজ করছিলেন, করোনার কারণে সেই প্রকল্পের তহবিল নিয়ে কিন্তু কোনো সমস্যা হয়নি। পাঁচ বছরের তহবিল আগেই চলে এসেছিল। সুতরাং কর্মীকে অর্ধেক বেকার রাখার সিদ্ধান্ত একান্তই তাদের।
কিছু প্রস্তাব
এই সমস্যা দিন দিন বাড়ছে। সুতরাং এটা থেকে বেরিয়ে আসার জন্য নিচের প্রস্তাবগুলো বিবেচনায় নেওয়া যেতে পারে—
প্রস্তাব–১: দেশের এনজিও খাতের কর্মীদের বেতন-ভাতাসহ চাকরি সম্পর্কিত সুযোগ-সুবিধার সার্বিক চিত্র তুলে ধরার জন্য একটি কমপ্রিহেনসিভ গবেষণা করা হোক। গবেষণার ফলাফল জনসমক্ষে প্রকাশ করা হোক। এই কাজ সরকার, দাতাগোষ্ঠী এবং এনজিওগুলো যৌথভাবে করতে পারে।
প্রস্তাব–২: এনজিও খাতের কর্মীদের বেতন-ভাতা ও সুবিধাদির ন্যূনতম মানদণ্ড নির্ধারণ করা হোক। সরকার, এনজিও, সুশীল সমাজ, এমপ্লয়মেন্ট বিষয়ক বিশেষজ্ঞ, শ্রম আইন বিশেষজ্ঞ, উন্নয়ন সহযোগী প্রতিষ্ঠানগুলো এই প্রক্রিয়ায় যুক্ত হোক। কার্যক্রম ও প্রকল্প পরিচালনার ক্ষেত্রে এই ন্যূনতম সুবিধাদি নিশ্চিত করা বাধ্যতামূলক করা হোক এনজিও ও উন্নয়ন সহযোগী সবার জন্য।
প্রস্তাব–৩: একই প্রতিষ্ঠানে বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মীদের মধ্যে বেতন ও অন্যান্য সুবিধাদির বৈষম্য দূর করা হোক। সর্বোচ্চ বেতন যিনি পান, আর সর্বনিম্ন বেতন যিনি পান এই দুজনের বেতন ও সুবিধাদির একটা সর্বোচ্চ অনুপাত নির্ধারণ করা হোক। একইভাবে অনুপাত নির্দিষ্ট করে দেওয়া হোক প্রতিষ্ঠানের সব ধাপের কর্মীদের জন্যও। অন্তত এক ধাপ থেকে অন্য ধাপে পার্থক্য সর্বোচ্চ কত শতাংশ হতে পারে, সর্বনিম্ন কত শতাংশ হতে পারে, সেটা নির্দিষ্ট করে দেওয়া হোক।
প্রস্তাব–৪: একই সঙ্গে ছোট-বড়, স্থানীয়-জাতীয়, বার্ষিক বাজেট, মোট জনবল—এসবের ভিত্তিতে এনজিওগুলোর স্তরবিন্যাস করে কর্মী নিয়োগ কাঠামোর মধ্যে সমন্বয় করা হোক। বেতন কাঠামোর একটা গাইডলাইন নির্ধারণ করা হোক। ফ্লেক্সিবিলিটি থাক; কিন্তু একটা বৃহত্তর নীতিমালার মধ্যে থেকে।
প্রস্তাব–৫: এনজিও কর্মীদের জন্য বাধ্যতামূলক পেনশন ব্যবস্থা চালু করা হোক। নিয়োগকারী তাঁর কর্মীকে এই সুবিধা ছাড়া নিয়োগ দিতে পারবেন না, এমন বিধান করা হোক। তাহলে তাঁরা দাতাদের কাছে প্রকল্প প্রস্তাব দেওয়ার সময় বাজেটে এটা অন্তর্ভুক্ত করেই দেবেন। সবাই যদি এটা অন্তর্ভুক্ত করে প্রতিযোগিতায় নামেন, তাহলে সেটা সার্বিক প্রতিযোগিতায় প্রভাব ফেলবে না। কিন্তু কর্মীর একটা আর্থিক নিরাপত্তা তৈরি হবে।

অধিকার-কর্মীদের অধিকার নিয়ে সাধারণত কেউ কথা বলেন না। বিভিন্ন ক্ষেত্রের মানুষের অধিকার নিয়ে যারা সভা-সেমিনার, মানববন্ধন করে বেড়ান, তাঁরাও তাঁদের সহকর্মীদের অধিকার নিয়ে কথা বলেন না। এ বিষয়ে কোনো সভা-সেমিনার হয় না। লাখ লাখ মানুষ যে সেক্টরে কাজ করেন, তাঁদের ভালোমন্দের ইস্যু নিয়ে কথা হয় না কেন? কারণ, সে কথা বলতে গেলে দায়টা সভা-সেমিনার যারা করে বেড়ান, এই খাতের সেই সব হেভিওয়েটদের নিজের কাঁধেও এসে পড়ে।
বলছি দেশি-বিদেশি ও আন্তর্জাতিক উন্নয়ন প্রতিষ্ঠানের কর্মীদের কথা। করোনার দুটো বছর তাঁদের কেমন গেল? তাঁদের নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ তাঁদের পাশে কতটা দাঁড়িয়েছে—এসব কথা ভাববার দরকার আছে। ভাবার দরকার আছে, সুশীল সমাজ কেন এই খাতে কর্মরত মানুষের অধিকার নিয়ে মোটামুটি নীরব। কারণ সম্ভবত এই যে, এসব প্রতিষ্ঠানের সাথে সুশীল সমাজের বড় মানুষদের নিবিড় যোগাযোগ রয়েছে। এদের আয়োজিত সভা-সেমিনারেই সুশীল সমাজের লোকজন কথাবার্তা বলেন।
পঞ্চাশ বছর ধরে একটা খাত বিকশিত হয়েছে। লাখ লাখ মানুষ কাজ করছেন সেখানে। এই খাতের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান কত কত মানুষের ভালো-মন্দ নিয়ে গবেষণা করে। অথচ এই খাতে কাজ করা মানুষেরা কেমন আছেন—এটা নিয়ে কোনো ভালো গবেষণা চোখে পড়ে না।
কর্মীর সুযোগ-সুবিধাকে গুরুত্ব না দেওয়ার সম্ভাব্য কারণ
একসময় এনজিওগুলো নিজেরা পরিস্থিতি বা সমস্যা বিশ্লেষণ করত। এই বিশ্লেষণের ভিত্তিতে প্রকল্প প্রস্তাব তৈরি করত। তারপর সেই প্রস্তাবে কোন দাতা সংস্থা বা সহনীয় ভাষায় উন্নয়ন সহযোগী অর্থায়ন করতে চায়, সেটা খুঁজে বের করত। তার মানে সমস্যা চিহ্নিতকরণ ও তার ভিত্তিতে স্থানীয়ভাবে মানানসই কর্মসূচি এখানেই ডিজাইন করা হতো। সেটার সাথে যিনি একমত হতেন, তিনি অর্থায়ন করতেন।
এখন ঘটনা উল্টো। অধিকাংশ ক্ষেত্রে দাতা সংস্থা তাদের অগ্রাধিকারের ওপর ভিত্তি করে নিজেরাই নিজেদের উদ্যোগে প্রকল্প তৈরি করে। তারপর সাধারণত সেই দেশি কোন কনসালট্যান্সি ফার্ম সেটি বাস্তবায়নের ঠিকাদারি নেয় অনেকটা মধ্যস্বত্বভোগীর মতো। তারা নিজেদের বিভিন্ন নামে অভিহিত করে। তার মধ্যে ফান্ড ম্যানেজার, ফ্যাসিলিটি ম্যানেজার ইত্যাদি আছে। যা হোক, তারা তখন আগে থেকে কাজের গণ্ডি নির্দিষ্ট করে তার মধ্যে কিছু কাজ করার জন্য সাব-কন্ট্রাক্ট দেয়। এনজিওগুলো প্রতিযোগিতামূলক কর্মপরিকল্পনা ও বাজেট দাখিল করে প্রতিযোগিতার ভিত্তিতে কাজটি পায়। অধিকাংশ ক্ষেত্রে এখন এটাই নিয়ম হয়ে গেছে।
এখানেই প্রশ্নটা ওঠে। এই যে প্রতিযোগিতার মাধ্যমে কাজ পাওয়ার প্রক্রিয়া, সেখানে প্রতিযোগিতামূলক দর দিতে গিয়ে এনজিওগুলো কি তাদের কর্মীদের বেতন-ভাতা ও অন্য সুবিধাদির জায়গাটাতে ছাড় দিচ্ছে। এই অভিযোগ আমরা তৈরি পোশাক খাতের শিল্প উদ্যোক্তাদের বিরুদ্ধে শুনি। তারা প্রতিযোগিতামূলক দামে বিশ্ববাজারে পণ্য সরবরাহ করতে গিয়ে যে জায়গাটাতে খরচ কমায়, সেটা হচ্ছে শ্রমিকের বেতন ও অন্যান্য সুবিধাদি।
এনজিও খাত মানুষের অধিকার নিয়ে কাজ করে। তাদের কর্মীরাও যে মানুষ, এটা তারা মনে রাখলে এই কাজটি তাদের করার কথা না। উন্নয়ন সহযোগীদেরও কাজ দেওয়ার সময় প্রকল্পের বা প্রতিষ্ঠানের কর্মীরা, যারা কাজটি করবেন, তাদের অধিকার নিশ্চিত করেই কাজটি দেওয়া উচিত। এর বাইরে, সামন্তবাদী মনোভাব এবং কর্মীকে যত কম দিয়ে যত খাটিয়ে নেওয়া যায়, সেই চেষ্টা অনেক এনজিও প্রধানের মধ্যে ব্যাপকভাবে দেখা যায়।
খাত অলাভজনক হলেও কর্মীরা স্বেচ্ছাসেবী নয়
প্রয়োজনের তুলনায় কমসংখ্যক কর্মী দিয়ে বেশি পরিমাণ কাজ তুলে নিতে গিয়ে এনজিওকর্মীদের কর্মঘণ্টার ঠিকঠিকানা থাকে না। সপ্তাহে সাড়ে ৩৭ ঘণ্টার কাজ কখনো-কখনো ৫৫ বা ৬০ ঘণ্টায় গিয়ে দাঁড়ায়, যা নিশ্চিতভাবে শ্রমবিষয়ক জাতীয় ও আন্তর্জাতিক আইন ও নীতিমালাসমূহের ব্যত্যয়।
খাতটি অলাভজনক। তাই বলে কর্মীরা স্বেচ্ছাসেবী তা তো নয়। এসব প্রতিষ্ঠানে কাজ করা তো পেশা। মানুষ অন্য প্রতিষ্ঠানে যেমন বেতনের বিনিময়ে কাজ করে, এখানেও তাই। এত বড় একটা খাত দাঁড়িয়ে গেল। কিন্তু এই খাতে এমপ্লয়মেন্টের কোন সুনির্দিষ্ট নীতিমালা দাঁড়াল না কেন, সেটা দেখতে হবে। বছরের পর বছর চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ এখন এই খাতের নতুন ট্রেন্ড। এথিক্যাল ট্রেড নিয়ে যারা কাজ করে, তারা কমার্শিয়াল খাতেই এটার ঘোরবিরোধী। কারণ, এর মাধ্যমে কর্মীকে বিভিন্ন বেনিফিট থেকে ঠকানো হয়। অথচ উন্নয়ন নিয়ে কাজ করা প্রতিষ্ঠানে এই আনএথিক্যাল চর্চাই নিয়ম হয়ে দাঁড়িয়ে গেছে।
সমস্যা হলো, আমরা অ্যাক্টিভিজম ও প্রফেশনালিজমকে গুলিয়ে ফেলি। সেটা নিয়োগদাতাও; নিয়োগকৃত কর্মীও। আপনি বেতনের বিনিময়ে কাজ করেন এটা আপনার পেশা। কাজটা ভালো করে করবেন সেটা কাজের প্রতি সততা। অ্যাকটিভিস্ট না হয়েও সেটা করা যায়। কিন্তু একজন অ্যাকটিভিস্ট এই কর্মদায়িত্বের বাইরে গিয়েও সমাজের জন্য কাজ করেন। সমাজ পরিবর্তনে অবদান রাখেন। একজন ব্যক্তি একসঙ্গে পেশাদার এনজিও কর্মী ও অ্যাকটিভিস্ট হতে পারেন। কিন্তু হতেই হবে তেমন কোনো কথা নেই। একজন ব্যক্তি এর যেকোনো একটিও হতে পারেন। এবং দুটোর মাঝখানের সূক্ষ্ম রেখাটা যদি নিয়োগদাতা এবং কর্মী—দুজনই খেয়াল রাখেন, তাহলে সেটা সবার জন্য ভালো। বিশেষত নিয়োগকারী দিক থেকে স্বেচ্ছাশ্রম দাবির ঘটনা কম ঘটবে। খাত স্বেচ্ছাসেবী হলেও যে লোকটি কাজ করছে, সে পেশা হিসেবে এটাকে নিয়েছে। আর তাঁর নিয়োগটি হয়েছে চুক্তির অধীনে।
মানুষকে নিয়মিত কর্মী হিসেবে নিয়োগ না দিয়ে বারবার চুক্তি ভিত্তিতে নিয়োগ দেওয়া আইন ও নীতিবিরোধী। অথচ দেশীয় এনজিও তো বটেই জাতিসংঘের কোনো কোনো প্রতিষ্ঠানও এই চর্চা চালিয়ে যাচ্ছে বছরের পর বছর। সেখানে বার্ষিক চুক্তিতে নিয়োগ হয়। বছরের পর বছর চাকরির একই গ্রেড ও বেতনের একই ধাপে এই চুক্তি নবায়ন করা হয়।
করোনার সময় দেশি-বিদেশি নির্বিশেষে অধিকার নিয়ে সোচ্চার প্রতিষ্ঠানগুলো নিজেদের কর্মীদের অধিকার ভায়োলেট করে গেছে। পাঁচ বছরের প্রকল্প দুই বছর পর টাকা দেওয়া বন্ধ করেছে বড় দাতা সংস্থা এবং বিভিন্ন এনজিওকর্মীরা চাকরি হারিয়ে মানবেতর জীবনযাপন করছেন এমন উদাহরণ রয়েছে। মানবাধিকার নিশ্চিতের জন্য বিভিন্ন ক্ষেত্রে যারা আইন বদলের জন্য অ্যাডভোকেসি করে, তারা চুক্তির আইনগত ফাঁকফোকর ব্যবহার করে নিজের কর্মীকে কতটা কম দেওয়া যায় সেই সুযোগটা নিয়েছে।
করোনার ধাক্কা: একটি বাস্তব উদাহরণ
একটি নামডাকওয়ালা বিদেশি প্রতিষ্ঠানের একটি বাস্তব উদাহরণ দেওয়া যাক। একজন কর্মী সেখানে একটি উন্নয়ন প্রকল্পের কাজে যোগ দেন ২০১৬ সালে। প্রতিষ্ঠানের নিয়ম অনুযায়ী তিনি প্রভিডেন্ট ফান্ড, গ্র্যাচুইটি ইত্যাদি সুবিধা পেতেন। দুই বছর পর অফিস তাঁকে জানায়, আপনার কন্ট্রাক্টের ধরনটা বদলানোর সিদ্ধান্ত হয়েছে। আপনার পদ ও কর্মদায়িত্ব একই থাকবে। টাকাপয়সা, সুযোগ-সুবিধা, যা পাচ্ছেন তার সবই পাবেন। কিন্তু স্টাফ কন্ট্রাক্ট থেকে আপনাকে কনসালটেন্সি কন্ট্রাক্টে নেওয়া হবে। বার্ষিক মোট প্রাপ্য একই থাকলেও সেটাকে দিন হিসেবে ভাঙা হবে এবং প্রতি মাসে যত দিন কাজ করবেন, তত দিনের টাকা পাবেন।
সেই প্রকল্পেই একজন সরকারি কর্মকর্তা লিয়েন নিয়ে কাজ করছিলেন। তাঁর ক্ষেত্রে আবার এটা করা হলো না। কারণ, তাহলে পদ ও কর্মদায়িত্ব একই রেখে কন্ট্রাক্টের ধরন পরিবর্তনের যৌক্তিকতা নিয়ে সরকারি কর্তৃপক্ষ প্রশ্ন তুলতে পারেন, যার আসলেই কোনো জবাব নেই।
তারপর এল করোনা। স্টাফ কন্ট্রাক্ট থাকলে কর্মীটির আয় আগের মতোই থাকত। কিন্তু নতুন চুক্তিতে যেহেতু দিন হিসেবে পেমেন্ট করার সুযোগ আছে, তাকে বলা হলো এখন আপনি অর্ধেকসংখ্যক দিন কাজ করেন। ফলে তার মাসিক আয় গেল অর্ধেক হয়ে। হঠাৎ আয় অর্ধেক হয়ে যাওয়া মানুষের কষ্ট এই প্রতিষ্ঠানগুলো বুঝতে চায় না।
বলে রাখা ভালো, ওই কর্মীটি যে প্রকল্পে কাজ করছিলেন, করোনার কারণে সেই প্রকল্পের তহবিল নিয়ে কিন্তু কোনো সমস্যা হয়নি। পাঁচ বছরের তহবিল আগেই চলে এসেছিল। সুতরাং কর্মীকে অর্ধেক বেকার রাখার সিদ্ধান্ত একান্তই তাদের।
কিছু প্রস্তাব
এই সমস্যা দিন দিন বাড়ছে। সুতরাং এটা থেকে বেরিয়ে আসার জন্য নিচের প্রস্তাবগুলো বিবেচনায় নেওয়া যেতে পারে—
প্রস্তাব–১: দেশের এনজিও খাতের কর্মীদের বেতন-ভাতাসহ চাকরি সম্পর্কিত সুযোগ-সুবিধার সার্বিক চিত্র তুলে ধরার জন্য একটি কমপ্রিহেনসিভ গবেষণা করা হোক। গবেষণার ফলাফল জনসমক্ষে প্রকাশ করা হোক। এই কাজ সরকার, দাতাগোষ্ঠী এবং এনজিওগুলো যৌথভাবে করতে পারে।
প্রস্তাব–২: এনজিও খাতের কর্মীদের বেতন-ভাতা ও সুবিধাদির ন্যূনতম মানদণ্ড নির্ধারণ করা হোক। সরকার, এনজিও, সুশীল সমাজ, এমপ্লয়মেন্ট বিষয়ক বিশেষজ্ঞ, শ্রম আইন বিশেষজ্ঞ, উন্নয়ন সহযোগী প্রতিষ্ঠানগুলো এই প্রক্রিয়ায় যুক্ত হোক। কার্যক্রম ও প্রকল্প পরিচালনার ক্ষেত্রে এই ন্যূনতম সুবিধাদি নিশ্চিত করা বাধ্যতামূলক করা হোক এনজিও ও উন্নয়ন সহযোগী সবার জন্য।
প্রস্তাব–৩: একই প্রতিষ্ঠানে বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মীদের মধ্যে বেতন ও অন্যান্য সুবিধাদির বৈষম্য দূর করা হোক। সর্বোচ্চ বেতন যিনি পান, আর সর্বনিম্ন বেতন যিনি পান এই দুজনের বেতন ও সুবিধাদির একটা সর্বোচ্চ অনুপাত নির্ধারণ করা হোক। একইভাবে অনুপাত নির্দিষ্ট করে দেওয়া হোক প্রতিষ্ঠানের সব ধাপের কর্মীদের জন্যও। অন্তত এক ধাপ থেকে অন্য ধাপে পার্থক্য সর্বোচ্চ কত শতাংশ হতে পারে, সর্বনিম্ন কত শতাংশ হতে পারে, সেটা নির্দিষ্ট করে দেওয়া হোক।
প্রস্তাব–৪: একই সঙ্গে ছোট-বড়, স্থানীয়-জাতীয়, বার্ষিক বাজেট, মোট জনবল—এসবের ভিত্তিতে এনজিওগুলোর স্তরবিন্যাস করে কর্মী নিয়োগ কাঠামোর মধ্যে সমন্বয় করা হোক। বেতন কাঠামোর একটা গাইডলাইন নির্ধারণ করা হোক। ফ্লেক্সিবিলিটি থাক; কিন্তু একটা বৃহত্তর নীতিমালার মধ্যে থেকে।
প্রস্তাব–৫: এনজিও কর্মীদের জন্য বাধ্যতামূলক পেনশন ব্যবস্থা চালু করা হোক। নিয়োগকারী তাঁর কর্মীকে এই সুবিধা ছাড়া নিয়োগ দিতে পারবেন না, এমন বিধান করা হোক। তাহলে তাঁরা দাতাদের কাছে প্রকল্প প্রস্তাব দেওয়ার সময় বাজেটে এটা অন্তর্ভুক্ত করেই দেবেন। সবাই যদি এটা অন্তর্ভুক্ত করে প্রতিযোগিতায় নামেন, তাহলে সেটা সার্বিক প্রতিযোগিতায় প্রভাব ফেলবে না। কিন্তু কর্মীর একটা আর্থিক নিরাপত্তা তৈরি হবে।
সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন
সম্পর্কিত
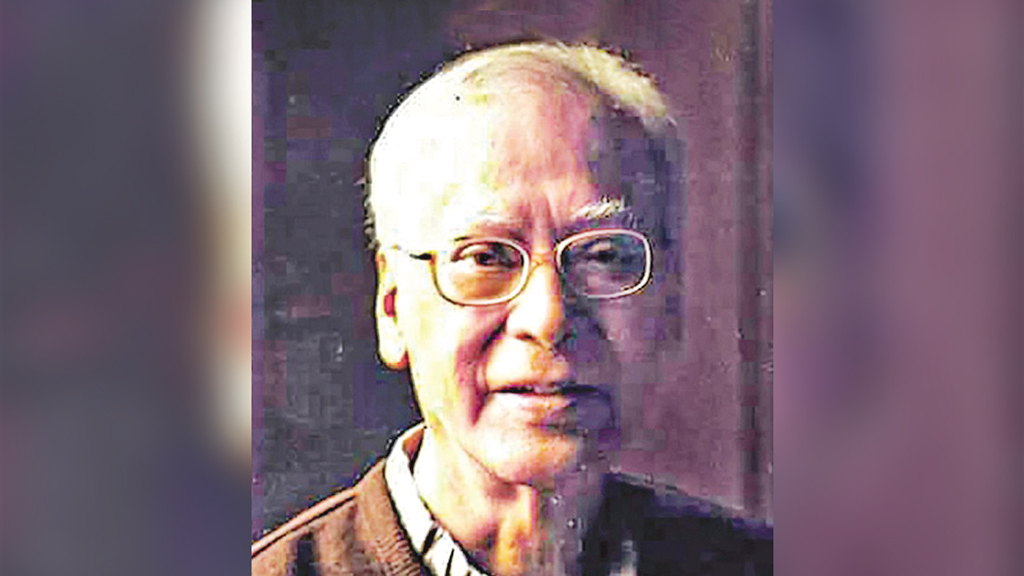
‘দারিদ্র্য নিরসন’ কথাটায় তিনি বিশ্বাস করতেন না
আমার শিক্ষক, শিক্ষাগুরু ও পথপ্রদর্শক প্রফেসর মো. আনিসুর রহমান ৫ জানুয়ারি মৃত্যুবরণ করেছেন (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)। ১৯৭২ সালে আমি যখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে মাস্টার্স ফাইনাল ইয়ারের ছাত্র, তখন বাংলাদেশের প্রথম পরিকল্পনা কমিশনের সদস্য প্রফেসর আনিসুর রহমান তাঁর কমিশনের কর্মপরিধি কিছুটা...
১২ ঘণ্টা আগে
উচ্চমূল্যেও গ্যাস পাওয়ার নিশ্চয়তা আছে কি
গাজীপুরের কোনাবাড়ীতে প্লাস্টিক পণ্য উৎপাদনকারী ৪০ বছরের পুরোনো একটি কারখানা অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ ঘোষণা করেছে কর্তৃপক্ষ। গত বৃহস্পতিবার সকালে কারখানার মূল ফটকে বন্ধ ঘোষণার নোটিশ সাঁটিয়ে দেওয়া হয়। কারখানাটির নাম পলিকন লিমিটেড।
১২ ঘণ্টা আগে
সাধারণ নাগরিকের সংবিধান ভাবনা
বাংলাদেশে সংবিধানের কী দরকার? কার জন্য দরকার? নাগরিকের জন্য, নাকি রাজনৈতিক দলগুলোর জন্য? যে সংবিধানে দেশের একজন মানুষের জনগণ থেকে নাগরিক হওয়ার সুযোগ নেই, সেই সংবিধান দিয়ে আমরা কী করব? আমরা যখন জনগণ থেকে নাগরিক হতে যাই, তখন নাগরিক অধিকার সামনে আসে। সংবিধানে আমাদের নাগরিক অধিকার আদৌ আছে? উত্তর জানতে..
১২ ঘণ্টা আগে
রূপা হকের মন্তব্য ও পরিবারতন্ত্র
ব্রিটিশ লেবার পার্টির সংসদ সদস্য রূপা হক একটি ব্রিটিশ প্রতিনিধিদলের সদস্য হিসেবে বাংলাদেশে এসেছেন। বিটিএমএর এক আয়োজনে অন্য অনেক বিষয়ের সঙ্গে তিনি পরিবারতন্ত্রের ব্যাপারে কিছু কথা বলেছেন। আজকের পত্রিকায় প্রকাশিত খবর থেকে জানা যায়, তিনি বলেছেন, একজন নেতার কন্যা, আরেকজন নেতার বেগম এবং তাঁদের...
১৩ ঘণ্টা আগে



