বিভুরঞ্জন সরকার

২৬ মার্চ বাংলাদেশের ৫৫তম স্বাধীনতা দিবস। দিনটি এক গৌরবময় অধ্যায়ের স্মারক, যেখানে বাঙালি জাতির বীরত্ব, সাহসিকতা, আত্মত্যাগ ও বিজয়ের অমর কাহিনি জড়িয়ে আছে। একাত্তরের রক্তঝরা পথ বেয়ে যে স্বাধীনতার সূর্য উদিত হয়েছিল, তা আজ পাঁচ দশকের বেশি সময় ধরে দেশের অগ্রযাত্রাকে আলোকিত করছে। স্বাধীনতার সেই প্রথম প্রহরে যে স্বপ্ন মানুষ দেখেছিল—একটি গণতান্ত্রিক, বৈষম্যহীন ও উন্নত বাংলাদেশের—তা কতটা বাস্তবায়িত হয়েছে? বীর মুক্তিযোদ্ধাদের আত্মত্যাগ, সাধারণ মানুষের অবিস্মরণীয় সাহসিকতা আর ঐক্যের শক্তিতে অর্জিত এই বিজয় আজও আমাদের পথ দেখায়। সঙ্গে সঙ্গে এই প্রশ্নও সামনে আসে, স্বাধীনতার ৫৫ বছরে আমরা একাত্তরের কাঙ্ক্ষিত বাংলাদেশ গড়তে কতটা সফল হয়েছি?
মুক্তিযুদ্ধ কেবল একাত্তরের নয়, তার শিকড় বহু গভীরে। সমাজের প্রতিটি স্তরে এই যুদ্ধের অভিঘাত পড়েছিল। তখনকার সমাজ যেমন শত্রু ও মিত্রে দ্বিধাবিভক্ত হয়েছিল, তেমনি শত্রুদের মধ্যেও ছিল ভিন্ন স্তর—লোভের কারণে যাওয়া, ভয় থেকে যোগ দেওয়া কিংবা সুবিধাবাদের পথ বেছে নেওয়া। একইভাবে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষেও ছিল বহুস্তরবিশিষ্ট মানুষ—আদর্শবাদী বিপ্লবী, বঞ্চনার শিকার সাধারণ মানুষ, উচ্চাভিলাষী মধ্যবিত্ত কিংবা প্রাণভয়ে প্রতিরোধে নামা সংগ্রামী। তাই মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসকে একরৈখিকভাবে দেখা কখনোই যথেষ্ট নয়; এটি ছিল বহুমাত্রিক রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক টানাপোড়েনের ফল।
একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত বাঙালির রাজনৈতিক নেতৃত্ব দর-কষাকষির মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। পাকিস্তানের রাষ্ট্রকাঠামোর মধ্যে থেকেই অধিকারের সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়ার কৌশল গ্রহণ করেছিল আওয়ামী লীগ। ছয় দফা ছিল তারই প্রকাশ। ছয় দফার মধ্যে যেমন পূর্ব পাকিস্তানের অর্থনৈতিক মুক্তির দাবি ছিল, তেমনি এটি পুরোপুরি স্বাধীনতার পরিকল্পনা ছিল না। কারণ আওয়ামী লীগের নেতৃত্ব মূলত মধ্যবিত্তের হাতে ছিল, যারা ক্ষমতার ভাগাভাগির কাঠামোর মধ্যেই নিজেদের ভবিষ্যৎ খুঁজছিল। ফলে ছয় দফা ঘোষণা, আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা, উনসত্তরের গণ-অভ্যুত্থান, আইয়ুব খানের পতন, ইয়াহিয়া-ভুট্টোর উত্থান এবং সত্তরের নির্বাচন—এ সবকিছুর পরও আওয়ামী লীগ পাকিস্তান কাঠামোর মধ্যেই ক্ষমতা গ্রহণের জন্য দর-কষাকষির পথে অগ্রসর হয়েছিল।
কিন্তু ১৯৭০-এর নির্বাচনের নিরঙ্কুশ বিজয় এই দর-কষাকষির পথকে সংকুচিত করে ফেলে। সংসদে সংখ্যাগরিষ্ঠতা পাওয়ার পর আওয়ামী লীগ যখন কেন্দ্রীয় শাসনে অধিষ্ঠিত হতে চাইল, তখন পশ্চিম পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠীর মনে হলো, এটি পূর্ব পাকিস্তানের আস্তে আস্তে বেরিয়ে যাওয়ার প্রথম ধাপ। অতএব, তারা ছলচাতুরীর আশ্রয় নিল, বারবার আলোচনার নামে কালক্ষেপণ করল এবং শেষে ২৫ মার্চের কালরাত্রিতে গণহত্যা শুরু করল।
২৫ মার্চের পর যখন যুদ্ধ বাস্তবতা হয়ে দেখা দিল, তখন দর-কষাকষির জায়গা শেষ হয়ে গেল। স্বাধীনতা হয়ে উঠল একমাত্র বাস্তবতা। সেই যুদ্ধের আহ্বান এল রাজপথ থেকে, জনতার মুখ থেকে। ‘বীর বাঙালি অস্ত্র ধর, বাংলাদেশ স্বাধীন কর’—এই স্লোগান তখন ছাপিয়ে গেল ছয় দফাকে, যা আসলে ছয় দফার কাঠামো ভেঙে এক দফায় রূপান্তরিত হয়েছিল।
ওই সময়কার আরেকটি বাস্তবতা ছিল বামপন্থীদের দুর্বল সংগঠন। তারা জাতিগত মুক্তির প্রশ্নে নেতৃত্ব দিতে পারেনি। তাদের আন্দোলন গোপন ছিল, শুধু পুলিশের কাছেই নয়, সাধারণ মানুষের কাছেও। তাদের চাওয়া ছিল শ্রেণিসংগ্রামের মাধ্যমে মুক্তি, কিন্তু বাস্তবতা হয়ে উঠল জাতীয় মুক্তির লড়াই। ফলে তাদের স্লোগান ‘ভোটের আগে ভাত চাই, নইলে এবার রক্ষা নাই’ কিংবা ‘অন্ন চাই, বস্ত্র চাই, বাঁচার মতো বাঁচতে চাই’ সাধারণ মানুষ গ্রহণ করলেও রাজনৈতিক নেতৃত্বের ক্ষেত্রে তারা প্রধান শক্তি হয়ে উঠতে পারেনি।
এই পরিস্থিতিতে শেখ মুজিব হয়ে উঠলেন এক প্রতীকী নেতা। তিনি প্রত্যক্ষভাবে মুক্তিযুদ্ধের নেতৃত্ব দেননি, কিন্তু যুদ্ধ চলাকালে সর্বত্র তাঁর উপস্থিতি অনুভূত হয়েছে। কারণ পাকিস্তানিদের বিরুদ্ধে দর-কষাকষির মঞ্চে তিনি ছিলেন সবচেয়ে বড় কণ্ঠস্বর এবং জাতিসত্তার দাবিতে তিনিই ছিলেন সবচেয়ে গ্রহণযোগ্য নেতা। বামপন্থীরা বিকল্প নেতৃত্ব গড়ে তুলতে পারেনি বলেই মুজিবের নেতৃত্ব প্রশ্নাতীত থেকে গেছে।
শেখ মুজিবের এই নেতৃত্ব মধ্যবিত্তকে আশ্বস্ত করেছিল। কারণ, মধ্যবিত্ত শ্রেণির রাজনৈতিক কৌশল সব সময়ই একটা নিরাপত্তাবোধের ওপর নির্ভর করে। তারা সর্বদা চায় এমন এক নেতা, যিনি তাদের স্বার্থ রক্ষা করবেন এবং একেবারে চরম বিপ্লবের দিকে নিয়ে যাবেন না। শেখ মুজিবের নেতৃত্ব সেই নিরাপত্তাবোধ দিয়েছিল। বামপন্থীরা যেখানে ‘শ্রেণিসংগ্রাম’-এর কথা বলছিল, সেখানে আওয়ামী লীগ বিদ্যমান বাস্তব রাজনৈতিক কাঠামোর মধ্যেই পরিবর্তন আনতে চেয়েছিল।
মুক্তিযুদ্ধের সময়ের বিভাজন শুধু রাজনৈতিক ছিল না, সামাজিকও ছিল। সুবিধাভোগীরা পাকিস্তানের পক্ষে ছিল, কারণ তারা জানত নতুন রাষ্ট্রে তাদের স্বার্থ হারাবে। আবার অনেকে নিরুপায় হয়েও রাজাকারে নাম লিখিয়েছে। আর সাধারণ কৃষক, শ্রমিক এবং গরিব মানুষের চাওয়া ছিল কেবল মুক্তি—শোষণমুক্ত জীবন।
কিন্তু যুদ্ধ শেষ হওয়ার পর দেখা গেল, যে শ্রেণিটি সবচেয়ে বেশি রক্ত দিল, তারাই সবচেয়ে বেশি বঞ্চিত হলো। ক্ষমতা ফিরে গেল সেই মধ্যবিত্ত শ্রেণির হাতেই। যুদ্ধে যাদের ভূমিকা সীমিত ছিল, তারাই রাষ্ট্রশক্তির কেন্দ্রবিন্দুতে চলে এল। কৃষক-শ্রমিকেরা স্বপ্ন দেখেছিল যে স্বাধীন দেশে তারা ‘খাদ্য, বস্ত্র, শিক্ষা, চিকিৎসা, বাসস্থান’ পাবে, কিন্তু বাস্তবতা তাদের জন্য অনেক কঠিন হয়ে দাঁড়াল।
আওয়ামী লীগ মূলত মধ্যবিত্তের রাজনৈতিক দল ছিল, ফলে স্বাধীনতার পর ক্ষমতার কাঠামো গড়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে শ্রমজীবী মানুষের প্রত্যাশা পূরণের জায়গাটি সংকুচিত হয়ে এল। ফলে স্বাধীনতার প্রথম কয়েক বছরেই সমাজে নতুন করে বিভাজন তৈরি হলো—একদিকে ক্ষমতাসীন মধ্যবিত্ত ও তাদের সুবিধাভোগী অংশ, অন্যদিকে মুক্তিযোদ্ধা, কৃষক, শ্রমিক ও সাধারণ মানুষ।
মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসকে বুঝতে হলে শুধু যুদ্ধকালীন শত্রু-মিত্র বিভাজন নয়, বরং যুদ্ধের অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বও বুঝতে হবে। কেন শেখ মুজিব সরাসরি নেতৃত্ব না দিয়েও প্রধান নেতা হয়ে রইলেন? কেন বামপন্থীরা বিকল্প শক্তি হয়ে উঠতে পারল না? কেন যুদ্ধের পরে কৃষক-শ্রমিকেরা আবার শোষিত হলো? এসব প্রশ্নের উত্তর আমাদের খুঁজতে হবে।
মুক্তিযুদ্ধের প্রকৃত বিজয় তখনই আসবে, যখন স্বাধীনতার চেতনা শুধু রাজনৈতিক স্বাধীনতায় সীমাবদ্ধ থাকবে না, বরং সামাজিক ও অর্থনৈতিক মুক্তির প্রশ্নেও কার্যকর হবে। শেখ মুজিব বজ্রকণ্ঠে বলেছিলেন, ‘এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।’ ৯ মাসের অসম যুদ্ধে আমরা স্বাধীন হয়েছি কিন্তু মুক্তি পাইনি। ইতিহাস আমাদের মনে করিয়ে দেয়, মুক্তিযুদ্ধ শুধু একাত্তরের যুদ্ধ ছিল না, এটি একটি চলমান লড়াই। আমাদের কাজ এই লড়াইকে সামনের দিকে এগিয়ে নেওয়া, যাতে যে স্বপ্নে লাখো মানুষ জীবন দিয়েছিল, সেই স্বপ্ন সত্যি হয়ে ওঠে।
লেখক: জ্যেষ্ঠ সহকারী সম্পাদক, আজকের পত্রিকা

২৬ মার্চ বাংলাদেশের ৫৫তম স্বাধীনতা দিবস। দিনটি এক গৌরবময় অধ্যায়ের স্মারক, যেখানে বাঙালি জাতির বীরত্ব, সাহসিকতা, আত্মত্যাগ ও বিজয়ের অমর কাহিনি জড়িয়ে আছে। একাত্তরের রক্তঝরা পথ বেয়ে যে স্বাধীনতার সূর্য উদিত হয়েছিল, তা আজ পাঁচ দশকের বেশি সময় ধরে দেশের অগ্রযাত্রাকে আলোকিত করছে। স্বাধীনতার সেই প্রথম প্রহরে যে স্বপ্ন মানুষ দেখেছিল—একটি গণতান্ত্রিক, বৈষম্যহীন ও উন্নত বাংলাদেশের—তা কতটা বাস্তবায়িত হয়েছে? বীর মুক্তিযোদ্ধাদের আত্মত্যাগ, সাধারণ মানুষের অবিস্মরণীয় সাহসিকতা আর ঐক্যের শক্তিতে অর্জিত এই বিজয় আজও আমাদের পথ দেখায়। সঙ্গে সঙ্গে এই প্রশ্নও সামনে আসে, স্বাধীনতার ৫৫ বছরে আমরা একাত্তরের কাঙ্ক্ষিত বাংলাদেশ গড়তে কতটা সফল হয়েছি?
মুক্তিযুদ্ধ কেবল একাত্তরের নয়, তার শিকড় বহু গভীরে। সমাজের প্রতিটি স্তরে এই যুদ্ধের অভিঘাত পড়েছিল। তখনকার সমাজ যেমন শত্রু ও মিত্রে দ্বিধাবিভক্ত হয়েছিল, তেমনি শত্রুদের মধ্যেও ছিল ভিন্ন স্তর—লোভের কারণে যাওয়া, ভয় থেকে যোগ দেওয়া কিংবা সুবিধাবাদের পথ বেছে নেওয়া। একইভাবে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষেও ছিল বহুস্তরবিশিষ্ট মানুষ—আদর্শবাদী বিপ্লবী, বঞ্চনার শিকার সাধারণ মানুষ, উচ্চাভিলাষী মধ্যবিত্ত কিংবা প্রাণভয়ে প্রতিরোধে নামা সংগ্রামী। তাই মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসকে একরৈখিকভাবে দেখা কখনোই যথেষ্ট নয়; এটি ছিল বহুমাত্রিক রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক টানাপোড়েনের ফল।
একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত বাঙালির রাজনৈতিক নেতৃত্ব দর-কষাকষির মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। পাকিস্তানের রাষ্ট্রকাঠামোর মধ্যে থেকেই অধিকারের সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়ার কৌশল গ্রহণ করেছিল আওয়ামী লীগ। ছয় দফা ছিল তারই প্রকাশ। ছয় দফার মধ্যে যেমন পূর্ব পাকিস্তানের অর্থনৈতিক মুক্তির দাবি ছিল, তেমনি এটি পুরোপুরি স্বাধীনতার পরিকল্পনা ছিল না। কারণ আওয়ামী লীগের নেতৃত্ব মূলত মধ্যবিত্তের হাতে ছিল, যারা ক্ষমতার ভাগাভাগির কাঠামোর মধ্যেই নিজেদের ভবিষ্যৎ খুঁজছিল। ফলে ছয় দফা ঘোষণা, আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা, উনসত্তরের গণ-অভ্যুত্থান, আইয়ুব খানের পতন, ইয়াহিয়া-ভুট্টোর উত্থান এবং সত্তরের নির্বাচন—এ সবকিছুর পরও আওয়ামী লীগ পাকিস্তান কাঠামোর মধ্যেই ক্ষমতা গ্রহণের জন্য দর-কষাকষির পথে অগ্রসর হয়েছিল।
কিন্তু ১৯৭০-এর নির্বাচনের নিরঙ্কুশ বিজয় এই দর-কষাকষির পথকে সংকুচিত করে ফেলে। সংসদে সংখ্যাগরিষ্ঠতা পাওয়ার পর আওয়ামী লীগ যখন কেন্দ্রীয় শাসনে অধিষ্ঠিত হতে চাইল, তখন পশ্চিম পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠীর মনে হলো, এটি পূর্ব পাকিস্তানের আস্তে আস্তে বেরিয়ে যাওয়ার প্রথম ধাপ। অতএব, তারা ছলচাতুরীর আশ্রয় নিল, বারবার আলোচনার নামে কালক্ষেপণ করল এবং শেষে ২৫ মার্চের কালরাত্রিতে গণহত্যা শুরু করল।
২৫ মার্চের পর যখন যুদ্ধ বাস্তবতা হয়ে দেখা দিল, তখন দর-কষাকষির জায়গা শেষ হয়ে গেল। স্বাধীনতা হয়ে উঠল একমাত্র বাস্তবতা। সেই যুদ্ধের আহ্বান এল রাজপথ থেকে, জনতার মুখ থেকে। ‘বীর বাঙালি অস্ত্র ধর, বাংলাদেশ স্বাধীন কর’—এই স্লোগান তখন ছাপিয়ে গেল ছয় দফাকে, যা আসলে ছয় দফার কাঠামো ভেঙে এক দফায় রূপান্তরিত হয়েছিল।
ওই সময়কার আরেকটি বাস্তবতা ছিল বামপন্থীদের দুর্বল সংগঠন। তারা জাতিগত মুক্তির প্রশ্নে নেতৃত্ব দিতে পারেনি। তাদের আন্দোলন গোপন ছিল, শুধু পুলিশের কাছেই নয়, সাধারণ মানুষের কাছেও। তাদের চাওয়া ছিল শ্রেণিসংগ্রামের মাধ্যমে মুক্তি, কিন্তু বাস্তবতা হয়ে উঠল জাতীয় মুক্তির লড়াই। ফলে তাদের স্লোগান ‘ভোটের আগে ভাত চাই, নইলে এবার রক্ষা নাই’ কিংবা ‘অন্ন চাই, বস্ত্র চাই, বাঁচার মতো বাঁচতে চাই’ সাধারণ মানুষ গ্রহণ করলেও রাজনৈতিক নেতৃত্বের ক্ষেত্রে তারা প্রধান শক্তি হয়ে উঠতে পারেনি।
এই পরিস্থিতিতে শেখ মুজিব হয়ে উঠলেন এক প্রতীকী নেতা। তিনি প্রত্যক্ষভাবে মুক্তিযুদ্ধের নেতৃত্ব দেননি, কিন্তু যুদ্ধ চলাকালে সর্বত্র তাঁর উপস্থিতি অনুভূত হয়েছে। কারণ পাকিস্তানিদের বিরুদ্ধে দর-কষাকষির মঞ্চে তিনি ছিলেন সবচেয়ে বড় কণ্ঠস্বর এবং জাতিসত্তার দাবিতে তিনিই ছিলেন সবচেয়ে গ্রহণযোগ্য নেতা। বামপন্থীরা বিকল্প নেতৃত্ব গড়ে তুলতে পারেনি বলেই মুজিবের নেতৃত্ব প্রশ্নাতীত থেকে গেছে।
শেখ মুজিবের এই নেতৃত্ব মধ্যবিত্তকে আশ্বস্ত করেছিল। কারণ, মধ্যবিত্ত শ্রেণির রাজনৈতিক কৌশল সব সময়ই একটা নিরাপত্তাবোধের ওপর নির্ভর করে। তারা সর্বদা চায় এমন এক নেতা, যিনি তাদের স্বার্থ রক্ষা করবেন এবং একেবারে চরম বিপ্লবের দিকে নিয়ে যাবেন না। শেখ মুজিবের নেতৃত্ব সেই নিরাপত্তাবোধ দিয়েছিল। বামপন্থীরা যেখানে ‘শ্রেণিসংগ্রাম’-এর কথা বলছিল, সেখানে আওয়ামী লীগ বিদ্যমান বাস্তব রাজনৈতিক কাঠামোর মধ্যেই পরিবর্তন আনতে চেয়েছিল।
মুক্তিযুদ্ধের সময়ের বিভাজন শুধু রাজনৈতিক ছিল না, সামাজিকও ছিল। সুবিধাভোগীরা পাকিস্তানের পক্ষে ছিল, কারণ তারা জানত নতুন রাষ্ট্রে তাদের স্বার্থ হারাবে। আবার অনেকে নিরুপায় হয়েও রাজাকারে নাম লিখিয়েছে। আর সাধারণ কৃষক, শ্রমিক এবং গরিব মানুষের চাওয়া ছিল কেবল মুক্তি—শোষণমুক্ত জীবন।
কিন্তু যুদ্ধ শেষ হওয়ার পর দেখা গেল, যে শ্রেণিটি সবচেয়ে বেশি রক্ত দিল, তারাই সবচেয়ে বেশি বঞ্চিত হলো। ক্ষমতা ফিরে গেল সেই মধ্যবিত্ত শ্রেণির হাতেই। যুদ্ধে যাদের ভূমিকা সীমিত ছিল, তারাই রাষ্ট্রশক্তির কেন্দ্রবিন্দুতে চলে এল। কৃষক-শ্রমিকেরা স্বপ্ন দেখেছিল যে স্বাধীন দেশে তারা ‘খাদ্য, বস্ত্র, শিক্ষা, চিকিৎসা, বাসস্থান’ পাবে, কিন্তু বাস্তবতা তাদের জন্য অনেক কঠিন হয়ে দাঁড়াল।
আওয়ামী লীগ মূলত মধ্যবিত্তের রাজনৈতিক দল ছিল, ফলে স্বাধীনতার পর ক্ষমতার কাঠামো গড়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে শ্রমজীবী মানুষের প্রত্যাশা পূরণের জায়গাটি সংকুচিত হয়ে এল। ফলে স্বাধীনতার প্রথম কয়েক বছরেই সমাজে নতুন করে বিভাজন তৈরি হলো—একদিকে ক্ষমতাসীন মধ্যবিত্ত ও তাদের সুবিধাভোগী অংশ, অন্যদিকে মুক্তিযোদ্ধা, কৃষক, শ্রমিক ও সাধারণ মানুষ।
মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসকে বুঝতে হলে শুধু যুদ্ধকালীন শত্রু-মিত্র বিভাজন নয়, বরং যুদ্ধের অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বও বুঝতে হবে। কেন শেখ মুজিব সরাসরি নেতৃত্ব না দিয়েও প্রধান নেতা হয়ে রইলেন? কেন বামপন্থীরা বিকল্প শক্তি হয়ে উঠতে পারল না? কেন যুদ্ধের পরে কৃষক-শ্রমিকেরা আবার শোষিত হলো? এসব প্রশ্নের উত্তর আমাদের খুঁজতে হবে।
মুক্তিযুদ্ধের প্রকৃত বিজয় তখনই আসবে, যখন স্বাধীনতার চেতনা শুধু রাজনৈতিক স্বাধীনতায় সীমাবদ্ধ থাকবে না, বরং সামাজিক ও অর্থনৈতিক মুক্তির প্রশ্নেও কার্যকর হবে। শেখ মুজিব বজ্রকণ্ঠে বলেছিলেন, ‘এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।’ ৯ মাসের অসম যুদ্ধে আমরা স্বাধীন হয়েছি কিন্তু মুক্তি পাইনি। ইতিহাস আমাদের মনে করিয়ে দেয়, মুক্তিযুদ্ধ শুধু একাত্তরের যুদ্ধ ছিল না, এটি একটি চলমান লড়াই। আমাদের কাজ এই লড়াইকে সামনের দিকে এগিয়ে নেওয়া, যাতে যে স্বপ্নে লাখো মানুষ জীবন দিয়েছিল, সেই স্বপ্ন সত্যি হয়ে ওঠে।
লেখক: জ্যেষ্ঠ সহকারী সম্পাদক, আজকের পত্রিকা

কয়েক দিন ধরেই সেনাবাহিনী নিয়ে গণমাধ্যমে বেশ আলোচনা হচ্ছে। নবগঠিত জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) দক্ষিণাঞ্চলের মুখ্য সংগঠক হাসনাত আবদুল্লাহ ও আমার বাংলাদেশ পার্টি (এবি পার্টি) নামক অপর একটি দলের সাধারণ সম্পাদক ব্যারিস্টার আসাদুজ্জামান...
১৪ ঘণ্টা আগে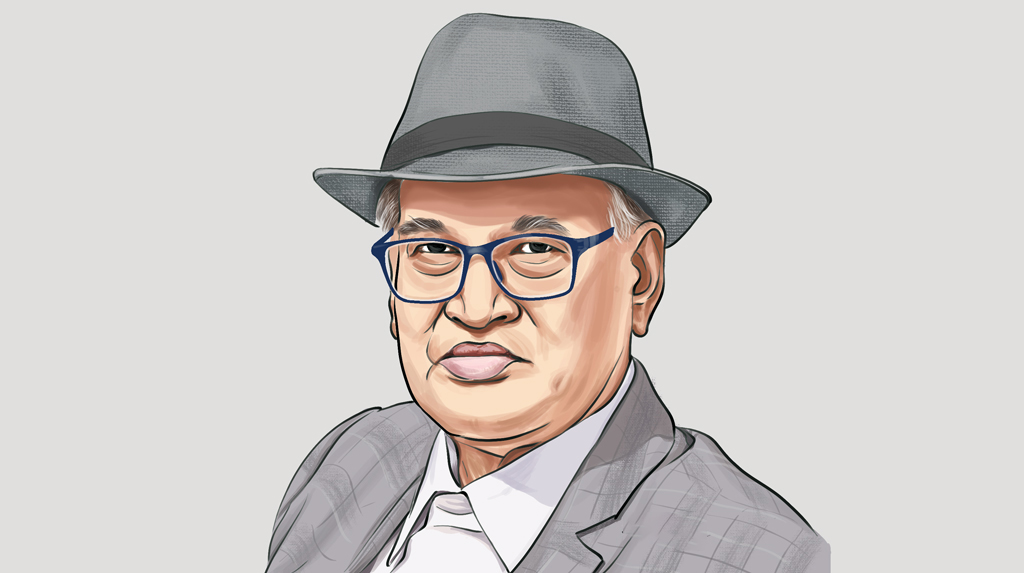
এখনই রাজনীতির মাঠের উত্তাপ বাড়াটা স্বাভাবিক ঘটনা। সম্ভাব্য নির্বাচনের সময় যত ঘনিয়ে আসবে, রাজনৈতিক দলগুলোর তৎপরতা যত বাড়তে থাকবে এবং রাজনীতির মাঠের উত্তাপ ততই বেশি করে অনুভূত হতে থাকবে। এখন সেটাই দেখা যাচ্ছে। তবে নির্বাচনের সময়সূচি...
১৫ ঘণ্টা আগে
আমরা সবাই পাপী; আপন পাপের বাটখারা দিয়ে অন্যের পাপ মাপি—কাজী নজরুল ইসলামের এই পঙ্ক্তিটি আমাদের সমাজের চিরন্তন বাস্তবতার নগ্ন প্রতিচিত্র। সময়ের পরিক্রমায় সভ্যতার অগ্রগতি হয়েছে, মানুষ বিজ্ঞানের চূড়ান্ত উৎকর্ষে পৌঁছেছে...
১৫ ঘণ্টা আগে
এসপি হতে পারেন তিনি। কিন্তু এ কথা তো সত্য, তিনি চলেন জনগণের করের টাকায়। যে দেশে বাস করেন, সে দেশের ইতিহাস-ঐতিহ্যকে অপমান করেও দিব্যি তিনি ব্রাহ্মণবাড়িয়ার এসপি হিসেবে দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছেন।
১৫ ঘণ্টা আগে