মানবর্দ্ধন পাল
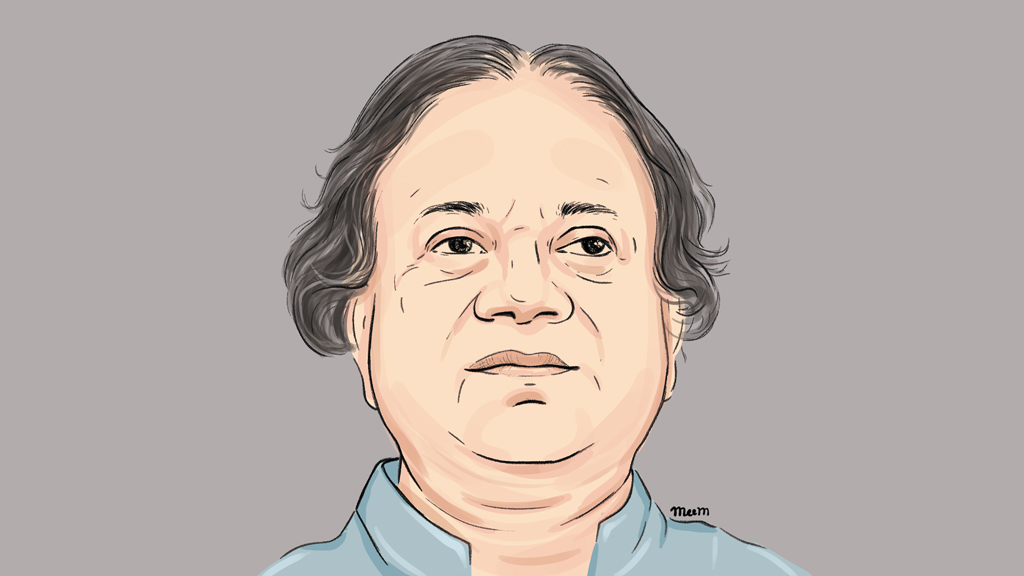
প্রবাদ আছে, বারো মাসে তেরো পার্বণের দেশ আমাদের। সীমিত সাধ্যের মধ্যেও আমরা সারা বছর উৎসবে মেতে থাকি। এসব উৎসবের মধ্যে কৃষি-সংস্কৃতিনির্ভর লৌকিক উৎসবের সংখ্যাই বেশি। পৌষপার্বণ তেমনই কৃষিনির্ভর লোকজ সাংস্কৃতিক উৎসব। প্রাচীনকাল থেকে বাংলার লোকজীবনে এই উৎসব পালিত হয়ে আসছে। নানা অঞ্চলে এর ভিন্ন ভিন্ন নাম-মকরসংক্রান্তি, মাঘ-বুড়, নবান্ন উৎসব, সাকরাইন, তিলুয়া-সংক্রান্তি, উত্তরায়ণ সংক্রান্তি ইত্যাদি। এসব নামেরও আছে লৌকিক ও জ্যোতিষী তাৎপর্য। মাসের এই শেষ দিনটিতে বাস্তুভিটা ও পূর্বপুরুষদের উদ্দেশে নৈবেদ্য নিবেদন করা হয়।
পৌষপার্বণ শীতকালীন উৎসব-ঋতু উৎসব, মূলত ভোগের অনুষ্ঠান। নানান লৌকিক ব্রত-আচার ও পূজা-অর্চনার মাধ্যমে প্রাচীনকালে পালিত হতো পৌষপার্বণ। গ্রামীণ মেলা, গরুদৌড়, মোরগ-লড়াই, গানবাজনা, যাত্রাপালা, কেচ্ছা-কীর্তন ও ঘুড়ি ওড়ানো হতো গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে। প্রবাদ আছে, ‘পান-পানি-পিঠা শীতের দিনে মিঠা’। বাংলায় রসনাবিলাসী পিঠার মৌসুম মূলত শীতকালে। অঘ্রান-পৌষ মাসে কৃষকের ঘরে আমন ধান উঠে গেলে কিছুদিন কিষান-কিষানির অবসর ও বিশ্রাম। তখন তাঁরা মেতে ওঠেন নানা উৎসব ও ভোজনবিলাসে। সেই সময়, পৌষ যায়, মাঘ আসে—শুরু হয় নতুন ধানের নবান্ন উৎসব।
নতুন ধানের চাল, চাল থেকে মিহি গুঁড়ি তৈরি, তা পায়েস-পিঠার মূল উপকরণ। এর সঙ্গে চাই তেল, গুড়, তিল, নারকেল, দুধ আরও কত-কী! এসব দিয়ে তৈরি বিচিত্র স্বাদ, আকৃতি ও নকশার পিঠা—পাটিসাপটা, চিতই, দুধপুলি, মালপোয়া, দুধচিতই, তেলের পিঠা, চুষিপিঠা, নকশিপিঠা, ভাপা, আলু মুগ ও বুটের পুলি। কোনোটা রসাল, কোনোটা মচমচে, কোনোটা গুড়ের রসে চুবানো, কোনোটা ঘন দুধে ডোবানো। সেসব রসনাবিলাসী পিঠার সম্ভার লোকজ সংস্কৃতি এখন অনেকটাই স্মৃতি, অধিকাংশই ইতিহাস-ঐতিহ্যের অংশ। এর পরিচয় পাওয়া যায় ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত ও সুনির্মল বসুর দুটি কবিতায়। তাতে পাই: ‘ঘোর জাঁক বাজে শাঁখ যত সব বামা।/কুটিছে তণ্ডুল সুখে করি ধামা ধামা/...পুলি সব উঠে গেল কিছু নাই ছাই।/নারকেল তেল গুড় ফের আনা চাই/...আলু তিল ক্ষীর নারিকেল আর/গড়িতেছে পিঠেপুলি অশেষ প্রকার।’ (পৌষপার্বণ, ঈশ্বর গুপ্ত)
সুনির্মল বসু ‘পৌষপার্বণ উৎসব’ কবিতায় লিখেছেন: ‘নলেন গুড়ের সৌরভে আজ/মশগুল যে ভিটে,/পিঠে পিঠে পিঠে।/ক্ষীর নারকেল লাগবে আরো?/নিয়ে যা হাত চিটে,/পিঠে পিঠে পিঠে।/কম খেলে আজ/হবে রে ভাই মেজাজটা খিটখিটে,/পিঠে পিঠে পিঠে।/...রসপুলি আর গোকুল-চসির/রস যে গিঁটে গিঁটে।’
পিঠা-পুলি-পায়েসের সেই দিন আর নেই! তা এখন স্থান করে নিয়েছে নগর-মহানগরের সুসজ্জিত আলো ঝলমলে পিঠাঘরে। রাজধানী তো বটেই, বিভাগীয় এবং জেলা শহরেও অগণিত পিঠাশপ বা পিঠাবিপণি। মা-খালাদের, নানি-দাদির মমতাময় পিঠা এখন তৈরি হচ্ছে বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানে, বিক্রি হচ্ছে বিপণিবিতানে। তিলের নাড়ু, নারকেলের নাড়ু, সাজের সন্দেশ—সবই এখন কিনতে পাওয়া যায় দোকানে এবং অনলাইনে। হাজার টাকার ভাপা পিঠাও বিক্রি হয় নরসিংদীর ওভারব্রিজের নিচে। গ্রামীণ সমাজের পিঠা-উৎসব একালে ঠাঁই নিয়েছে নগরের মিলনায়তন ও বিদ্যায়তনে। গ্রামগঞ্জের রাস্তার মোড়ে, ফুটপাতে এখন সান্ধ্যকালীন অস্থায়ী অসংখ্য পিঠার দোকান খেজুরের গুড়, ধনেপাতা আর সরিষার ভর্তার গন্ধে বিমোহিত। তবে স্বাস্থ্যবিধি কতটুকু পালিত হচ্ছে তা প্রশ্নবিদ্ধ।
ঐতিহ্যের এই বিবর্তন ও নবায়নের কথা ভাবলে রবীন্দ্রনাথকে মনে পড়ে। তিনি আধুনিক বাঙালির জীবনে অনেক উৎসবের উদ্গাতা। শান্তিনিকেতনের প্রাণকাড়া ঋতু-উৎসব পৌষমেলা তাঁরই সৃজন ও নবরূপায়ণ। তিনি মহাকবি হলেও ‘মহাকাব্য’ লেখেননি। তাতে জনৈক ‘মহাকবি’র ঈর্ষান্বিত ইঙ্গিতের জবাবে কাব্য করে তিনি বলেছেন: ‘আমি নাববো মহাকাব্য সংরচনে,/ছিল মনে।/বাজলো কখন তোমার কাঁকন/কিঙ্কিণীতে,/কল্পনাটি গেল ফাটি/হাজার গীতে।/মহাকাব্য সেই অভাব্য/দুর্ঘটনায়,/ছড়িয়ে আছে পায়ের কাছে/কানায় কানায়।’
শীতের ঐতিহ্যবাহী পিঠাও বোধকরি তেমনই ছড়িয়ে আছে পথেঘাটে, রাস্তার পাশে, গলির মোড়ে।
মানবর্দ্ধন পাল: অবসরপ্রাপ্ত কলেজশিক্ষক, গ্রন্থকার
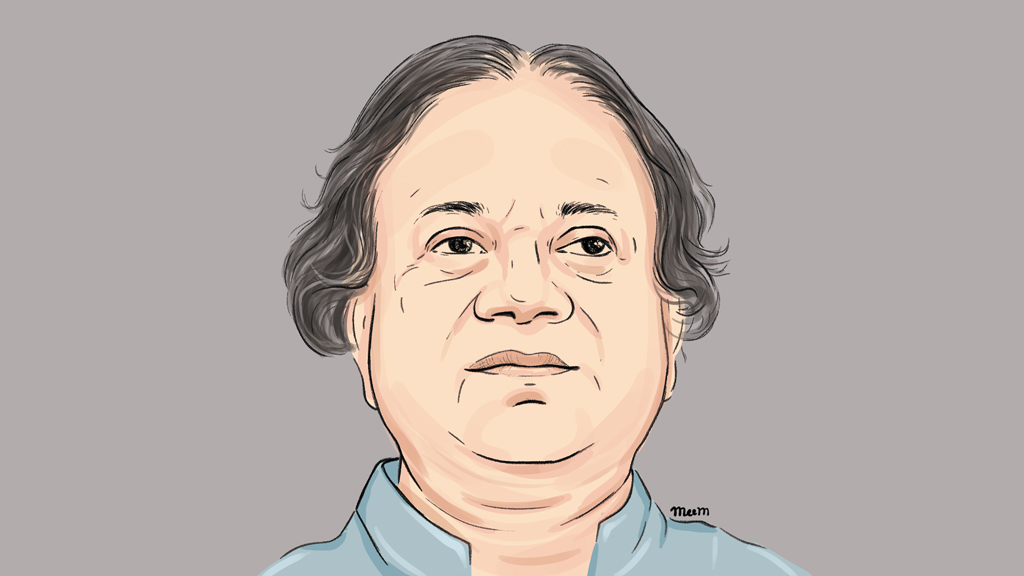
প্রবাদ আছে, বারো মাসে তেরো পার্বণের দেশ আমাদের। সীমিত সাধ্যের মধ্যেও আমরা সারা বছর উৎসবে মেতে থাকি। এসব উৎসবের মধ্যে কৃষি-সংস্কৃতিনির্ভর লৌকিক উৎসবের সংখ্যাই বেশি। পৌষপার্বণ তেমনই কৃষিনির্ভর লোকজ সাংস্কৃতিক উৎসব। প্রাচীনকাল থেকে বাংলার লোকজীবনে এই উৎসব পালিত হয়ে আসছে। নানা অঞ্চলে এর ভিন্ন ভিন্ন নাম-মকরসংক্রান্তি, মাঘ-বুড়, নবান্ন উৎসব, সাকরাইন, তিলুয়া-সংক্রান্তি, উত্তরায়ণ সংক্রান্তি ইত্যাদি। এসব নামেরও আছে লৌকিক ও জ্যোতিষী তাৎপর্য। মাসের এই শেষ দিনটিতে বাস্তুভিটা ও পূর্বপুরুষদের উদ্দেশে নৈবেদ্য নিবেদন করা হয়।
পৌষপার্বণ শীতকালীন উৎসব-ঋতু উৎসব, মূলত ভোগের অনুষ্ঠান। নানান লৌকিক ব্রত-আচার ও পূজা-অর্চনার মাধ্যমে প্রাচীনকালে পালিত হতো পৌষপার্বণ। গ্রামীণ মেলা, গরুদৌড়, মোরগ-লড়াই, গানবাজনা, যাত্রাপালা, কেচ্ছা-কীর্তন ও ঘুড়ি ওড়ানো হতো গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে। প্রবাদ আছে, ‘পান-পানি-পিঠা শীতের দিনে মিঠা’। বাংলায় রসনাবিলাসী পিঠার মৌসুম মূলত শীতকালে। অঘ্রান-পৌষ মাসে কৃষকের ঘরে আমন ধান উঠে গেলে কিছুদিন কিষান-কিষানির অবসর ও বিশ্রাম। তখন তাঁরা মেতে ওঠেন নানা উৎসব ও ভোজনবিলাসে। সেই সময়, পৌষ যায়, মাঘ আসে—শুরু হয় নতুন ধানের নবান্ন উৎসব।
নতুন ধানের চাল, চাল থেকে মিহি গুঁড়ি তৈরি, তা পায়েস-পিঠার মূল উপকরণ। এর সঙ্গে চাই তেল, গুড়, তিল, নারকেল, দুধ আরও কত-কী! এসব দিয়ে তৈরি বিচিত্র স্বাদ, আকৃতি ও নকশার পিঠা—পাটিসাপটা, চিতই, দুধপুলি, মালপোয়া, দুধচিতই, তেলের পিঠা, চুষিপিঠা, নকশিপিঠা, ভাপা, আলু মুগ ও বুটের পুলি। কোনোটা রসাল, কোনোটা মচমচে, কোনোটা গুড়ের রসে চুবানো, কোনোটা ঘন দুধে ডোবানো। সেসব রসনাবিলাসী পিঠার সম্ভার লোকজ সংস্কৃতি এখন অনেকটাই স্মৃতি, অধিকাংশই ইতিহাস-ঐতিহ্যের অংশ। এর পরিচয় পাওয়া যায় ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত ও সুনির্মল বসুর দুটি কবিতায়। তাতে পাই: ‘ঘোর জাঁক বাজে শাঁখ যত সব বামা।/কুটিছে তণ্ডুল সুখে করি ধামা ধামা/...পুলি সব উঠে গেল কিছু নাই ছাই।/নারকেল তেল গুড় ফের আনা চাই/...আলু তিল ক্ষীর নারিকেল আর/গড়িতেছে পিঠেপুলি অশেষ প্রকার।’ (পৌষপার্বণ, ঈশ্বর গুপ্ত)
সুনির্মল বসু ‘পৌষপার্বণ উৎসব’ কবিতায় লিখেছেন: ‘নলেন গুড়ের সৌরভে আজ/মশগুল যে ভিটে,/পিঠে পিঠে পিঠে।/ক্ষীর নারকেল লাগবে আরো?/নিয়ে যা হাত চিটে,/পিঠে পিঠে পিঠে।/কম খেলে আজ/হবে রে ভাই মেজাজটা খিটখিটে,/পিঠে পিঠে পিঠে।/...রসপুলি আর গোকুল-চসির/রস যে গিঁটে গিঁটে।’
পিঠা-পুলি-পায়েসের সেই দিন আর নেই! তা এখন স্থান করে নিয়েছে নগর-মহানগরের সুসজ্জিত আলো ঝলমলে পিঠাঘরে। রাজধানী তো বটেই, বিভাগীয় এবং জেলা শহরেও অগণিত পিঠাশপ বা পিঠাবিপণি। মা-খালাদের, নানি-দাদির মমতাময় পিঠা এখন তৈরি হচ্ছে বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানে, বিক্রি হচ্ছে বিপণিবিতানে। তিলের নাড়ু, নারকেলের নাড়ু, সাজের সন্দেশ—সবই এখন কিনতে পাওয়া যায় দোকানে এবং অনলাইনে। হাজার টাকার ভাপা পিঠাও বিক্রি হয় নরসিংদীর ওভারব্রিজের নিচে। গ্রামীণ সমাজের পিঠা-উৎসব একালে ঠাঁই নিয়েছে নগরের মিলনায়তন ও বিদ্যায়তনে। গ্রামগঞ্জের রাস্তার মোড়ে, ফুটপাতে এখন সান্ধ্যকালীন অস্থায়ী অসংখ্য পিঠার দোকান খেজুরের গুড়, ধনেপাতা আর সরিষার ভর্তার গন্ধে বিমোহিত। তবে স্বাস্থ্যবিধি কতটুকু পালিত হচ্ছে তা প্রশ্নবিদ্ধ।
ঐতিহ্যের এই বিবর্তন ও নবায়নের কথা ভাবলে রবীন্দ্রনাথকে মনে পড়ে। তিনি আধুনিক বাঙালির জীবনে অনেক উৎসবের উদ্গাতা। শান্তিনিকেতনের প্রাণকাড়া ঋতু-উৎসব পৌষমেলা তাঁরই সৃজন ও নবরূপায়ণ। তিনি মহাকবি হলেও ‘মহাকাব্য’ লেখেননি। তাতে জনৈক ‘মহাকবি’র ঈর্ষান্বিত ইঙ্গিতের জবাবে কাব্য করে তিনি বলেছেন: ‘আমি নাববো মহাকাব্য সংরচনে,/ছিল মনে।/বাজলো কখন তোমার কাঁকন/কিঙ্কিণীতে,/কল্পনাটি গেল ফাটি/হাজার গীতে।/মহাকাব্য সেই অভাব্য/দুর্ঘটনায়,/ছড়িয়ে আছে পায়ের কাছে/কানায় কানায়।’
শীতের ঐতিহ্যবাহী পিঠাও বোধকরি তেমনই ছড়িয়ে আছে পথেঘাটে, রাস্তার পাশে, গলির মোড়ে।
মানবর্দ্ধন পাল: অবসরপ্রাপ্ত কলেজশিক্ষক, গ্রন্থকার

ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের কুমিল্লা এলাকায় যাত্রীবাহী বাসে ডাকাতি বেড়েই চলছে। এ কারণে চালক ও যাত্রীদের কাছে আতঙ্কের নাম হয়ে উঠছে এই সড়ক। ডাকাতির শিকার বেশি হচ্ছেন প্রবাসফেরত লোকজন। ডাকাতেরা অস্ত্র ঠেকিয়ে লুট করে নিচ্ছে সর্বস্ব। আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর পরিচয়েও ঘটছে ডাকাতির ঘটনা।
০২ মার্চ ২০২৫
বিআরটিসির বাস দিয়ে চালু করা বিশেষায়িত বাস র্যাপিড ট্রানজিট (বিআরটি) লেনে অনুমতি না নিয়েই চলছে বেসরকারি কোম্পানির কিছু বাস। ঢুকে পড়ছে সিএনজিচালিত অটোরিকশা, ব্যাটারিচালিত অটোরিকশা। উল্টো পথে চলছে মোটরসাইকেল। অন্যদিকে বিআরটিসির মাত্র ১০টি বাস চলাচল করায় সোয়া চার হাজার কোটি টাকার এই প্রকল্প থেকে...
১৬ জানুয়ারি ২০২৫
গাজীপুর মহানগরের বোর্ডবাজার এলাকার ইসলামিক ইউনিভার্সিটি অব টেকনোলজির (আইইউটি) মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের শিক্ষার্থীরা পিকনিকে যাচ্ছিলেন শ্রীপুরের মাটির মায়া ইকো রিসোর্টে। ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়ক থেকে বাসগুলো গ্রামের সরু সড়কে ঢোকার পর বিদ্যুতের তারে জড়িয়ে যায় বিআরটিসির একটি দোতলা বাস...
২৪ নভেম্বর ২০২৪
ঝড়-জলোচ্ছ্বাস থেকে রক্ষায় সন্দ্বীপের ব্লক বেড়িবাঁধসহ একাধিক প্রকল্প হাতে নিয়েছে সরকার। এ লক্ষ্যে বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে ৫৬২ কোটি টাকা। এ জন্য টেন্ডারও হয়েছে। প্রায় এক বছর পেরিয়ে গেলেও ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানগুলো কাজ শুরু করছে না। পানি উন্নয়ন বোর্ডের (পাউবো) তাগাদায়ও কোনো কাজ হচ্ছে না বলে জানিয়েছেন...
২০ নভেম্বর ২০২৪