সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী
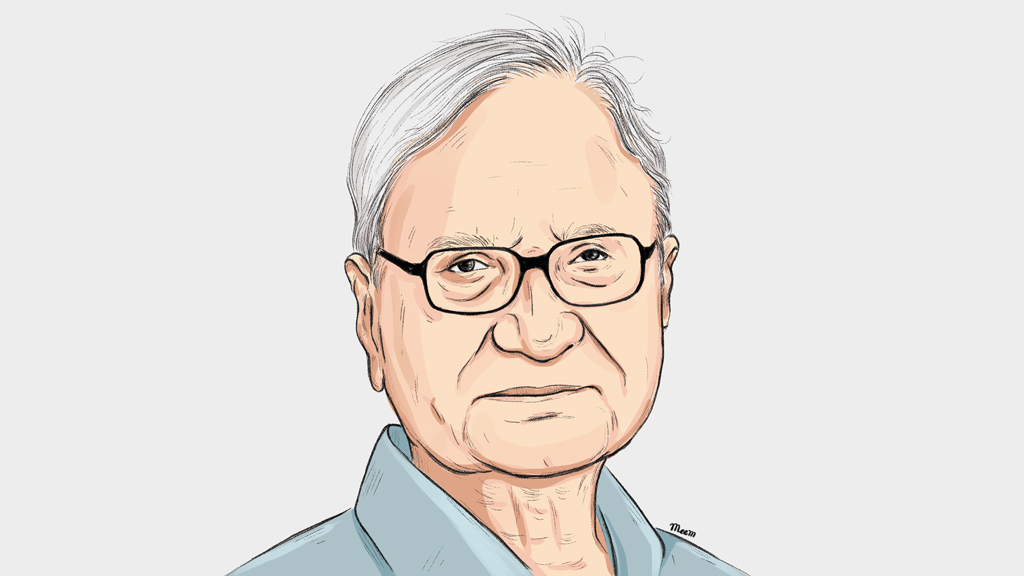
পুঁজিবাদ একটি বিশ্বব্যবস্থা। বাংলাদেশ সেই ব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত হয়ে গেছে এবং যোগাযোগের ব্যাপারে বিশ্ব পুঁজিবাদের যেটি প্রধান ভাষা, সেই ইংরেজিকেই আঁকড়ে ধরে রেখেছে। সে জন্য দেখা যাচ্ছে যে রাষ্ট্রভাষা যদিও বাংলা, কিন্তু রাষ্ট্রের ভাষা যে পুরোমাত্রায় বাংলা হবে, তেমনটা মোটেই ঘটেনি।
অর্থনীতিই হচ্ছে আসল নিয়ন্ত্রক; পুঁজিবাদী অর্থনীতি শ্রেণিবিভাজনকে অপরিহার্য করে তোলে। সেই বিভাজন সমাজে যখন রয়েছে, তখন শিক্ষাক্ষেত্রে থাকবে না কেন? সেখানেও আছে। যারা সুবিধাপ্রাপ্ত শ্রেণির সদস্য, তাঁরা আগের মতোই ইংরেজির দিকে ঝুঁকে থাকে এবং প্রাপ্ত সুবিধার বৃদ্ধি ঘটায়। রাষ্ট্রের শাসকও তারাই। ইংরেজি ভাষার প্রতি তাদের পক্ষপাত রাষ্ট্রব্যবস্থার বিবিধ ক্ষেত্রে প্রবহমান; শিক্ষাক্ষেত্রেও তা অনিবার্যভাবেই কার্যকর রয়ে গেছে। ওদিকে সাম্রাজ্যবাদের দ্বারা শাসিত হওয়ার দরুন যে মোহ ও মৌতাত সৃষ্টি হয়েছিল, সেটাও কিন্তু কাটেনি।
এর অদৃশ্য তৎপরতা বহুবিধ। দৃশ্যমান প্রমাণ মিলবে ছোট ছোট ঘটনাতেও। যেমন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পাকিস্তানি আমলে চালু করা ইকবাল হল, জিন্নাহ হল—এসব নাম বদল হয়েছে। ইংরেজ আমলে প্রবর্তিত কার্জন হল, লিটন হল বা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকার ফুলার রোড, এসব নাম কিন্তু অক্ষতই রয়ে গেছে। বাংলা প্রচলনের বেলায়ও এই ঔপনিবেশিক পিছুটানও একটা প্রতিবন্ধক বৈকি। আমরা তো ইংরেজদের অধীনে ছিলাম প্রায় ২০০ বছর, আর পাকিস্তানি শাসন টেকেনি ২২ বছরের বেশি। তদুপরি ইংরেজদের ছিল সাম্রাজ্য; পাকিস্তানিরা সাম্রাজ্য পাবে কোথায়? রাষ্ট্রই গড়তে পারেনি! তাদের প্রভাবটা তাই কম টেকসই হয়েছে।
কিন্তু মাতৃভাষাকে মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার না করলে শিক্ষা যে স্থায়ী, গভীর ও যথার্থ হবে, এমনটা তো সম্ভব নয়। শিক্ষা ভাষার সাহায্য ছাড়াও দেওয়া যায় বৈকি। কিন্তু মানুষ ভাষাহীন প্রাণী নয়। অভ্যাসেরও ভাষা আছে, আর সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে ভাষা তো খুবই জরুরি বিষয়। মাতৃভাষা ভিন্ন অন্য ভাষায় শিক্ষা দিলে সেটা হবে কৃত্রিম, অনেকাংশে যান্ত্রিক। ঘটেছেও ঠিক সেটাই। শিক্ষাক্ষেত্রে আমাদের প্রধান দুর্বলতাই হলো মাধ্যম হিসেবে মাতৃভাষাকে ব্যবহার করার ক্ষেত্রে ব্যর্থতা। মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা স্বাধীন বাংলাদেশের জন্য ছিল প্রধান চ্যালেঞ্জগুলোর একটি।
এই দায়িত্ব পালনের জন্য দরকার ছিল প্রচুর পরিমাণে ও অব্যাহত ধারায় বই লেখা, অনুবাদ করা এবং গবেষণা করা ও গবেষণাকে বাংলা ভাষায় প্রকাশ করা। এসব কাজ একা কেউ করতে পারে না। আবশ্যক ছিল রাষ্ট্রীয় উদ্যোগের। বলা বাহুল্য, সেই উদ্যোগ নেওয়া হয়নি। যে জন্য শিক্ষায় আমরা খুবই পিছিয়ে রয়েছি। একই সঙ্গে কর্তব্য ছিল দেশের সব মানুষকে প্রথম পর্যায়ে অক্ষরজ্ঞান দান করে দ্বিতীয় পর্যায়ে অর্জিত সাক্ষরতার অনুশীলন, যাতে চালু থাকে তার জন্য পদক্ষেপ নেওয়া।
শিক্ষক ছাড়া তো শিক্ষা সম্ভব নয়। একটা সময় ছিল, যে কথাটা বক্তাদের আলোচনায় এসেছে, শিক্ষকেরা যখন ছিলেন সমাজে অত্যন্ত সম্মানিত ব্যক্তি। কখনো কখনো মনে হতো সর্বাধিক সম্মানের পাত্র তাঁরাই। এর কারণ ছিল।
সমাজে তখন শিক্ষিত লোকের সংখ্যা ছিল অল্প। দ্বিতীয়ত, শিক্ষকেরা ছিলেন ব্যতিক্রমধর্মী মানুষ। তাঁদের দেখা হতো দাতা হিসেবে। তা ছাড়া, সাংস্কৃতিকভাবে তখন আমরা কিছুটা সামন্তবাদীও ছিলাম বটে। শ্রদ্ধা ও ভক্তি শক্তিশালী উপাদান ছিল আমাদের সংস্কৃতিতে। লোকে ভালোমানুষ খুঁজত এবং শিক্ষকদেরই সামনে দেখতে পেত। সে অবস্থা এখন আর নেই। সমাজে এখন তারাই সম্মানিত, যারা ক্ষমতাবান। আর ক্ষমতার মূল উৎস হচ্ছে অর্থ। অর্থ আছে ব্যবসায়ীদের হাতে; তাদের সহযোগী হচ্ছে আমলারা এবং রাজনীতিকেরা। জ্ঞানের মূল্য কমেছে, কারণ জ্ঞানও চলে গেছে অর্থের অধীনে এবং জ্ঞানার্জন মোটেই অর্থোপার্জনের জন্য প্রকৃষ্ট পন্থা হয়ে ওঠেনি। উন্নতির পথে জ্ঞান অনেক ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকও; নৈতিক জ্ঞান তো বোঝা হয়েই দাঁড়াতে চায়।
অভিযোগ আছে, আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে এখন আর তেমন একটা গবেষণা হয় না। কথাটা পুরোপুরি সত্য নয়। গবেষণা অবশ্যই হয়, তবে আগের তুলনায় কম হয়। হ্রাসপ্রাপ্তির কারণ যে কেবল বিশ্ববিদ্যালয়ের ভেতরেই রয়েছে, তা কিন্তু নয়। রয়েছে বাইরেও। ওই যে জ্ঞানের প্রায়োগিক মূল্যের হ্রাসপ্রাপ্তি, সেটাকে তো অবশ্যই বিবেচনায় রাখতে হবে। প্রাতিষ্ঠানিকভাবে গবেষণাকে যে উৎসাহিত করা হচ্ছে না, এটাও বাস্তবিক সত্য। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে উচ্চপদ লাভের জন্য গবেষণা ও প্রকাশনা এখন আর অত্যাবশ্যকীয় শর্ত নয়। আবার গবেষণা হলেও তা যথোপযুক্ত প্রচার পায় না। প্রাতিষ্ঠানিকভাবে প্রকাশনার উদ্যোগ অত্যন্ত সীমিত। সর্বোপরি অর্থোপার্জনের দাপটটা এতই প্রবল যে গবেষণায় মনোযোগ রাখা কঠিন হয়ে পড়ে।
শিক্ষা যে কোনোমতেই বিচ্ছিন্ন কোনো ব্যাপার নয়, সেটা তো আমরা সবাই জানি এবং মানি। শিক্ষা সংস্কৃতিরই অংশ। সংস্কৃতি সভ্যতার চেয়েও বড়। সভ্যতার পতন ঘটলেও সংস্কৃতি রয়ে যায়—থাকে সৃষ্টিশীল কর্মের নিদর্শনে, ইতিহাসে ও ঐতিহ্যে, থাকে আচার-আচরণে এবং বিশেষভাবে থাকে ভাষায়। সংস্কৃতির চর্চায় আনন্দ থাকে, সেই আনন্দ একাধারে সৃষ্টির ও উপভোগের এবং সংস্কৃতির চর্চা সামাজিকভাবেই করতে হয়। বাংলাদেশে সংস্কৃতির চর্চা এখন খুবই সংকুচিত।
পাড়ায়-মহল্লায় পাঠাগার নেই; থাকলেও সেগুলোর ব্যবহার অত্যন্ত সীমিত। নাটক হয় না। গান, বিতর্ক, প্রদর্শনী, উৎসব—সবকিছুরই নিদারুণ অভাব। খেলাধুলার সুযোগ পাওয়া ভার। সিনেমা হলে গিয়ে মানুষ যে চলচ্চিত্র দেখবে, সেই সুযোগ কমছে তো কমছেই। খোলা জায়গার অভাব মানুষকে চেপে ধরে। সন্ধ্যা হওয়ার আগেই নেমে আসে অন্ধকার। মানুষ ছোট ছোট প্রকোষ্ঠে চলে যায়। বন্দী হয়ে সময় কাটায়। মোবাইল ফোন, ফেসবুক, ইন্টারনেট ইত্যাদির ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ে।
ছায়ার সঙ্গে কথোপকথন চলে। প্রতারণাও ঘটে নানাবিধ। ওদিকে বিশ্বজুড়ে যে মাদকের, অস্ত্র ব্যবসার ও পর্নোগ্রাফির ব্যবসা নিজেই নিজের সীমাকে অতিক্রম করে চলেছে ক্রমাগত, তার আক্রমণ থেকেও বাংলাদেশ মোটেই মুক্ত নয়। করোনার আঘাতে কর্মহীনতা, দারিদ্র্য এবং হতাশা—সবকিছুই বেড়েছে। সংস্কৃতির চর্চার জন্য এসব উপদ্রব মোটেও সহায়ক নয়। জীবনে আনন্দের উপস্থিতি যদি কমে যায়, তবে শিক্ষার পক্ষেও তো স্বাভাবিক, সাবলীল ও আনন্দপূর্ণ থাকার কথা নয়। থাকছেও না। বাংলাদেশে এখন বায়ু, পানিসহ অনেক কিছুই দূষিত, শিক্ষা কি করে সুস্থ থাকে? পারছে না থাকতে।
শিক্ষায় প্রশিক্ষণ থাকে, কিন্তু প্রশিক্ষণ ও শিক্ষা এক জিনিস নয়। প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রটা সীমিত, শিক্ষার এলাকা প্রশস্ত এবং শিক্ষার্জনের সঙ্গে সঙ্গে প্রসারতা বাড়তে থাকে। শিক্ষার মধ্য দিয়ে বিশেষজ্ঞ তৈরি হয়, কিন্তু বিশেষজ্ঞ তৈরি শিক্ষার উদ্দেশ্য নয়। এখানে আবারও আসে সংস্কৃতির ভূমিকার প্রশ্ন। সংস্কৃতিমান না হলে বিশেষ বিষয়ে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত মানুষটি পূর্ণ অর্থে শিক্ষিত হয়ে উঠতে পারে না। কিছুতেই না। সুস্থ জীবনের জন্য যেমন আলো ও বাতাসের প্রয়োজন, যথার্থ শিক্ষার জন্যও তেমনি উপযুক্ত সাংস্কৃতিক পরিবেশ অত্যাবশ্যক।
লেখক: ইমেরিটাস অধ্যাপক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
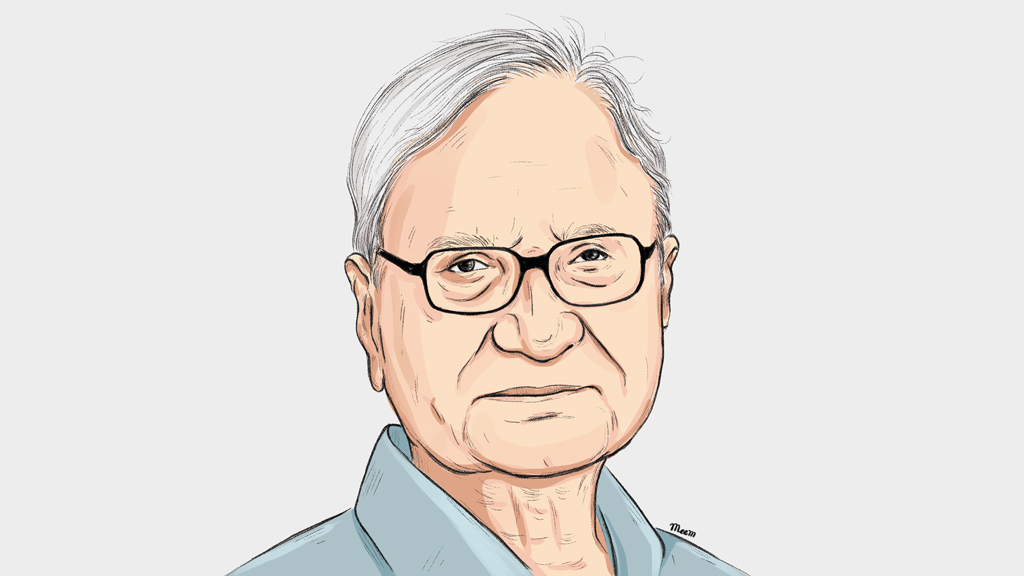
পুঁজিবাদ একটি বিশ্বব্যবস্থা। বাংলাদেশ সেই ব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত হয়ে গেছে এবং যোগাযোগের ব্যাপারে বিশ্ব পুঁজিবাদের যেটি প্রধান ভাষা, সেই ইংরেজিকেই আঁকড়ে ধরে রেখেছে। সে জন্য দেখা যাচ্ছে যে রাষ্ট্রভাষা যদিও বাংলা, কিন্তু রাষ্ট্রের ভাষা যে পুরোমাত্রায় বাংলা হবে, তেমনটা মোটেই ঘটেনি।
অর্থনীতিই হচ্ছে আসল নিয়ন্ত্রক; পুঁজিবাদী অর্থনীতি শ্রেণিবিভাজনকে অপরিহার্য করে তোলে। সেই বিভাজন সমাজে যখন রয়েছে, তখন শিক্ষাক্ষেত্রে থাকবে না কেন? সেখানেও আছে। যারা সুবিধাপ্রাপ্ত শ্রেণির সদস্য, তাঁরা আগের মতোই ইংরেজির দিকে ঝুঁকে থাকে এবং প্রাপ্ত সুবিধার বৃদ্ধি ঘটায়। রাষ্ট্রের শাসকও তারাই। ইংরেজি ভাষার প্রতি তাদের পক্ষপাত রাষ্ট্রব্যবস্থার বিবিধ ক্ষেত্রে প্রবহমান; শিক্ষাক্ষেত্রেও তা অনিবার্যভাবেই কার্যকর রয়ে গেছে। ওদিকে সাম্রাজ্যবাদের দ্বারা শাসিত হওয়ার দরুন যে মোহ ও মৌতাত সৃষ্টি হয়েছিল, সেটাও কিন্তু কাটেনি।
এর অদৃশ্য তৎপরতা বহুবিধ। দৃশ্যমান প্রমাণ মিলবে ছোট ছোট ঘটনাতেও। যেমন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পাকিস্তানি আমলে চালু করা ইকবাল হল, জিন্নাহ হল—এসব নাম বদল হয়েছে। ইংরেজ আমলে প্রবর্তিত কার্জন হল, লিটন হল বা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকার ফুলার রোড, এসব নাম কিন্তু অক্ষতই রয়ে গেছে। বাংলা প্রচলনের বেলায়ও এই ঔপনিবেশিক পিছুটানও একটা প্রতিবন্ধক বৈকি। আমরা তো ইংরেজদের অধীনে ছিলাম প্রায় ২০০ বছর, আর পাকিস্তানি শাসন টেকেনি ২২ বছরের বেশি। তদুপরি ইংরেজদের ছিল সাম্রাজ্য; পাকিস্তানিরা সাম্রাজ্য পাবে কোথায়? রাষ্ট্রই গড়তে পারেনি! তাদের প্রভাবটা তাই কম টেকসই হয়েছে।
কিন্তু মাতৃভাষাকে মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার না করলে শিক্ষা যে স্থায়ী, গভীর ও যথার্থ হবে, এমনটা তো সম্ভব নয়। শিক্ষা ভাষার সাহায্য ছাড়াও দেওয়া যায় বৈকি। কিন্তু মানুষ ভাষাহীন প্রাণী নয়। অভ্যাসেরও ভাষা আছে, আর সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে ভাষা তো খুবই জরুরি বিষয়। মাতৃভাষা ভিন্ন অন্য ভাষায় শিক্ষা দিলে সেটা হবে কৃত্রিম, অনেকাংশে যান্ত্রিক। ঘটেছেও ঠিক সেটাই। শিক্ষাক্ষেত্রে আমাদের প্রধান দুর্বলতাই হলো মাধ্যম হিসেবে মাতৃভাষাকে ব্যবহার করার ক্ষেত্রে ব্যর্থতা। মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা স্বাধীন বাংলাদেশের জন্য ছিল প্রধান চ্যালেঞ্জগুলোর একটি।
এই দায়িত্ব পালনের জন্য দরকার ছিল প্রচুর পরিমাণে ও অব্যাহত ধারায় বই লেখা, অনুবাদ করা এবং গবেষণা করা ও গবেষণাকে বাংলা ভাষায় প্রকাশ করা। এসব কাজ একা কেউ করতে পারে না। আবশ্যক ছিল রাষ্ট্রীয় উদ্যোগের। বলা বাহুল্য, সেই উদ্যোগ নেওয়া হয়নি। যে জন্য শিক্ষায় আমরা খুবই পিছিয়ে রয়েছি। একই সঙ্গে কর্তব্য ছিল দেশের সব মানুষকে প্রথম পর্যায়ে অক্ষরজ্ঞান দান করে দ্বিতীয় পর্যায়ে অর্জিত সাক্ষরতার অনুশীলন, যাতে চালু থাকে তার জন্য পদক্ষেপ নেওয়া।
শিক্ষক ছাড়া তো শিক্ষা সম্ভব নয়। একটা সময় ছিল, যে কথাটা বক্তাদের আলোচনায় এসেছে, শিক্ষকেরা যখন ছিলেন সমাজে অত্যন্ত সম্মানিত ব্যক্তি। কখনো কখনো মনে হতো সর্বাধিক সম্মানের পাত্র তাঁরাই। এর কারণ ছিল।
সমাজে তখন শিক্ষিত লোকের সংখ্যা ছিল অল্প। দ্বিতীয়ত, শিক্ষকেরা ছিলেন ব্যতিক্রমধর্মী মানুষ। তাঁদের দেখা হতো দাতা হিসেবে। তা ছাড়া, সাংস্কৃতিকভাবে তখন আমরা কিছুটা সামন্তবাদীও ছিলাম বটে। শ্রদ্ধা ও ভক্তি শক্তিশালী উপাদান ছিল আমাদের সংস্কৃতিতে। লোকে ভালোমানুষ খুঁজত এবং শিক্ষকদেরই সামনে দেখতে পেত। সে অবস্থা এখন আর নেই। সমাজে এখন তারাই সম্মানিত, যারা ক্ষমতাবান। আর ক্ষমতার মূল উৎস হচ্ছে অর্থ। অর্থ আছে ব্যবসায়ীদের হাতে; তাদের সহযোগী হচ্ছে আমলারা এবং রাজনীতিকেরা। জ্ঞানের মূল্য কমেছে, কারণ জ্ঞানও চলে গেছে অর্থের অধীনে এবং জ্ঞানার্জন মোটেই অর্থোপার্জনের জন্য প্রকৃষ্ট পন্থা হয়ে ওঠেনি। উন্নতির পথে জ্ঞান অনেক ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকও; নৈতিক জ্ঞান তো বোঝা হয়েই দাঁড়াতে চায়।
অভিযোগ আছে, আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে এখন আর তেমন একটা গবেষণা হয় না। কথাটা পুরোপুরি সত্য নয়। গবেষণা অবশ্যই হয়, তবে আগের তুলনায় কম হয়। হ্রাসপ্রাপ্তির কারণ যে কেবল বিশ্ববিদ্যালয়ের ভেতরেই রয়েছে, তা কিন্তু নয়। রয়েছে বাইরেও। ওই যে জ্ঞানের প্রায়োগিক মূল্যের হ্রাসপ্রাপ্তি, সেটাকে তো অবশ্যই বিবেচনায় রাখতে হবে। প্রাতিষ্ঠানিকভাবে গবেষণাকে যে উৎসাহিত করা হচ্ছে না, এটাও বাস্তবিক সত্য। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে উচ্চপদ লাভের জন্য গবেষণা ও প্রকাশনা এখন আর অত্যাবশ্যকীয় শর্ত নয়। আবার গবেষণা হলেও তা যথোপযুক্ত প্রচার পায় না। প্রাতিষ্ঠানিকভাবে প্রকাশনার উদ্যোগ অত্যন্ত সীমিত। সর্বোপরি অর্থোপার্জনের দাপটটা এতই প্রবল যে গবেষণায় মনোযোগ রাখা কঠিন হয়ে পড়ে।
শিক্ষা যে কোনোমতেই বিচ্ছিন্ন কোনো ব্যাপার নয়, সেটা তো আমরা সবাই জানি এবং মানি। শিক্ষা সংস্কৃতিরই অংশ। সংস্কৃতি সভ্যতার চেয়েও বড়। সভ্যতার পতন ঘটলেও সংস্কৃতি রয়ে যায়—থাকে সৃষ্টিশীল কর্মের নিদর্শনে, ইতিহাসে ও ঐতিহ্যে, থাকে আচার-আচরণে এবং বিশেষভাবে থাকে ভাষায়। সংস্কৃতির চর্চায় আনন্দ থাকে, সেই আনন্দ একাধারে সৃষ্টির ও উপভোগের এবং সংস্কৃতির চর্চা সামাজিকভাবেই করতে হয়। বাংলাদেশে সংস্কৃতির চর্চা এখন খুবই সংকুচিত।
পাড়ায়-মহল্লায় পাঠাগার নেই; থাকলেও সেগুলোর ব্যবহার অত্যন্ত সীমিত। নাটক হয় না। গান, বিতর্ক, প্রদর্শনী, উৎসব—সবকিছুরই নিদারুণ অভাব। খেলাধুলার সুযোগ পাওয়া ভার। সিনেমা হলে গিয়ে মানুষ যে চলচ্চিত্র দেখবে, সেই সুযোগ কমছে তো কমছেই। খোলা জায়গার অভাব মানুষকে চেপে ধরে। সন্ধ্যা হওয়ার আগেই নেমে আসে অন্ধকার। মানুষ ছোট ছোট প্রকোষ্ঠে চলে যায়। বন্দী হয়ে সময় কাটায়। মোবাইল ফোন, ফেসবুক, ইন্টারনেট ইত্যাদির ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ে।
ছায়ার সঙ্গে কথোপকথন চলে। প্রতারণাও ঘটে নানাবিধ। ওদিকে বিশ্বজুড়ে যে মাদকের, অস্ত্র ব্যবসার ও পর্নোগ্রাফির ব্যবসা নিজেই নিজের সীমাকে অতিক্রম করে চলেছে ক্রমাগত, তার আক্রমণ থেকেও বাংলাদেশ মোটেই মুক্ত নয়। করোনার আঘাতে কর্মহীনতা, দারিদ্র্য এবং হতাশা—সবকিছুই বেড়েছে। সংস্কৃতির চর্চার জন্য এসব উপদ্রব মোটেও সহায়ক নয়। জীবনে আনন্দের উপস্থিতি যদি কমে যায়, তবে শিক্ষার পক্ষেও তো স্বাভাবিক, সাবলীল ও আনন্দপূর্ণ থাকার কথা নয়। থাকছেও না। বাংলাদেশে এখন বায়ু, পানিসহ অনেক কিছুই দূষিত, শিক্ষা কি করে সুস্থ থাকে? পারছে না থাকতে।
শিক্ষায় প্রশিক্ষণ থাকে, কিন্তু প্রশিক্ষণ ও শিক্ষা এক জিনিস নয়। প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রটা সীমিত, শিক্ষার এলাকা প্রশস্ত এবং শিক্ষার্জনের সঙ্গে সঙ্গে প্রসারতা বাড়তে থাকে। শিক্ষার মধ্য দিয়ে বিশেষজ্ঞ তৈরি হয়, কিন্তু বিশেষজ্ঞ তৈরি শিক্ষার উদ্দেশ্য নয়। এখানে আবারও আসে সংস্কৃতির ভূমিকার প্রশ্ন। সংস্কৃতিমান না হলে বিশেষ বিষয়ে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত মানুষটি পূর্ণ অর্থে শিক্ষিত হয়ে উঠতে পারে না। কিছুতেই না। সুস্থ জীবনের জন্য যেমন আলো ও বাতাসের প্রয়োজন, যথার্থ শিক্ষার জন্যও তেমনি উপযুক্ত সাংস্কৃতিক পরিবেশ অত্যাবশ্যক।
লেখক: ইমেরিটাস অধ্যাপক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের কুমিল্লা এলাকায় যাত্রীবাহী বাসে ডাকাতি বেড়েই চলছে। এ কারণে চালক ও যাত্রীদের কাছে আতঙ্কের নাম হয়ে উঠছে এই সড়ক। ডাকাতির শিকার বেশি হচ্ছেন প্রবাসফেরত লোকজন। ডাকাতেরা অস্ত্র ঠেকিয়ে লুট করে নিচ্ছে সর্বস্ব। আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর পরিচয়েও ঘটছে ডাকাতির ঘটনা।
০২ মার্চ ২০২৫
বিআরটিসির বাস দিয়ে চালু করা বিশেষায়িত বাস র্যাপিড ট্রানজিট (বিআরটি) লেনে অনুমতি না নিয়েই চলছে বেসরকারি কোম্পানির কিছু বাস। ঢুকে পড়ছে সিএনজিচালিত অটোরিকশা, ব্যাটারিচালিত অটোরিকশা। উল্টো পথে চলছে মোটরসাইকেল। অন্যদিকে বিআরটিসির মাত্র ১০টি বাস চলাচল করায় সোয়া চার হাজার কোটি টাকার এই প্রকল্প থেকে...
১৬ জানুয়ারি ২০২৫
গাজীপুর মহানগরের বোর্ডবাজার এলাকার ইসলামিক ইউনিভার্সিটি অব টেকনোলজির (আইইউটি) মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের শিক্ষার্থীরা পিকনিকে যাচ্ছিলেন শ্রীপুরের মাটির মায়া ইকো রিসোর্টে। ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়ক থেকে বাসগুলো গ্রামের সরু সড়কে ঢোকার পর বিদ্যুতের তারে জড়িয়ে যায় বিআরটিসির একটি দোতলা বাস...
২৪ নভেম্বর ২০২৪
ঝড়-জলোচ্ছ্বাস থেকে রক্ষায় সন্দ্বীপের ব্লক বেড়িবাঁধসহ একাধিক প্রকল্প হাতে নিয়েছে সরকার। এ লক্ষ্যে বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে ৫৬২ কোটি টাকা। এ জন্য টেন্ডারও হয়েছে। প্রায় এক বছর পেরিয়ে গেলেও ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানগুলো কাজ শুরু করছে না। পানি উন্নয়ন বোর্ডের (পাউবো) তাগাদায়ও কোনো কাজ হচ্ছে না বলে জানিয়েছেন...
২০ নভেম্বর ২০২৪