মামুনুর রশীদ
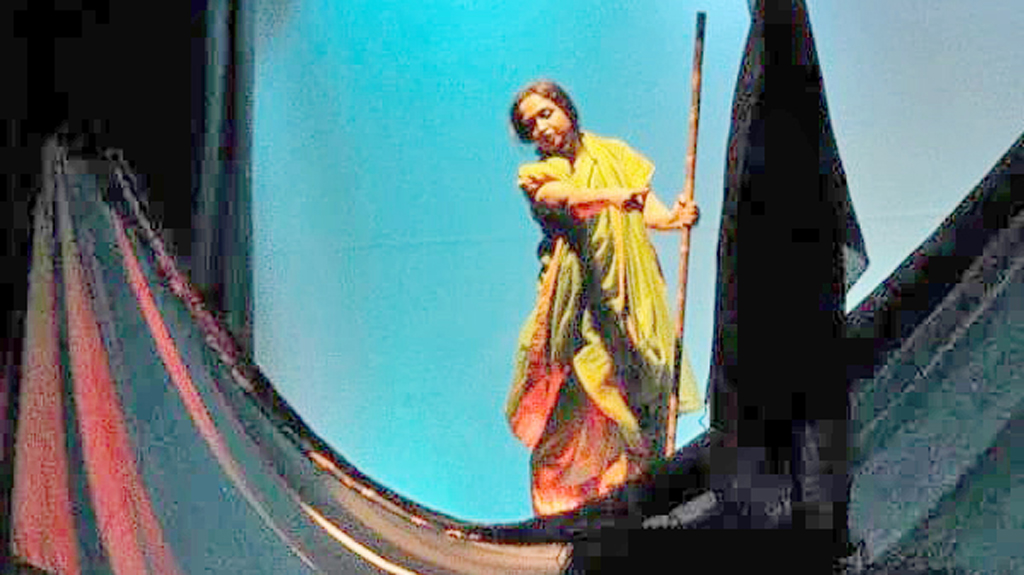
বাংলাদেশের নিয়মিত নাট্যচর্চার বয়স পঞ্চাশ। এখানেও নাটক প্রবলভাবে রাজনৈতিক। অভিনয় নিয়ন্ত্রণ ও প্রমোদ কর দিয়ে প্রথম দিকে এর বিরুদ্ধে নাটকের চর্চাকে ব্যাহত করার চেষ্টা চলেছে।
সম্প্রতি এক ঐতিহাসিক ঘটনা হয়ে গেল।
৭ ডিসেম্বর, ২০২২ বাংলা সাধারণ রঙ্গালয়ের দেড় শ বছর পূর্তি উৎসব। এই দিনে ১৮৭২ সালে অবিভক্ত ভারতের রাজধানী কলকাতায় সূচনা হলো সাধারণ রঙ্গালয়। এর আগে নাটকের অভিনয় হতো জমিদারের বাগানবাড়িতে, পূজার মণ্ডপে বা যেকোনো উন্মুক্ত স্থানে কিংবা পাড়া-মহল্লায়। সেসব নাট্যাভিনয়ে প্রতিভাবান অভিনেতারা
অভিনয় করতেন বটে, কিন্তু সবার প্রবেশাধিকার ছিল না।
আবার নাট্যাভিনয়ের জন্য সামন্ত প্রভু ও বিত্তবানদের অনুগ্রহ নিতে হতো। ১৮৭২ সালের প্রথম দিক থেকেই কিছু উদ্যমী তরুণ ন্যাশনাল থিয়েটার প্রতিষ্ঠা করেন এবং দীনবন্ধু মিত্রের ‘নীল দর্পণ’ নাটক দিয়ে টিকিটের বিনিময়ে যাত্রা শুরু করেন। অভিনয়ের জন্য খুব কম টাকায় জোড়াসাঁকোর মধুসূদন সান্যালের ঘড়িওয়ালা বাড়িটি ভাড়া নেন। চারদিক ঘেরাও করে আট আনা ও এক টাকা মূল্যের টিকিটের বিনিময়ে নাট্যাভিনয় শুরু করেন। দীনবন্ধু মিত্র নীল দর্পণ নাটকটি রচনা করেন ১৮৬০ সালে এবং ওই বছরই ঢাকার বাঙ্গালা প্রেস থেকে মুদ্রিত হয়ে প্রকাশিত হয়। নাটকটি যেহেতু অত্যাচারী ইংরেজ নীলকরদের বিরুদ্ধে, তাই নাট্যকার সেখানে তাঁর নাম ব্যবহার করেননি।
১৮৬১ সালে ঢাকার পূর্ববঙ্গ রঙ্গভূমিতে নাটকটি অভিনীত হয়। নাটকটি অভিনীত হওয়ার পর নানা ধরনের নিপীড়ন নেমে আসে এবং বিষয়টি কোর্ট পর্যন্ত গড়ায়। তবু কলকাতার উদ্যমী তরুণেরা বাংলা সাধারণ রঙ্গালয়ের প্রথম নাটক হিসেবে মঞ্চস্থ করার সিদ্ধান্ত নেয়। ওই দিন পুরো প্রেক্ষাগৃহে একটি মাত্র গ্যাসলাইটের মাধ্যমে অভিনীত হয় এবং টিকিট বিক্রি হয় এক শ টাকা।
ন্যাশনাল থিয়েটার এরপর নানা ধরনের সংকটে নিপতিত হয়। তবু নাট্যাভিনয়ের অগ্রযাত্রা চলতে থাকে। এ সময়ে ১৮৭৬ সালে ইংল্যান্ডের প্রিন্স অব ওয়েলস কলকাতায় বেড়াতে আসেন। জনৈক জগদানন্দ উকিলের বাড়িতে তাঁকে সংবর্ধনা জানানো হয়, সেখানে প্রচুর পানাহার ও নৃত্য-গীতের আয়োজন হয়েছিল। কলকাতার সুন্দরী রমণীরা মাটিতে তাঁদের চুল বিছিয়ে দিয়েছিলেন, যার ওপর দিয়ে প্রিন্স অব ওয়েলস হেঁটে সংবর্ধনাস্থলে পৌঁছান। এ ঘটনা সারা কলকাতায় ছড়িয়ে পড়ে। তখনকার নাট্যকর্মীরা এই সংবর্ধনাকে কেন্দ্র করে নাটক রচনা করেন, যার নাম ‘গজদানন্দ’। এ প্রহসনটি কলকাতায় খুবই আলোড়ন সৃষ্টি করে। তখন কোম্পানির শাসনের অবসান হলেও এখানকার ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ এটি বরদাশত করে না। নাটকের পাণ্ডুলিপি, দৃশ্যসজ্জা, প্রপস ইত্যাদি বাজেয়াপ্ত হয় এবং নাটকটি বন্ধ করে দেওয়া হয়। শুধু তা-ই নয়, অভিনয় নিয়ন্ত্রণ আইন, ১৮৭৬ কালাকানুন হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়। এই সময়ে বহু অভিনেতা, নাট্যকার ও নির্দেশক কারাবরণ করেন। সেই আইনে এ-ও বলা হয়, অভিনয়ের জন্য একটি চন্দ্রালোকিত রাত্রিই প্রয়োজন হবে, কৃষ্ণপক্ষের কোনো রজনীতে অভিনয় হবে না। আইনটি ভারতবর্ষে সর্বত্র প্রয়োগ করা হয় নাটকের কণ্ঠ রোধ করার জন্য।
স্বাধীন ভারতের কোনো কোনো স্থানে আইনটির এখনো প্রয়োগ আছে। কিন্তু বাংলাদেশে অনেক লড়াই-সংগ্রামের পর ২০০১ সালে আইনটি রদ করা হয়েছে। এর আগে এ আইনটিকে অমান্য করার জন্য নাট্যকর্মীরা নানা ধরনের উদ্যোগ নিয়েছিলেন। শুধু নাটক নয়, যাত্রাপালায়ও এর প্রয়োগ চলতে থাকে। মুকুন্দ দাস স্বদেশী যাত্রা নামে বরিশাল থেকে শুরু করে সারা বাংলায় দেশাত্মবোধক যাত্রাভিনয় করতেন। যেহেতু যেকোনো জেলার সদরে অভিনয় করতে গেলে পুলিশ এসে তা বন্ধ করতে পারে এবং তিনি গ্রেপ্তার হতে পারেন, এই ভেবে অভিনয়গুলো করতেন জেলার সীমান্তে। অভিনয় চলাকালে তিনি হয়তো খবর পেতেন বরিশাল জেলার পুলিশ অভিনয় বন্ধ করতে এগিয়ে আসছে। তখন তিনি তাঁর দলবল নিয়ে পাশের জেলা ফরিদপুরে চলে যেতেন। এমনি করেই জেলা থেকে জেলায় তাঁর অভিনয় চালিয়ে যেতেন। ব্রিটিশ সরকার সে সময়ে আরেকটি আইন প্রবর্তন করে, যার নাম ‘ডিস্ট্রিক্ট এনডোর্সমেন্ট অ্যাক্ট’। এটার সারমর্ম হলো, কোনো যাত্রাদল যদি এক জেলা থেকে আরেক জেলায় অভিনয় করতে যায়, তাহলে ওই জেলার ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেটের কাছ থেকে পূর্বাহ্ণে অনুমতি নিতে হয়। এত সব ঝামেলা উপেক্ষা করে বহুদিন পর্যন্ত মুকুন্দ দাস গ্রামবাংলার পথে-প্রান্তরে তাঁর স্বদেশী যাত্রা চালিয়ে গেছেন। সাধারণ রঙ্গালয় প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর কলকাতা শহরে বেশ কয়েকটি রঙ্গমঞ্চ গড়ে ওঠে। এই রঙ্গমঞ্চগুলোর মালিকানায় চলে আসে ধনাঢ্য ব্যক্তিরাই।
কিন্তু প্রথমে যাঁরা ন্যাশনাল থিয়েটার প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, তাঁদের ভাবনা ছিল টিকিটলব্ধ টাকা দিয়েই থিয়েটার চালিয়ে যাবেন। সাধারণ রঙ্গালয়ে একসময়ে বিনোদন মুখ্য হয়ে ওঠে। যে আদর্শ সামনে রেখে নীল দর্পণের মতো নাটক দিয়ে বাংলা সাধারণ রঙ্গালয় প্রতিষ্ঠা হয়েছিল, সেই ভাবনা আর রক্ষা করা যাচ্ছিল না। তাই চল্লিশের দশকের শুরুতে পাল্টা আরেকটি নাট্যধারার জন্ম হয়, যার উদ্যোগ নিল ভারতীয় গণনাট্য সংঘ। সেই উদ্যোগের প্রথম নাটক ‘নবান্ন’। দেশে তখন দুর্ভিক্ষ, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ চলছে। মানুষের তৈরি এই দুর্ভিক্ষের বিরুদ্ধে এক শৈল্পিক প্রতিবাদ নবান্ন। তারপর যুদ্ধ চলে যাওয়ার পর আরেকটি বড় আঘাত আসে সেটি হচ্ছে—দেশভাগ। নাট্যকর্মীরা তা-ও মেনে নিতে পারেননি। সাধারণ রঙ্গালয়ের বিনোদনধর্মিতার বিরুদ্ধে প্রতিবাদী নাটকের জোয়ার বইতে থাকে। অনেকে এই প্রক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত হলেন, আর এর নাম হলো সংঘনাট্য।পরবর্তীকালে ইংরেজিতে ‘গ্রুপ থিয়েটার’।
কলকাতা এবং ভারতবর্ষের অনেক স্থানে এই গ্রুপ থিয়েটার খুবই জনপ্রিয় হয়। নাট্যকর্মীদের নিজেদের সৃজনশীলতা এবং পকেটের পয়সা দিয়ে স্বেচ্ছাশ্রমে এই নাট্যধারা গড়ে ওঠে, যা এখনো ভারত ও বাংলাদেশে প্রচলিত আছে। বাংলাদেশের নাটকের ইতিহাসটা ঠিক সে রকমই। দেশ স্বাধীন হওয়ার আগেও নাটক হতো পাড়া-মহল্লায়, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ে এক অনিয়মিত চর্চায়। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর ১৯৭২ সাল থেকে এ চর্চা নিয়মিত হয়ে যায়। সেই অর্থে বাংলাদেশের নিয়মিত নাট্যচর্চার বয়স পঞ্চাশ। এখানেও নাটক প্রবলভাবে রাজনৈতিক। অভিনয় নিয়ন্ত্রণ ও প্রমোদ কর দিয়ে প্রথম দিকে এর বিরুদ্ধে নাটকের চর্চাকে ব্যাহত করার চেষ্টা চলেছে। বঙ্গবন্ধু বিষয়টিকে প্রথমে সহজ করে দিলেন প্রমোদ কর রহিত করে এবং পুলিশের কাছে নয়, নাটকের সেন্সর দিয়ে দিলেন শিল্পকলা একাডেমির হাতে। সামরিক শাসনামলে কখনো আবার পুলিশ কর্তৃপক্ষ নাটকের কালাকানুনকে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করেছে। কিন্তু নাট্যকর্মীদের প্রবল বাধার বিরুদ্ধে তা ধোপে টেকেনি। নাটকের সংঘবদ্ধ শক্তি বাংলাদেশ গ্রুপ থিয়েটার কর্তৃপক্ষ সেন্সর আইন অমান্য করতে শুরু করে। স্বৈরাচারবিরোধী আন্দোলনের সময়ে নাটক একটি বড় রাজনৈতিক হাতিয়ার হিসেবে আত্মপ্রকাশ করতে থাকে। নাটক হয়ে দাঁড়ায় রাজনীতির এক বিকল্প মাধ্যমে।
কোনো কিছু ছাপার অক্ষরে প্রকাশ করলে কোনো অনুমতি লাগে না। একমাত্র অনুমতি লাগে নাটকে। তা না হলে অভিনয় করা যায় না। শিল্পের অন্যান্য শাখায় এ ধরনের কালাকানুন নেই। এর কারণও খুব সহজ। নীল দর্পণ নাটক দেড় শ বছর আগে যে উদাহরণ সৃষ্টি করেছিল, তাতে শাসকগোষ্ঠীর ভয় পাওয়ারই কথা। নাটকের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, এ শিল্পটি গণতান্ত্রিক। কিছু জীবন্ত মানুষ অভিনয় করে আর কিছু জীবন্ত মানুষ নাটকটি অবলোকন করে। এই দুইয়ের মিথস্ক্রিয়ায় একটা চেতনা তৈরি হয় এবং আদিকাল থেকেই সেই চেতনা প্রতিবাদী।
সেই নাটক জনপ্রিয় হয়, যা মানুষের কণ্ঠস্বরকে ধারণ করতে পারে। মানুষের প্রাণের কথা বিবেকের মতো জনসাধারণের কাছে পৌঁছে দেয় এবং একই সঙ্গে শাসকগোষ্ঠীকে দর্শকের সামনে উন্মোচন করে। বাংলায় আদিকাল থেকেই যেসব আঙ্গিক সংলাপ ও অভিনয়ের মাধ্যমে মানুষের সামনে উপস্থিত করেছে, সেগুলোও প্রতিবাদী এবং সমাজসংস্কারের বিষয়টি সামনে নিয়ে এসেছে। তাই এই জীবন্ত মাধ্যমটি সারা বিশ্বেই এখন প্রতিবাদী চেতনার বাহক।
কলকাতায় দেড় শ বছর পূর্তি উপলক্ষে নানা ধরনের অনুষ্ঠানের সঙ্গে নীল দর্পণ নাটকটি যেমন অভিনীত হয়েছে, তেমনি ঢাকায়ও ১৬ ও ১৭ ডিসেম্বর জাতীয় নাট্যশালায় বাঙলা থিয়েটার কলকাতার ৭ ডিসেম্বরের পর পুনরায় অভিনয় করেছে। দুটি স্থানেই বিপুলসংখ্যক দর্শক নাটকটি দেখে দেড় শ বছরের প্রাচীন ঐতিহ্যে ফিরে গেছেন। দুটি দেশেই নাট্যচর্চায় পৃষ্ঠপোষকতা নেই। ভারতে কিছুটা থাকলেও তা অপ্রতুল। বাংলাদেশে নাট্যচর্চায় গত পঞ্চাশ বছরে এক অভাবনীয় অগ্রগতি হয়েছে।
অনেকে বলে, নাটক মুক্তিযুদ্ধের উজ্জ্বল ফসল, নাটক সত্যিকার অর্থেই মুক্তিযুদ্ধকে বুকে ধারণ করে তার চেতনাকে পৌঁছে দেওয়ার গুরুদায়িত্ব বহন করে আসছে।
স্বৈরাচার, সাম্প্রদায়িকতা, শোষণ-নিপীড়ন—এসবের বিরুদ্ধে নাটক সোচ্চার হয়েছে এবং তার দৃঢ় অবস্থানকে জানান দিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু এখন পর্যন্ত নাটককে পেশা হিসেবে নিতে পারছেন না নিবেদিতপ্রাণ নাট্যকর্মীরা। এই দুঃখ দিন দিন গভীর থেকে গভীরতর হচ্ছে।
লেখক: মামুনুর রশীদ, নাট্যব্যক্তিত্ব
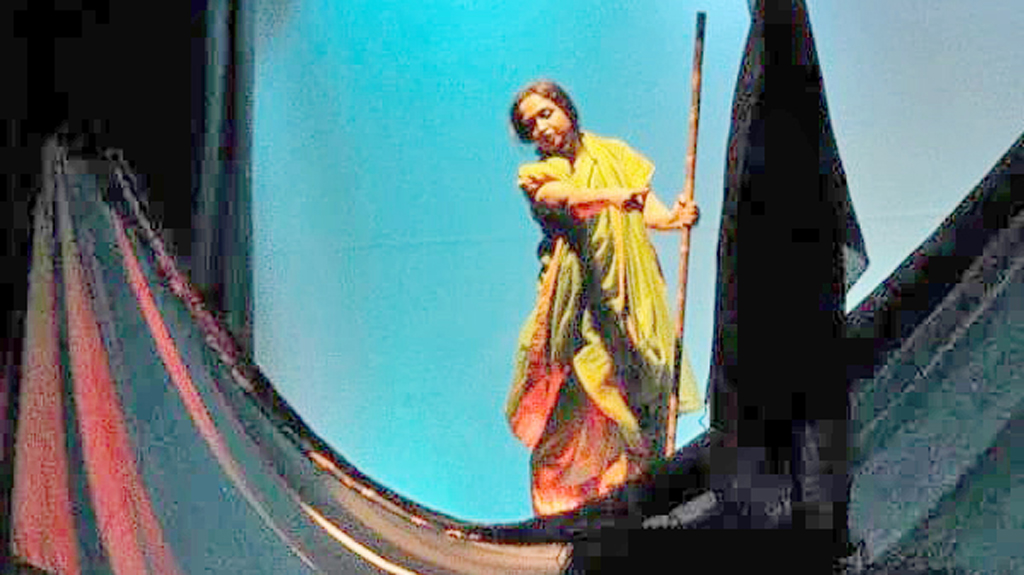
বাংলাদেশের নিয়মিত নাট্যচর্চার বয়স পঞ্চাশ। এখানেও নাটক প্রবলভাবে রাজনৈতিক। অভিনয় নিয়ন্ত্রণ ও প্রমোদ কর দিয়ে প্রথম দিকে এর বিরুদ্ধে নাটকের চর্চাকে ব্যাহত করার চেষ্টা চলেছে।
সম্প্রতি এক ঐতিহাসিক ঘটনা হয়ে গেল।
৭ ডিসেম্বর, ২০২২ বাংলা সাধারণ রঙ্গালয়ের দেড় শ বছর পূর্তি উৎসব। এই দিনে ১৮৭২ সালে অবিভক্ত ভারতের রাজধানী কলকাতায় সূচনা হলো সাধারণ রঙ্গালয়। এর আগে নাটকের অভিনয় হতো জমিদারের বাগানবাড়িতে, পূজার মণ্ডপে বা যেকোনো উন্মুক্ত স্থানে কিংবা পাড়া-মহল্লায়। সেসব নাট্যাভিনয়ে প্রতিভাবান অভিনেতারা
অভিনয় করতেন বটে, কিন্তু সবার প্রবেশাধিকার ছিল না।
আবার নাট্যাভিনয়ের জন্য সামন্ত প্রভু ও বিত্তবানদের অনুগ্রহ নিতে হতো। ১৮৭২ সালের প্রথম দিক থেকেই কিছু উদ্যমী তরুণ ন্যাশনাল থিয়েটার প্রতিষ্ঠা করেন এবং দীনবন্ধু মিত্রের ‘নীল দর্পণ’ নাটক দিয়ে টিকিটের বিনিময়ে যাত্রা শুরু করেন। অভিনয়ের জন্য খুব কম টাকায় জোড়াসাঁকোর মধুসূদন সান্যালের ঘড়িওয়ালা বাড়িটি ভাড়া নেন। চারদিক ঘেরাও করে আট আনা ও এক টাকা মূল্যের টিকিটের বিনিময়ে নাট্যাভিনয় শুরু করেন। দীনবন্ধু মিত্র নীল দর্পণ নাটকটি রচনা করেন ১৮৬০ সালে এবং ওই বছরই ঢাকার বাঙ্গালা প্রেস থেকে মুদ্রিত হয়ে প্রকাশিত হয়। নাটকটি যেহেতু অত্যাচারী ইংরেজ নীলকরদের বিরুদ্ধে, তাই নাট্যকার সেখানে তাঁর নাম ব্যবহার করেননি।
১৮৬১ সালে ঢাকার পূর্ববঙ্গ রঙ্গভূমিতে নাটকটি অভিনীত হয়। নাটকটি অভিনীত হওয়ার পর নানা ধরনের নিপীড়ন নেমে আসে এবং বিষয়টি কোর্ট পর্যন্ত গড়ায়। তবু কলকাতার উদ্যমী তরুণেরা বাংলা সাধারণ রঙ্গালয়ের প্রথম নাটক হিসেবে মঞ্চস্থ করার সিদ্ধান্ত নেয়। ওই দিন পুরো প্রেক্ষাগৃহে একটি মাত্র গ্যাসলাইটের মাধ্যমে অভিনীত হয় এবং টিকিট বিক্রি হয় এক শ টাকা।
ন্যাশনাল থিয়েটার এরপর নানা ধরনের সংকটে নিপতিত হয়। তবু নাট্যাভিনয়ের অগ্রযাত্রা চলতে থাকে। এ সময়ে ১৮৭৬ সালে ইংল্যান্ডের প্রিন্স অব ওয়েলস কলকাতায় বেড়াতে আসেন। জনৈক জগদানন্দ উকিলের বাড়িতে তাঁকে সংবর্ধনা জানানো হয়, সেখানে প্রচুর পানাহার ও নৃত্য-গীতের আয়োজন হয়েছিল। কলকাতার সুন্দরী রমণীরা মাটিতে তাঁদের চুল বিছিয়ে দিয়েছিলেন, যার ওপর দিয়ে প্রিন্স অব ওয়েলস হেঁটে সংবর্ধনাস্থলে পৌঁছান। এ ঘটনা সারা কলকাতায় ছড়িয়ে পড়ে। তখনকার নাট্যকর্মীরা এই সংবর্ধনাকে কেন্দ্র করে নাটক রচনা করেন, যার নাম ‘গজদানন্দ’। এ প্রহসনটি কলকাতায় খুবই আলোড়ন সৃষ্টি করে। তখন কোম্পানির শাসনের অবসান হলেও এখানকার ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ এটি বরদাশত করে না। নাটকের পাণ্ডুলিপি, দৃশ্যসজ্জা, প্রপস ইত্যাদি বাজেয়াপ্ত হয় এবং নাটকটি বন্ধ করে দেওয়া হয়। শুধু তা-ই নয়, অভিনয় নিয়ন্ত্রণ আইন, ১৮৭৬ কালাকানুন হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়। এই সময়ে বহু অভিনেতা, নাট্যকার ও নির্দেশক কারাবরণ করেন। সেই আইনে এ-ও বলা হয়, অভিনয়ের জন্য একটি চন্দ্রালোকিত রাত্রিই প্রয়োজন হবে, কৃষ্ণপক্ষের কোনো রজনীতে অভিনয় হবে না। আইনটি ভারতবর্ষে সর্বত্র প্রয়োগ করা হয় নাটকের কণ্ঠ রোধ করার জন্য।
স্বাধীন ভারতের কোনো কোনো স্থানে আইনটির এখনো প্রয়োগ আছে। কিন্তু বাংলাদেশে অনেক লড়াই-সংগ্রামের পর ২০০১ সালে আইনটি রদ করা হয়েছে। এর আগে এ আইনটিকে অমান্য করার জন্য নাট্যকর্মীরা নানা ধরনের উদ্যোগ নিয়েছিলেন। শুধু নাটক নয়, যাত্রাপালায়ও এর প্রয়োগ চলতে থাকে। মুকুন্দ দাস স্বদেশী যাত্রা নামে বরিশাল থেকে শুরু করে সারা বাংলায় দেশাত্মবোধক যাত্রাভিনয় করতেন। যেহেতু যেকোনো জেলার সদরে অভিনয় করতে গেলে পুলিশ এসে তা বন্ধ করতে পারে এবং তিনি গ্রেপ্তার হতে পারেন, এই ভেবে অভিনয়গুলো করতেন জেলার সীমান্তে। অভিনয় চলাকালে তিনি হয়তো খবর পেতেন বরিশাল জেলার পুলিশ অভিনয় বন্ধ করতে এগিয়ে আসছে। তখন তিনি তাঁর দলবল নিয়ে পাশের জেলা ফরিদপুরে চলে যেতেন। এমনি করেই জেলা থেকে জেলায় তাঁর অভিনয় চালিয়ে যেতেন। ব্রিটিশ সরকার সে সময়ে আরেকটি আইন প্রবর্তন করে, যার নাম ‘ডিস্ট্রিক্ট এনডোর্সমেন্ট অ্যাক্ট’। এটার সারমর্ম হলো, কোনো যাত্রাদল যদি এক জেলা থেকে আরেক জেলায় অভিনয় করতে যায়, তাহলে ওই জেলার ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেটের কাছ থেকে পূর্বাহ্ণে অনুমতি নিতে হয়। এত সব ঝামেলা উপেক্ষা করে বহুদিন পর্যন্ত মুকুন্দ দাস গ্রামবাংলার পথে-প্রান্তরে তাঁর স্বদেশী যাত্রা চালিয়ে গেছেন। সাধারণ রঙ্গালয় প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর কলকাতা শহরে বেশ কয়েকটি রঙ্গমঞ্চ গড়ে ওঠে। এই রঙ্গমঞ্চগুলোর মালিকানায় চলে আসে ধনাঢ্য ব্যক্তিরাই।
কিন্তু প্রথমে যাঁরা ন্যাশনাল থিয়েটার প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, তাঁদের ভাবনা ছিল টিকিটলব্ধ টাকা দিয়েই থিয়েটার চালিয়ে যাবেন। সাধারণ রঙ্গালয়ে একসময়ে বিনোদন মুখ্য হয়ে ওঠে। যে আদর্শ সামনে রেখে নীল দর্পণের মতো নাটক দিয়ে বাংলা সাধারণ রঙ্গালয় প্রতিষ্ঠা হয়েছিল, সেই ভাবনা আর রক্ষা করা যাচ্ছিল না। তাই চল্লিশের দশকের শুরুতে পাল্টা আরেকটি নাট্যধারার জন্ম হয়, যার উদ্যোগ নিল ভারতীয় গণনাট্য সংঘ। সেই উদ্যোগের প্রথম নাটক ‘নবান্ন’। দেশে তখন দুর্ভিক্ষ, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ চলছে। মানুষের তৈরি এই দুর্ভিক্ষের বিরুদ্ধে এক শৈল্পিক প্রতিবাদ নবান্ন। তারপর যুদ্ধ চলে যাওয়ার পর আরেকটি বড় আঘাত আসে সেটি হচ্ছে—দেশভাগ। নাট্যকর্মীরা তা-ও মেনে নিতে পারেননি। সাধারণ রঙ্গালয়ের বিনোদনধর্মিতার বিরুদ্ধে প্রতিবাদী নাটকের জোয়ার বইতে থাকে। অনেকে এই প্রক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত হলেন, আর এর নাম হলো সংঘনাট্য।পরবর্তীকালে ইংরেজিতে ‘গ্রুপ থিয়েটার’।
কলকাতা এবং ভারতবর্ষের অনেক স্থানে এই গ্রুপ থিয়েটার খুবই জনপ্রিয় হয়। নাট্যকর্মীদের নিজেদের সৃজনশীলতা এবং পকেটের পয়সা দিয়ে স্বেচ্ছাশ্রমে এই নাট্যধারা গড়ে ওঠে, যা এখনো ভারত ও বাংলাদেশে প্রচলিত আছে। বাংলাদেশের নাটকের ইতিহাসটা ঠিক সে রকমই। দেশ স্বাধীন হওয়ার আগেও নাটক হতো পাড়া-মহল্লায়, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ে এক অনিয়মিত চর্চায়। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর ১৯৭২ সাল থেকে এ চর্চা নিয়মিত হয়ে যায়। সেই অর্থে বাংলাদেশের নিয়মিত নাট্যচর্চার বয়স পঞ্চাশ। এখানেও নাটক প্রবলভাবে রাজনৈতিক। অভিনয় নিয়ন্ত্রণ ও প্রমোদ কর দিয়ে প্রথম দিকে এর বিরুদ্ধে নাটকের চর্চাকে ব্যাহত করার চেষ্টা চলেছে। বঙ্গবন্ধু বিষয়টিকে প্রথমে সহজ করে দিলেন প্রমোদ কর রহিত করে এবং পুলিশের কাছে নয়, নাটকের সেন্সর দিয়ে দিলেন শিল্পকলা একাডেমির হাতে। সামরিক শাসনামলে কখনো আবার পুলিশ কর্তৃপক্ষ নাটকের কালাকানুনকে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করেছে। কিন্তু নাট্যকর্মীদের প্রবল বাধার বিরুদ্ধে তা ধোপে টেকেনি। নাটকের সংঘবদ্ধ শক্তি বাংলাদেশ গ্রুপ থিয়েটার কর্তৃপক্ষ সেন্সর আইন অমান্য করতে শুরু করে। স্বৈরাচারবিরোধী আন্দোলনের সময়ে নাটক একটি বড় রাজনৈতিক হাতিয়ার হিসেবে আত্মপ্রকাশ করতে থাকে। নাটক হয়ে দাঁড়ায় রাজনীতির এক বিকল্প মাধ্যমে।
কোনো কিছু ছাপার অক্ষরে প্রকাশ করলে কোনো অনুমতি লাগে না। একমাত্র অনুমতি লাগে নাটকে। তা না হলে অভিনয় করা যায় না। শিল্পের অন্যান্য শাখায় এ ধরনের কালাকানুন নেই। এর কারণও খুব সহজ। নীল দর্পণ নাটক দেড় শ বছর আগে যে উদাহরণ সৃষ্টি করেছিল, তাতে শাসকগোষ্ঠীর ভয় পাওয়ারই কথা। নাটকের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, এ শিল্পটি গণতান্ত্রিক। কিছু জীবন্ত মানুষ অভিনয় করে আর কিছু জীবন্ত মানুষ নাটকটি অবলোকন করে। এই দুইয়ের মিথস্ক্রিয়ায় একটা চেতনা তৈরি হয় এবং আদিকাল থেকেই সেই চেতনা প্রতিবাদী।
সেই নাটক জনপ্রিয় হয়, যা মানুষের কণ্ঠস্বরকে ধারণ করতে পারে। মানুষের প্রাণের কথা বিবেকের মতো জনসাধারণের কাছে পৌঁছে দেয় এবং একই সঙ্গে শাসকগোষ্ঠীকে দর্শকের সামনে উন্মোচন করে। বাংলায় আদিকাল থেকেই যেসব আঙ্গিক সংলাপ ও অভিনয়ের মাধ্যমে মানুষের সামনে উপস্থিত করেছে, সেগুলোও প্রতিবাদী এবং সমাজসংস্কারের বিষয়টি সামনে নিয়ে এসেছে। তাই এই জীবন্ত মাধ্যমটি সারা বিশ্বেই এখন প্রতিবাদী চেতনার বাহক।
কলকাতায় দেড় শ বছর পূর্তি উপলক্ষে নানা ধরনের অনুষ্ঠানের সঙ্গে নীল দর্পণ নাটকটি যেমন অভিনীত হয়েছে, তেমনি ঢাকায়ও ১৬ ও ১৭ ডিসেম্বর জাতীয় নাট্যশালায় বাঙলা থিয়েটার কলকাতার ৭ ডিসেম্বরের পর পুনরায় অভিনয় করেছে। দুটি স্থানেই বিপুলসংখ্যক দর্শক নাটকটি দেখে দেড় শ বছরের প্রাচীন ঐতিহ্যে ফিরে গেছেন। দুটি দেশেই নাট্যচর্চায় পৃষ্ঠপোষকতা নেই। ভারতে কিছুটা থাকলেও তা অপ্রতুল। বাংলাদেশে নাট্যচর্চায় গত পঞ্চাশ বছরে এক অভাবনীয় অগ্রগতি হয়েছে।
অনেকে বলে, নাটক মুক্তিযুদ্ধের উজ্জ্বল ফসল, নাটক সত্যিকার অর্থেই মুক্তিযুদ্ধকে বুকে ধারণ করে তার চেতনাকে পৌঁছে দেওয়ার গুরুদায়িত্ব বহন করে আসছে।
স্বৈরাচার, সাম্প্রদায়িকতা, শোষণ-নিপীড়ন—এসবের বিরুদ্ধে নাটক সোচ্চার হয়েছে এবং তার দৃঢ় অবস্থানকে জানান দিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু এখন পর্যন্ত নাটককে পেশা হিসেবে নিতে পারছেন না নিবেদিতপ্রাণ নাট্যকর্মীরা। এই দুঃখ দিন দিন গভীর থেকে গভীরতর হচ্ছে।
লেখক: মামুনুর রশীদ, নাট্যব্যক্তিত্ব

ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের কুমিল্লা এলাকায় যাত্রীবাহী বাসে ডাকাতি বেড়েই চলছে। এ কারণে চালক ও যাত্রীদের কাছে আতঙ্কের নাম হয়ে উঠছে এই সড়ক। ডাকাতির শিকার বেশি হচ্ছেন প্রবাসফেরত লোকজন। ডাকাতেরা অস্ত্র ঠেকিয়ে লুট করে নিচ্ছে সর্বস্ব। আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর পরিচয়েও ঘটছে ডাকাতির ঘটনা।
০২ মার্চ ২০২৫
বিআরটিসির বাস দিয়ে চালু করা বিশেষায়িত বাস র্যাপিড ট্রানজিট (বিআরটি) লেনে অনুমতি না নিয়েই চলছে বেসরকারি কোম্পানির কিছু বাস। ঢুকে পড়ছে সিএনজিচালিত অটোরিকশা, ব্যাটারিচালিত অটোরিকশা। উল্টো পথে চলছে মোটরসাইকেল। অন্যদিকে বিআরটিসির মাত্র ১০টি বাস চলাচল করায় সোয়া চার হাজার কোটি টাকার এই প্রকল্প থেকে...
১৬ জানুয়ারি ২০২৫
গাজীপুর মহানগরের বোর্ডবাজার এলাকার ইসলামিক ইউনিভার্সিটি অব টেকনোলজির (আইইউটি) মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের শিক্ষার্থীরা পিকনিকে যাচ্ছিলেন শ্রীপুরের মাটির মায়া ইকো রিসোর্টে। ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়ক থেকে বাসগুলো গ্রামের সরু সড়কে ঢোকার পর বিদ্যুতের তারে জড়িয়ে যায় বিআরটিসির একটি দোতলা বাস...
২৪ নভেম্বর ২০২৪
ঝড়-জলোচ্ছ্বাস থেকে রক্ষায় সন্দ্বীপের ব্লক বেড়িবাঁধসহ একাধিক প্রকল্প হাতে নিয়েছে সরকার। এ লক্ষ্যে বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে ৫৬২ কোটি টাকা। এ জন্য টেন্ডারও হয়েছে। প্রায় এক বছর পেরিয়ে গেলেও ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানগুলো কাজ শুরু করছে না। পানি উন্নয়ন বোর্ডের (পাউবো) তাগাদায়ও কোনো কাজ হচ্ছে না বলে জানিয়েছেন...
২০ নভেম্বর ২০২৪